অধ্যায় – ১ (আপেক্ষিকতা)
একের মাঝে লভিতে সবে,
সবের মাঝে করি একের সন্ধান।
জীবন এক, জিজ্ঞাসা অনেক। একই সত্যকে গর্ভে ধরে অন্তঃসত্ত্বা অজস্র ঘটনা (ফ্যাক্ট), আর সেই সত্য হলো – ঘটনা সর্বদাই আপেক্ষিক। দুধে যতই চিনি মেশাই না কেন, বিড়াল সেই মিষ্টতা আস্বাদনে অক্ষম। এমন অনেক রঙ আছে যা তোমার-আমার অদেখাই রয়ে গেল কিন্তু মৌমাছি তাদের দেখেছে। একই রচনা কারও অসাধারণ বোধ হয় আবার কারও কাছে তা ভীষণ অপরিণত। প্রবাহী ( তরল বা গ্যাস) যেমন স্বাকারহীন, ঘটনারও তেমন কোন নিজস্ব পরম (অ্যাব্সলিউট) রূপ নেই কারণ পর্যবেক্ষকের (অবসারভার) উপলব্ধিই হলো ঘটনার স্বরূপ যা পর্যবেক্ষক বদলে গেলে বা একই পর্যবেক্ষকের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে বদলে যেতে পারে – তা সেই পর্যবেক্ষক কোন জীব হোক্ বা যন্ত্র। চোখ কালো চশমায় ঢাকলে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনেও সন্ধ্যা নেমে আসে। উপলব্ধি হলো সেই চশমা যার মধ্য দিয়ে জগৎ এক আপাত রূপে প্রতিভাত হয়।
এখন বলাই বাহুল্য যে,পর্যবেক্ষকের মধ্যে যদি উপলব্ধি জন্ম না নেয়,তার কাছে ঘটনাও অস্তিত্বহীন। আমাদের চোখ কেবল ৩৮০ বা ৪০০ ন্যানোমিটার থেকে ৭০০ বা ৭৮০ ন্যানোমিটার সীমার মধ্যে থাকা কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (ওয়েভলেঙ্থ) তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের প্রতি সংবেদনশীল কিংবা আমরা কেবল ২০-২০০০০ হার্ৎজ কম্পাঙ্কের (ফ্রিকোয়েন্সি) শব্দই শুনতে সক্ষম। এখন ভেবে দেখ,যন্ত্রের সাহায্য না নিলে উপরোক্ত সীমার বর্হিভূত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বা কম্পাঙ্কের যথাক্রমে আলো বা শব্দের উপস্থিতি আমাদের বোধের অতীত – এরা নিতান্তই আমাদের কাছে অস্তিত্বহীন।


উপলব্ধি (পারসেপ্শন্) : আলোচনার শুরু থেকেই “উপলব্ধি” (পারসেপ্শন্) শব্দটা বেশ কয়েকবার ব্যবহার করেছি। সময় এসেছে “উপলব্ধি” বস্তুত কি তা বোঝার। উদ্দীপনা (স্টিমুলাস) আভ্যন্তরীণ (ইন্টারনাল) হোক কিংবা বাহ্যিক (এক্সটারনাল), তা পর্যবেক্ষকের মধ্যে সর্বদাই কিছু পরিবর্তন ঘটায়। কোন পর্যবেক্ষকের মধ্যে হওয়া পরিবর্তন (চেঞ্জ) যখন সেই পর্যবেক্ষক পরিমাপে (মেসার) সক্ষম হয়, সেই পরিমাপকে (মেসারমেন্ট) বলতে পারি ঐ “পর্যবেক্ষকের উপলব্ধি”। বিষয়টা উদাহরণের মাধ্যমে সহজ করে বোঝাই। চিন্তা করে দেখ যে, আমরা কোন বস্তু (অবজেক্ট) দেখতে পাই কিভাবে। ৩৮০ বা ৪০০ ন্যানোমিটার থেকে ৭০০ বা ৭৮০ ন্যানোমিটার সীমার মধ্যে থাকা যে কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (ওয়েভলেঙ্থ) তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ কোন উৎস (সোর্স) থেকে বস্তুটির উপর পতিত হয় ও সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখের রেটিনায় পড়ে ও রেটিনার তাৎক্ষণিক অবস্থার (স্টেট) পরিবর্তন ঘটায়। এই পরিবর্তনটি মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট স্নায়ুকোষকে উদ্দীপিত করার জন্য যথেষ্ট। ঐ উদ্দীপিত স্নায়ুকোষের প্লাজমা পর্দার স্থির তাড়িতিক বিভব-বৃদ্ধি (ইনক্রিস্ অফ ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক পোটেন্শিয়াল) লাগোয়া সাইন্যাপ্স-কে (দুটি নিউরোন বা স্নায়ুকোষের সংযোগস্থল নিউরাল কানেক্শন বা স্নায়ু-সংযোগ বা “সাইন্যাপ্স” নামে পরিচিত) সক্রিয় করে তোলে ও সেখানে নিউরোট্রান্সমিটার ক্ষরণ ঘটায় যা সাইন্যাপ্স-টির লাগোয়া আরেকটি স্নায়ুকোষের প্লাজমা পর্দার স্থির তাড়িতিক বিভব-বৃদ্ধি ঘটায় অর্থাৎ স্নায়ুকোষটিকে উদ্দীপিত করে। কতগুলি নিউরোন বা স্নায়ুকোষের একটি ক্রমে (অর্ডার) এভাবে উদ্দীপিত হওয়াই উপলব্ধির (ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা বা কিছু স্মরণ করা বা নতুন কিছু ভাবা) পরিভাষা। মস্তিষ্কের মধ্যে ঐ নির্দিষ্ট কিছু স্নায়ুকোষের উদ্দীপিত হওয়ার অর্থই হলো, মস্তিষ্ক চোখের রেটিনার অবস্থা-পরিবর্তনটি পরিমাপ করতে পেরেছে এবং বস্তুটির আমাদের কাছে দৃশ্যমান হওয়া (যাকে আমরা এক প্রকার “উপলব্ধি” বলতে পারি) মস্তিষ্কের সেই পরিমাপেরই নামান্তর।
এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, কতগুলি স্নায়ুকোষের উদ্দীপনার ক্রম যদি নিতান্তই ছন্দবদ্ধ (রিদ্মিক) হয়, তবে তা “ব্রেইন ওয়েভ” বা “মস্তিষ্ক তরঙ্গ” নামে পরিচিত।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের “ব্রেইন ওয়েভ” বা “মস্তিষ্ক তরঙ্গ”-র প্রাচুর্য্যের ভিত্তিতে মনুষ্য-মস্তিষ্কের প্রধান প্রধান কতগুলি অবস্থা রয়েছে যারা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পক্ষে বেশ জটিল। আমি যতটা সম্ভব সঠিকভাবে ও সহজ করে সেগুলি বোঝানোর চেষ্টা করব দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে (এই প্রবন্ধের পরবর্তী অধ্যায়গুলো পরের পেজ বা পাতাগুলিতে একে একে তুলে ধরা হলো) –




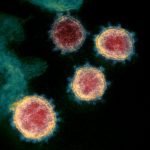
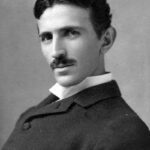
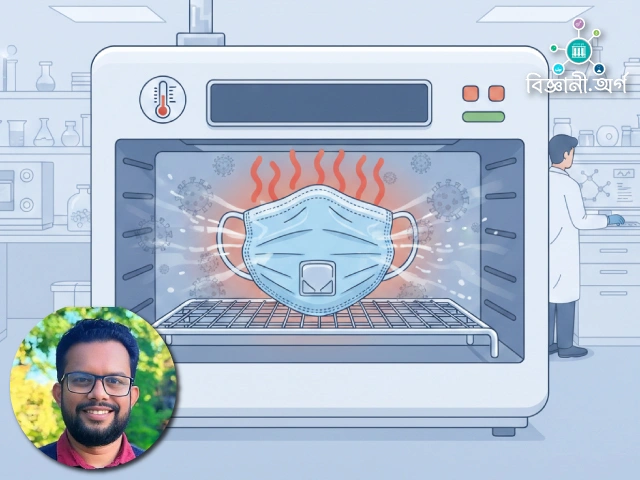




Leave a comment