অন্ধকার ঘরে ঢুকে হঠাৎ ভুলে গেলেন কেন এসেছিলেন? কিংবা জরুরি কিছু গুগল করে দু’সেকেন্ড পরেই কী খুঁজছিলেন ভুলে গেলেন? এমন অভিজ্ঞতা কার না আছে! এই ছোট ছোট ভুলে যাওয়া বা ভুলে থাকার পেছনে প্রযুক্তি ঠিক কীভাবে আমাদের মস্তিষ্কের কাজকে প্রভাবিত করছে, সেটাই আজকের গল্প।
গল্পের শুরু: মানুষের ‘ডিজিটাল মনে’ অভ্যস্ত হওয়া
একসময় মানুষ জ্ঞান সংরক্ষণ করত স্মৃতিতে বা মুখে মুখে গল্প বলে। পরে সেই স্থান নিয়েছিল পাণ্ডুলিপি, বই, ও লাইব্রেরি। আর এখন আমাদের হাতের কাছে ইন্টারনেট—বিশ্বের যেকোনো তথ্য মুহূর্তেই পাওয়া যায়। ফলে আমরা নিজেরা কম মনে রাখছি, বরং মনে রাখার কাজটা সঁপে দিচ্ছি ডিজিটাল ডিভাইস বা অনলাইন টুলগুলোকে। এটা মোটেও কল্পকাহিনী নয়; গবেষণাও কিন্তু একই কথা বলছে।
‘গুগল এফেক্ট’: কোথায় তথ্য আছে মনে রাখি, তথ্যটা নয়
২০১১ সালে আমেরিকার মনোবিজ্ঞানী বেটসি স্প্যারো ও তাঁর সহকর্মীরা “Science” জার্নালে একটি গবেষণা প্রকাশ করেন। সেখানে দেখা গেল, মানুষ এখন তথ্য নিজে মনে রাখার বদলে মনে রাখে কোথায় সেই তথ্য পেতে পারে—যেমন গুগলে কীভাবে সার্চ করলে সহজে পাওয়া যাবে। এই প্রবণতাকেই বলা হচ্ছে ‘গুগল এফেক্ট’। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বেশিরভাগই তথ্যের চেয়ে ‘তথ্য কোথায় আছে’ সেটা মনে রাখার দিকে বেশি মনোযোগী ছিলেন।
পরিসংখ্যানের দিকে একটু নজর
এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রায় ৬০-৭০% মানুষ এখন যেকোনো অজানা তথ্য গুগলে সার্চ করে।
আর গুগলে সার্চ করার পর, মাত্র ২০-২৫% মানুষ দীর্ঘমেয়াদে ওই তথ্য মনে রাখতে পারেন।
বাকিরা মনে রাখেন মূলত “কী সার্চ দেব” বা “কোন ওয়েবসাইটে তথ্যটি পাওয়া যাবে”—ফলাফল নয়।
জিপিএস ও পথভোলার গল্প
শুধু তথ্য খোঁজার ক্ষেত্রেই নয়, রাস্তা মনে রাখার ক্ষেত্রেও প্রযুক্তি আমাদের উপর প্রভাব ফেলছে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, নিয়মিত জিপিএসের উপর নির্ভরশীল মানুষগুলো পরে নিজেরাই পথ খুঁজে পেতে হিমশিম খায়। এই অবস্থা অনেকটা তাদের মতোই, যারা কোনো দিন নিজের হাতে ড্রাইভ করেননি। উদাহরণস্বরূপ, কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত জিপিএস ব্যবহারকারীদের মস্তিষ্কের ‘হিপোক্যাম্পাস’ তুলনামূলক কম সক্রিয় থাকে, যা জায়গা মনে রাখা ও মানচিত্র বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।
উল্লেখযোগ্য সংখ্যা
গবেষণায় দেখা যায়, যারা নিয়মিত জিপিএস ব্যবহার করেন, তাদের মধ্যে ৪০-৫০% লোক রুট মুখস্থ রাখতে ব্যর্থ হন।
বিপরীতে, যারা ম্যাপ বা ধারণার উপর নির্ভর করে পথ চলে, তাদের মধ্যে এই হার ২০-২৫%।
এআই আমাদের চিন্তা আরও কতদূর বদলে দিতে পারে?
গুগলের মতো টুল ব্যবহার করে মানুষ যেমন মনে করে যে, “আমার অনেক কিছু জানা আছে,” এআই-চ্যাটবট কিংবা উন্নত সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে সেই ভাবনাটাই আরও বাড়ছে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, যখন অংশগ্রহণকারীরা গুগল ব্যবহার করে প্রশ্নের উত্তর জানছিলেন, তখন তারা নিজেকে অন্যদের চেয়ে স্মার্ট মনে করছিলেন—even যদি তাদের প্রকৃত জ্ঞান বা মনে রাখার ক্ষমতা বাড়ত না!
তবে এআই শুধু তথ্য উদ্ধার করে দেয় না, প্রয়োজনে নিজেই তথ্য তৈরি করতে পারে (যা মাঝে মাঝে ভুলও হতে পারে)। কোনো চ্যাটবট ভুল বা মিথ্যা তথ্য দিলেও, বারবার তা পড়তে পড়তে আমরা হয়তো একটা সময় তা-ই সত্যি বলে বিশ্বাস করতে শুরু করব। এই ঘটনাকে ‘এআই-জেনারেটেড কনটেন্ট’-এর স্মৃতি পুনর্লিখন বা ‘মেমোরি রিরাইটিং’ সমস্যা বলা হয়।
সাম্প্রতিক গবেষণার দিকে নজর
২০২৩ সালের এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, নিয়মিত এআই চ্যাটবটের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিরা বাস্তব ঘটনার পাশাপাশি ভুল তথ্যও শিখে নিচ্ছেন।
দুই-তৃতীয়াংশ ব্যবহারকারী জানিয়েছেন, তথ্য যাচাই না করেই চ্যাটবটের মতামতকে ‘সত্য’ বলে ধরে নেন।
তবে কী আমাদের চিন্তিত হওয়া উচিত?
মানুষ বরাবরই নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। মুখে মুখে গল্প বলা থেকে বই, বই থেকে ডিজিটাল মিডিয়া—এভাবেই আমাদের জানা-বোঝা এগিয়ে গেছে। এআই হলো সেই ধারাবাহিকতারই সাম্প্রতিক সংযোজন। অতীতের সব মাধ্যম আমাদের জ্ঞান সংরক্ষণ ও পেতে সহায়তা করেছে। কিন্তু এআই সেই জ্ঞানকে গঠনও করতে পারে—সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে নতুন তথ্য ‘উৎপাদন’ করতে পারে। তাই আমরা শুধু স্মৃতি সরিয়ে দিচ্ছি না, বরং প্রশ্ন না করেই এআইকে দায়িত্ব দিচ্ছি তথ্য সাজানো, ছেঁকে দেওয়া, এমনকি তৈরি করার।
এর ফলে সমস্যা শুধু ভুলে যাওয়া নয়; ভুল বা অপূর্ণ তথ্য গ্রহণ করা এবং সমালোচনামূলক চিন্তার অভ্যাস হারিয়ে ফেলা। একজন সক্রিয় পাঠক বা শিখিয়েছেন হিসেবে আমাদের উচিত এআই-নির্ভর তথ্যকে যাচাই করা, উৎস খুঁজে দেখা, নিজে পড়ে বোঝার চেষ্টা করা।
শেষকথা: যুক্তিপূর্ণ ভাবনা বজায় রাখুন
এআই বা ডিজিটাল টুল ব্যবহার করা খারাপ নয়—বরং এগুলো আমাদের সময় বাঁচায়, জ্ঞানের জগৎ প্রসারিত করে। কিন্তু অন্তত যাচাই ও বিশ্লেষণের কাজটা আমাদেরই করতে হবে। তথ্য পাওয়ার পর নিজের চিন্তাশক্তি ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করা জরুরি। নতুবা এআই যা দেবে, সেটাই একমাত্র ‘সত্য’ বলে মেনে নেওয়ার ঝুঁকি থেকে যাবে।
তাই প্রযুক্তিকে সঙ্গী করে এগিয়ে যান, কিন্তু নিজের বুদ্ধি ও যুক্তিমূলক চিন্তার লাগাম হাতে রাখুন। যেকোনো তথ্য শেখার পর একটু সময় নিয়ে ভাবুন—আপনি যা শিখলেন, সেটি সত্যি কিনা, কোথা থেকে এলো। ডিজিটাল যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের বড় এক বন্ধু, তবে বন্ধু যেন আমাদের নিয়ন্ত্রণ না করে, বরং আমরা যেন সেই বন্ধুর সাহায্যে আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারি।


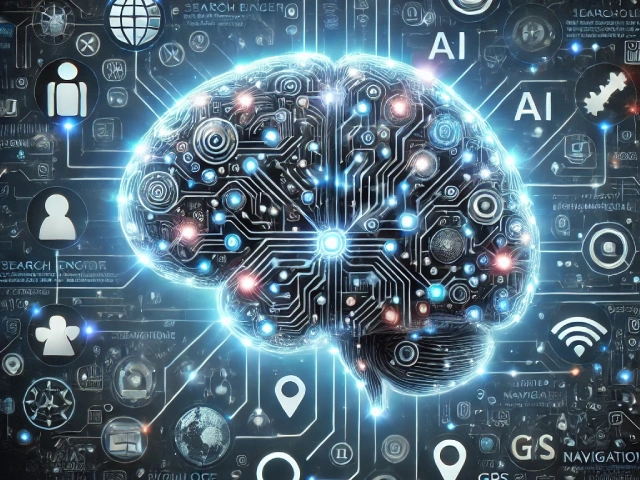

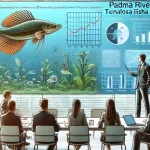
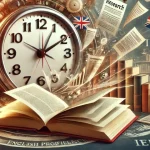





Leave a comment