একটা সময় ছিল, যখন মৃত্যুই ছিল একমাত্র সমাধান।
ওয়াশিংটনের রেন্টনে বসবাসকারী ৩৭ বছর বয়সী জোসেফ কোটসকে এক বছরের কিছু আগে তাঁর চিকিৎসকরা বলেছিলেন— “তুমি কী হাসপাতালে মরতে চাও, নাকি বাড়িতে?” তখন কোটস প্রায় অচেতন, বিছানায় শুয়ে একের পর এক দিন পার করছিলেন। তাঁর শরীরে ছিল এক বিরল ব্লাড ডিজঅর্ডার, নাম POEMS syndrome। হাত-পা অবশ, হৃদপিণ্ড বড় হয়ে গেছে, কিডনির কার্যক্ষমতা কমে এসেছে। প্রতি কয়েকদিন পর পর পেট থেকে লিটার লিটার করে তরল বের করতে হতো। কোটস তখন এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে, স্টেম সেল ট্রান্সপ্ল্যান্ট—যেটা তাঁকে বাঁচাতে পারত—সেটাও সম্ভব ছিল না।
“আমি ধরে নিয়েছিলাম, এবার বুঝি শেষ,” পরে এক সাক্ষাৎকারে বলেন কোটস। “আমি মানসিকভাবে হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম।”
কিন্তু তাঁর প্রেমিকা তারা থিওবাল্ড সহজে হাল ছাড়ার মানুষ নন। এক বছর আগে এক বিরল রোগ সম্পর্কিত সম্মেলনে পরিচয় হয়েছিল ফিলাডেলফিয়ার এক চিকিৎসক ড. ডেভিড ফাজগেনবাউমের সঙ্গে। সেই আশায় এক ইমেইল পাঠান তিনি।
পরদিন সকালেই ড. ফাজগেনবাউম ইমেইলে একটি বিকল্প চিকিৎসার প্রস্তাব দেন—কেমোথেরাপি, ইমিউনোথেরাপি ও স্টেরয়েডের এমন এক সংমিশ্রণ যা এই রোগের জন্য আগে কখনো ব্যবহার করা হয়নি।
তিন দিনের মধ্যেই কোটসের শরীর সাড়া দিতে শুরু করে। চার মাসের মধ্যে তিনি যথেষ্ট সুস্থ হন স্টেম সেল ট্রান্সপ্ল্যান্টের জন্য। আজ তিনি সম্পূর্ণ রেমিশনে।
আর এই চিকিৎসার প্রস্তাব? সেটা এসেছিল একজন মানুষের কাছ থেকে নয়, বরং একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (A.I.) মডেলের কাছ থেকে।
পুরনো ওষুধে নতুন প্রাণ
“আমরা আসলে এতদিন চোখের সামনে থাকা সম্ভাবনাগুলোকেই অগ্রাহ্য করে এসেছি,” বলেন ডোনাল্ড সি. লো, যিনি আগে National Center for Advancing Translational Sciences-এর থেরাপিউটিক ডেভেলপমেন্ট বিভাগের প্রধান ছিলেন এবং বর্তমানে ইউরোপীয় গ্রুপ Remedi4All-এ কর্মরত।
A.I.-এর সাহায্যে এখন বিজ্ঞানীরা হাজার হাজার পুরনো ওষুধের মধ্য থেকে নতুন চিকিৎসার উপায় খুঁজে বের করছেন। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় drug repurposing— অর্থাৎ বিদ্যমান ওষুধের নতুন ব্যবহার।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে প্রায় ৩০ কোটি মানুষ বিভিন্ন বিরল রোগে ভোগে। কিন্তু ৯০% এর বেশি রোগের কোনো অনুমোদিত চিকিৎসা নেই। গবেষণা কম, বিনিয়োগ কম, ফলাফলও অনিশ্চিত।
তাই এমন এক সময়, যখন অনেক রোগীর জন্য আশার আলো নিভে আসছে, সেখানে A.I. একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে।
একজন রোগী, একজন বিজ্ঞানী, আর একটি অদ্ভুত বিশ্বাস
এই গল্পটা শুরু হয়েছিল একজন রোগীর জীবন বাঁচাতে গিয়ে। ড. ডেভিড ফাজগেনবাউম নিজেই ছিলেন সেই রোগী। ২৫ বছর বয়সে মেডিকেল স্কুলে পড়ার সময় Castleman disease-এর এক বিরল ধরনে আক্রান্ত হন তিনি। তখন তিনি নিজেই নিজের চিকিৎসায় নেমে পড়েন।
“আমার হাতে না ছিল কোটি কোটি ডলার, না ছিল দশ বছর সময়। আমি জানতাম, পুরনো কোনো ওষুধেই হয়তো আমার মুক্তি লুকিয়ে আছে,” বলেন ড. ফাজগেনবাউম।
অবশেষে একটি কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্টে ব্যবহৃত ওষুধ sirolimus তাঁর জীবন রক্ষা করে।
এরপর থেকে তিনি ঠিক করেন—এই কাজই করবেন সারাজীবন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন Every Cure, একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান যা A.I.-এর সাহায্যে প্রতিটি অনুমোদিত ওষুধের সম্ভাব্য ব্যবহার বিশ্লেষণ করে।
গবেষণা থেকে বাস্তবতা
হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড. মারিঙ্কা জিটনিক বলেন, “A.I. শুধু গতি বাড়ায়নি, এটি গবেষণার ধরণই পাল্টে দিচ্ছে। একসঙ্গে হাজার হাজার ড্রাগ ও ডিজিজের মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ এখন সম্ভব হচ্ছে।”
যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামার এক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ড. ম্যাট মাইট বলেন, “আমরা A.I.-এর মাধ্যমে এক রোগীর বমিভাব কমাতে ইনহেল করা আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহলের কথা বলেছিলাম। বিশ্বাস করুন বা না করুন, সেটা সঙ্গে সঙ্গে কাজ করেছিল।”
তবুও, প্রশ্ন রয়ে যায়
অবশ্য সবসময় যে A.I. সঠিক হবে, এমন নয়। ড. জিটনিক বলেন, “কখনো কখনো A.I. এমন তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়, যা যথেষ্ট শক্তিশালী নয়।”
এর একটি উদাহরণ হলো ২০২৩ সালে জাপানে A.I.-এর প্রস্তাবিত একটি চিকিৎসা পদ্ধতি একটি শিশু রোগীর ক্ষেত্রে প্রয়োগের পর জটিল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যার ফলে সংশ্লিষ্ট গবেষণা বন্ধ করে দিতে হয়েছিল।
তাই চিকিৎসকদের সঠিক মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
তবে সামগ্রিকভাবে, আশার চিত্রটাই বড়।
ড. গ্রান্ট মিচেল বলেন, “এটা সেই A.I.-এর উদাহরণ যা আমাদের ভয় নয়, বরং আশাবাদী করে তোলে। এটা মানুষের জীবন বদলে দিচ্ছে।”
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সম্ভাবনা
বাংলাদেশেও রয়েছে হাজারো রোগী যারা চিকিৎসার জন্য লড়ছে, অনেক সময় নিরাশার সঙ্গে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যদি A.I.-ভিত্তিক drug repurposing মডেল চালু করা যায়, তাহলে অনেক রোগীর জীবনে পরিবর্তন আনা সম্ভব।
ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রফেসর ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, “এটা যদি বাংলাদেশে গবেষণা পর্যায়ে শুরু করা যায়, তাহলে ভবিষ্যতে এ দেশের রোগীদের জন্য নিজস্ব A.I. মডেল তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে যেসব ওষুধ বাজারে সহজলভ্য, সেগুলোর কার্যকারিতা নতুন রোগে পরীক্ষার মাধ্যমে জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বিপ্লব আনা সম্ভব।”
২০২৪ সালের ডিসেম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এক কর্মশালায় গবেষকরা ‘AI for Orphan Drugs’ নামে একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্পের কথা ঘোষণা দেন। এর আওতায় ১০টি পুরনো ওষুধের কার্যকারিতা A.I.-এর মাধ্যমে মূল্যায়নের কাজ চলছে।
শেষ কথা
জোসেফ কোটসের জীবন বাঁচানোর গল্পটা আসলে কেবল একটি গল্প নয়। এটা ভবিষ্যতের চিকিৎসাবিজ্ঞানের পথরেখা। এক সময় যে ওষুধ হয়তো ‘সাইড ইফেক্ট’ হিসেবে পরিগণিত হতো, আজ সেটাই কোনো রোগের মূল চিকিৎসা হয়ে উঠতে পারে—এই সত্য আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়।
এবং ভাবতে বাধ্য করে, হয়তো আমাদেরও নতুন করে বাঁচার রাস্তা খুঁজে নিতে হবে—মেশিনের সাহায্যে, মানুষের জন্য।
পাঠকের মতামত:
“আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশে এমন প্রযুক্তি প্রয়োগ করা গেলে হাজার হাজার জীবন রক্ষা করা সম্ভব,” — রুকাইয়া হোসেন, পাবলিক হেলথ গবেষক।
“A.I. যদি জীবন বাঁচাতে পারে, তাহলে সেটা আমাদের শত্রু নয়, বরং ভবিষ্যতের চিকিৎসক,” — মো. আরিফুজ্জামান, চিকিৎসা শিক্ষার্থী।







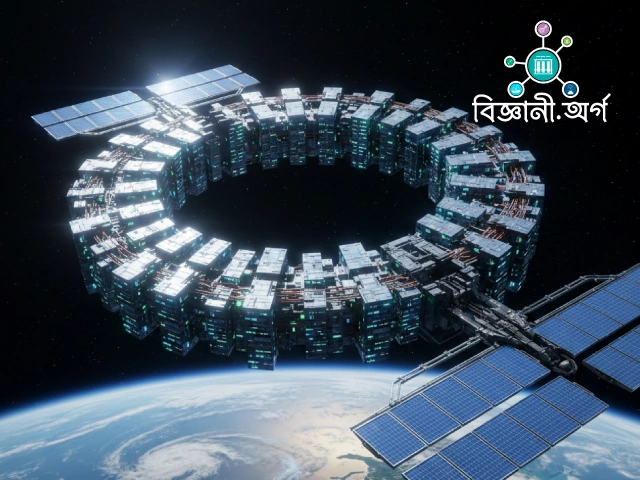
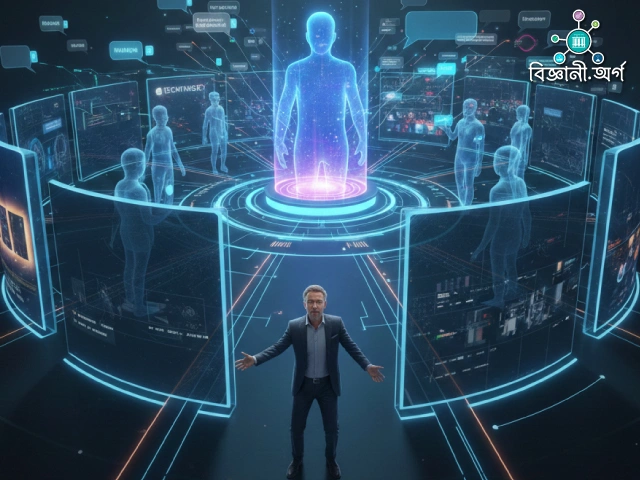
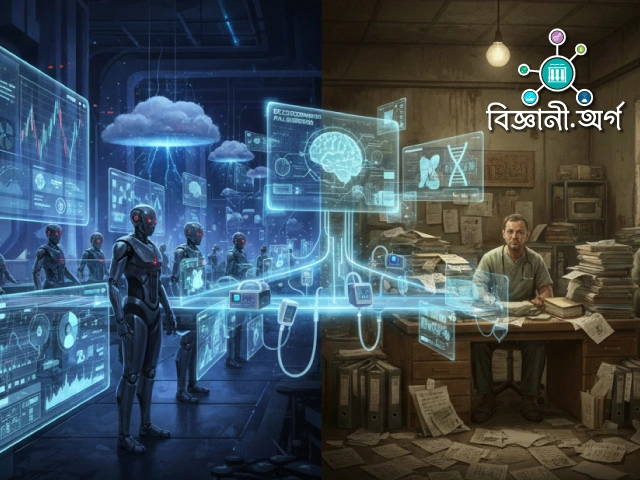

Leave a comment