আবুল বাসার
আধুনিক জার্মানি আর চেক রিপাবলিকের সীমান্ত এলাকা। ১৬ শতকের শুরুতে এই অঞ্চলকে দুই ভাগে বিভক্ত করে মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল রুক্ষ এক পর্বতশ্রেণি। এক পাশে স্যাক্সোনি আর আরেক পাশে বোহেমিয়া। পাহাড় ছাড়াও ছিল অভেদ্য এক বন। সেখানে রক্তলোলুপ নেকড়ে, ভালুকদের ছিল অভয়ারণ্য। তাদের চেয়েও আতঙ্কের ব্যাপার, হিংস্র আর ভয়ংকর ডাকাতদের আস্তানাও ছিল সেখানে। শিকারের খোঁজ পেলে অস্ত্র বাগিয়ে বুনো জন্তুর মতোই রে রে করে তেড়ে আসত তারা।
ওই শতকে এ অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয় বহু মূল্যবান এক ধাতু রুপা। যার পরিমাণ রাশি রাশি বলে মনে করা হয়েছিল। তার লোভে সব বিপদ তুচ্ছ করে এখানে একসময় নানা প্রান্ত থেকে পায়ে পায়ে হাজির হতে লাগল খনির ব্যবসায়ীরা। সঙ্গে জুটতে লাগল তাদের সাঙ্গপাঙ্গরাও। ইতিহাসে এটিই পরিচিত প্রথম ‘সিলভার রাশ’ নামে।
তাই সীমান্তের একেবারে কাছে ওয়াকিমথাল নামের ছোট্ট একটা শহর কদিনেই ইউরোপের সবচেয়ে বড় খনিকেন্দ্রে পরিণত হলো। ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় প্রবল উৎসাহে দলে দলে মানুষ ভিড় জমাতে লাগল এ শহরে। মাত্র কয়েক বছরে শহরটির জনসংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে দাঁড়াল ২০ হাজারে। এই খনি থেকে উত্তোলন করা রুপা দিয়ে কয়েন বানানো হতো, যাকে বলা হতো ওয়াকিমথেলার। লোকমুখে নামটি আস্তে আস্তে পরিণত হয় থেলারে। নামটি বিশ্বজুড়ে সেকালে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এখন সেই রৌপ্যমুদ্রার ব্যবহার না থাকলেও নামটি কিন্তু এখনো রয়েই গেছে, তবে একটু পরিবর্তিত রূপে। এই থেলারকে এখন আমরা বলি ডলার। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে মুদ্রা হিসেবে এখনো ব্যবহৃত হয় নামটি।
স্বাভাবিকভাবেই ওয়াকিমথেলার খনির রুপার পরিমাণ অফুরন্ত ছিল না। খনির সব রুপার মজুত ফুরিয়ে গেল মাত্র তিন দশকে। তার পরপর ভয়ংকর দানবের মতো আচমকা আঘাত হানল প্লেগ নামের মহামারি। বিপুল মানুষ ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে। এই ক্ষত শুকাতে না–শুকাতেই মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা। তাতে এককালের জমজমাটি শহরটিও প্রায় ধ্বংসস্তূপে রূপ নিল। লোকসংখ্যা কমতে কমতে নেমে এল প্রায় শূন্যের কোঠায়। ওয়াকিমথেলার পরিণত হলো ভুতুড়ে এক শহরে। সব জৌলুশ হারিয়ে আবার অস্বাস্থ্যকর এক শহর হিসেবেও বদনাম জুটল শহরটির কপালে। এ ভয়ে সেখানে তখন নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কেউ পা-ই মাড়াত না। অস্বাস্থ্যকর শহর হিসেবে কুখ্যাত হওয়ারও কারণ ছিল। শহরটিতে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের অনেক আগে থেকে অদ্ভুত আর রহস্যময় এক রোগে প্রায় অসুস্থ হতে দেখা যেত খনিশ্রমিকদের। কিন্তু তার কারণ কেউ জানত না।
রুপা ছাড়াও ওয়াকিমথেলারের খনিগুলোতে আরেকটি খনিজ পাওয়া যেত। চকচকে কালো এক খনিজ। তবে সেগুলো কাউকে সেভাবে আকর্ষণ করতে পারেনি। কারণ, একে সবাই দুর্ভাগ্যের পাথর বলেই জানত। তাই খনিজটির নামও দেওয়া হয়েছিল পিচব্লেন্ড। জার্মান এই শব্দের অর্থ ‘দুর্ভাগ্য বয়ে আনা খনিজ’ (জার্মান পিচ অর্থ দুর্ভাগ্য আর ব্লেন্ড অর্থ খনিজ)।
লোকমুখে খনিজটির কথা শোনেন সেকালের শৌখিন জার্মান রসায়নবিদ মার্টিন ক্লাপরথ। সেটা কী দিয়ে তৈরি, তা জানার কৌতূহল হলো তাঁর। সেটা ১৭৮৯ সালের কথা। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি দেখলেন, পিচব্লেন্ডে অদ্ভুত ধরনের একটা অর্ধধাতু আছে। বইপত্র, জার্নাল ঘেঁটে দেখলেন, এ ধাতুর কথা আগে কেউ বলেনি। অদ্ভুত ব্যাপার! তাই নতুন একটা ধাতু আবিষ্কারের কৃতিত্ব জুটল মার্টিনের কপালে। এর মাত্র ৮ বছর আগেই জ্যোতির্বিদ উইলিয়াম হার্শেল আবিষ্কার করেছেন ইউরেনাস নামের নতুন একটা গ্রহ। গ্রিকদের আকাশের দেবতার নামে নামকরণ করা হয় গ্রহটির। সেকালে ধারণা ছিল, এটিই সৌরজগতের শেষ গ্রহ। ইউরেনাস গ্রহের সম্মানে ধাতুটিকে তিনি নাম দেন ইউরেনিয়াম।
পরের শতকে এই পিচব্লেন্ড খনিজটি আবিষ্কৃত হয় ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া ও রোমানিয়ায়। ভিক্টোরিয়া যুগ শেষ হওয়ার আগে মৌলটির ভূতাত্ত্বিক এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশিত হয় কয়েক হাজার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। এতে বোঝা যায়, নতুন মৌলটি বিজ্ঞানীদের কেমন কৌতূহলের বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। এর পেছনে কারণও আছে অবশ্য। মৌলটি স্বর্ণের মতো ঘন। একে পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী মৌল বলে মনে ধারণা করেছিলেন সেকালের বিজ্ঞানীরা। মৌলটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণের আরেকটি কারণ হলো, এর অক্সাইড আর লবণে বিচিত্র সব রং পাওয়া যেত। সেগুলো ব্যবহার করা হতো কাচ, সিরামিক ও পোরসেলিনের বিভিন্ন জিনিসপত্র বানাতে। কারণ, এসব অক্সাইড আর লবণ ব্যবহারে সেগুলো কাচে আকর্ষণীয় প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করত, সিরামিক ও পোরসেলিনে কমলা, হলুদ, লাল, সবুজ ও কালো চাকচিক্য তৈরি করা যেত। অবশ্য এর কিছু কৌশল রোমান যুগ থেকেই অনেকের জানা ছিল। কিন্তু সে সময় এই আকর্ষণীয় রংচঙে এই সাজসজ্জার ভেতরে ঘাপটি মেরে বসে থাকা এক অদৃশ্য বিপদের কথা কেউ ঘুণাক্ষরে চিন্তাও করতে পারেনি।
ইউরেনিয়ামের এত সব আকর্ষণীয় ব্যবহারের মধ্যে হেনরি বেকেরেল আবিষ্কার করেন আরেকটি নাটকীয় সম্ভাবনা। ১৮৯৬ সালে প্রায় দুর্ঘটনাবশত তিনি দেখতে পান, মৌলটি থেকে একটা অদৃশ্য রশ্মি নির্গত হয়। আলোরোধী কালো কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখা ফটোগ্রাফিক প্লেটেও ঝাপসা দাগ সৃষ্টি করতে পারে সেই রশ্মি।
এ ঘটনার মাত্র মাস কয়েক আগে আরেকটি অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী হন জার্মান পদার্থবিদ উইলিয়াম রন্টজেন। ১৮৯৫ সালে জে জে টমসনের মতো বায়ুশূন্য টিউবে ক্যাথোড রে নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন তিনি। একটা উত্তপ্ত ধাতব ক্যাথোড থেকে বায়ুশূন্য টিউবের ভেতর ইলেকট্রনের স্রোত পাঠাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ খেয়াল করলেন, অন্য প্রান্তে রাখা একটা প্রতিপ্রভা ফসফর জাতীয় পর্দা এই রশ্মিতে দীপ্তিময় হয়ে উঠতে শুরু করেছে। আবার আরেকটি রহস্যময় রশ্মিও পাওয়া গেল এর মাধ্যমে। এবার বায়ুশূন্য টিউব থেকে রশ্মিটি বেরিয়ে ঘরের অন্য প্রান্তে চলে যেতে দেখলেন তিনি। টিউব আর পর্দার মাঝখানে একটা মোটা কালো কার্ড বসিয়ে দেওয়ার পরও পর্দাটি দীপ্তিময় হতে দেখা গেল। শেষ পর্যন্ত তিনি টিউবের সামনে তাঁর নিজের হাত রেখে পরীক্ষা করলেন। পরে ফটোগ্রাফিক প্লেটে নিজের হাতের কঙ্কাল দেখে তাঁর চোখ কপালে উঠল। তাঁর জানা ছিল না, বায়ুশূন্য টিউব থেকে ইলেকট্রনগুলো এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে তারা টিউবের কাচের পরমাণুতে আঘাত হানতেই ভিন্ন ধরনের বিকিরণের সৃষ্টি করেছিল।
শুরুতে রহস্যময়, ভুতুড়ে মনে হলেও এক সপ্তাহ পর রন্টজেন আবিষ্কার করলেন, ওই রশ্মির কিছু কাজেও লাগানো যায়। এটি ব্যবহার করে তিনি ফটোগ্রাফিক প্লেটে তাঁর স্ত্রীর হাতের কঙ্কালের ছবি তুললেন। তাঁর হাতের কঙ্কালগুলোর ঘন ছায়া দেখা গেল সেখানে। এমনকি তাঁর হাতে থাকা বিয়ের আংটির ছবিও পাওয়া গেল সেখানে। রন্টজেন এই ভুতুড়ে ছবি দেখে খুশি হলেও তাঁর স্ত্রী রীতিমতো ঘাবড়ে গেলেন। অবশ্য প্রাথমিক ভুতুড়ে ভাবটা কাটিয়ে উঠে এই আবিষ্কারের গুরুত্ব বেশ দ্রুতই অনুধাবন করতে পেরেছিল সেকালের চিকিৎসক সমাজ। কারণ, এর মাধ্যমে রোগীর ভাঙা হাড়ের অবস্থা বেশ ভালোমতো বোঝা যেত, কিংবা ঠিক কোথায় সার্জারি করতে হবে, তা–ও বুঝতে সুবিধা হতো চিকিৎসকদের। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই রশ্মি আসলে কী? কোনো অদৃশ্য আলো কি? শুরুতে এর উত্তর জানত না কেউই। সবার কাছে অজানা বলেই এর নাম দেওয়া হলো এক্স-রে বা এক্স-রশ্মি। আবার কেউ কেউ বিজ্ঞানী রন্টজেনের নামে একে রন্টজেন রশ্মি নামেও ডাকতে লাগল।
২.
হেনরি বেকেরেলের আবিষ্কৃত ইউরেনিয়াম রশ্মিতেও এক্স-রের মতো কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। বেকেরেল দেখতে পান, বিশেষ কিছু খনিজ পদার্থ থেকে বেরিয়ে আসা অদৃশ্য রশ্মি কালো কাগজ ভেদ করে চলে যেতে পারে। বিশেষ করে ইউরেনিয়াম ধাতুর নিউক্লিয়াস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকিরণ নির্গত হতে দেখেন তিনি। তাঁর নামানুসারে পরে এই বিকিরণের নাম দেওয়া হয় বেকেরেল রশ্মি। ফরাসি বিজ্ঞানী পিয়েরে কুরি এবং তাঁর স্ত্রী মেরি কুরি পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে দেখেন, শুধু কিছু নির্দিষ্ট পদার্থই এ রকম শক্তি বিকিরণ করতে পারে। সক্রিয় রশ্মির এই ঘটনাকে বোঝাতে তাঁরা ফরাসি রেডিও-অ্যাকটিফ (Radio-actif) শব্দটি ব্যবহার করেন। এখান থেকে পরে ইংরেজিতে Radioactive শব্দটির উৎপত্তি। এসব পদার্থের শক্তি বিকিরণের ধর্ম বোঝাতে তাঁরা প্রথম রেডিওঅ্যাক্টিভিটি (Radioactivity) শব্দটি ব্যবহার করেন, বাংলায় যার অনুবাদ করা হয়েছে তেজস্ক্রিয়তা। তেজস (অর্থ তেজ বা বিকিরণ) ও ক্রিয়া (কাজ) শব্দ দুটি একত্র হয়ে তেজস্ক্রিয় শব্দটি গঠিত হয়েছে। তবে পরমাণুর গঠন সঠিকভাবে আবিষ্কারের আগে রেডিওঅ্যাক্টিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তার কারণটা বোঝা যায়নি। তাই এ বিষয়ে আরও গবেষণার কথা ভাবলেন কুরি দম্পতি। কিন্তু সে জন্য দরকার উন্নত মানের গবেষণাগার। সেটা পাবেন কোথায়?
অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে একটা গবেষণাগারের ব্যবস্থা করতে পারলেন তাঁরা। ১৮৯৮ সালে প্যারিসের স্কুল আব ফিজিকস অ্যান্ড কেমিস্ট্রি কর্তৃপক্ষ তাদের গবেষণাগার ব্যবহারের অনুমতি দেয় কুরি দম্পতিকে। সেটা ছিল আসলে নামমাত্রই গবেষণাগার। আধুনিক গবেষণাগারের সঙ্গে তুলনা করলে সেটাকে বলা চলে স্রেফ গোয়ালঘর। কিংবা আস্তাবলও বলা চলে। ঘরের মেঝে আর ছাদটা ছিল ভাঙাচোরা, বৃষ্টি হলেই পানিতে ভেসে যেত ঘরটি। আর গ্রীষ্মে প্রচণ্ড গরমে সেই ঘরে টেকা দায় হয়ে পড়ত। আর শীতকালের কথা কী বলব! ভাঙাচোরা ঘরটির এখান-ওখানের চোরাগোপ্তা ফাঁকফোকর দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ত কনকনে বাতাস। তীব্র ঠান্ডায় জমে যাওয়ার মতো অবস্থা হতো ঘরের বাসিন্দাদের। আবার গ্যাস বার্নার আর রাসায়নিকের উৎকট গন্ধে পরিস্থিতি হয়ে উঠত আরও ভয়াবহ।
জার্মান রসায়নবিদ উইলহেম ওস্টওয়াল একবার কুরি দম্পতির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন প্যারিসের সেই গবেষণাগারে। তাঁর ভাষায়, গবেষণাগারটাকে আস্তাবল আর আলুর গুদামের সংমিশ্রণ ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। রাসায়নিক যন্ত্রপাতি আর কাজের জন্য একটা টেবিল চোখে পড়ার আগপর্যন্ত সেখানে যে কোনো গবেষণাকর্ম চলতে পারে, তা ভাবতেও পারেননি তিনি। অথচ সেই গবেষণাগারে রাত–দিন অমানুষিক পরিশ্রম করে পিচব্লেন্ড থেকে ইউরেনিয়াম আলাদা করতে শুরু করেন তাঁরা।
দিনের পর দিন রুটিন মেনে কাজ করে যেতে থাকেন কুরি দম্পতি। পরিত্যক্ত ওয়াকিমথাল খনির আশপাশে গাদা করা পিচব্লেন্ড গবেষণাগারে আনা হতো বস্তায় ভরে। কাজের শুরুতেই তা থেকে কাদা, ঘাস আর পাইনের পাতা পরিষ্কার করতেন মেরি। সেগুলো ভেঙে ভেঙে পাউডারের মতো মিহি ধুলায় পরিণত করা হতো। সেগুলো এরপর একটা তরলে উত্তপ্ত করে ছেঁকে আরও পরিশুদ্ধ করা হতো। পরে সেগুলো থেকে অদরকারি বস্তুগুলো বাদ দিতে ধোয়া হতো অ্যাসিডে। এরপর চলত ইলেকট্রোলাইসিস বা তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া। এভাবে কয়েক মাসের টানা পরিশ্রমে যেটুকু বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম পাওয়া যেত, তা যেন তালকে তিল করার মতো। মাত্র কয়েক গ্রাম ইউরেনিয়াম। ‘উত্তপ্ত তরলে আমার নিজের দেহের সমান লোহার রডের চামচ দিয়ে নাড়াচাড়া করতাম। মাঝেমধ্যে এ কাজ করতে সারা দিন লেগে যেত। দিন শেষে আমার শরীর ভেঙে আসত।’—সে সময়ের স্মৃতিচারণা করে লিখেছেন মেরি। অবশ্য এ নিয়েও তাঁর কোনো অভিযোগ ছিল না। কারণ, বৈজ্ঞানিক এই গবেষণায় তাঁর সঙ্গে তখন ছায়ার মতো থাকতেন তাঁর স্বামী পিয়েরে। মেরি লিখেছেন, ‘সেই দুর্বিষহ পুরোনো কুঁড়েঘরে আমাদের যৌথ জীবনের সবচেয়ে ভালো এবং সুখী বছরগুলো কাটিয়েছি আমরা।’ অচিরেই তাঁদের আমানবিক পরিশ্রমের ফলও মিলল হাতেনাতে।
অদ্ভুত ব্যাপার হলো, পরিশোধিত ইউরেনিয়ামের চেয়ে অপরিশোধিত পিচব্লেন্ডকে বেশি তেজস্ক্রিয় বলে মনে হলো তাঁদের কাছে। পিয়েরে আর মেরি সন্দেহ করলেন, পিচব্লেন্ড আকরিকে ইউরেনিয়াম ছাড়াও আরও অন্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকতে পারে। সেগুলো হয়তো তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। এক বছরের মাথায় আনকোরা দুটি তেজস্ক্রিয় মৌল আবিষ্কার করে সেই সন্দেহ সত্যি প্রমাণ করলেন কুরি দম্পতি।
কুরির দেশ পোল্যান্ডের কথা স্মরণে রেখে এদের একটি মৌলের নাম দেওয়া হলো পোলোনিয়াম (কারণ, পোল্যান্ডকে ল্যাটিনে বলা হয় পোলোনিয়া)। আরেকটির নাম দেওয়া হয় রেডিয়াম। পিচব্লেন্ড খনিজ থেকে ১৮৯৮ সালের ২১ ডিসেম্বর মৌলটি আবিষ্কৃত হয়। ২৬ ডিসেম্বর ফরাসি বিজ্ঞান একাডেমিতে এই আবিষ্কারের ঘোষণা দেন কুরি দম্পতি। প্রায় এক বছর পর মৌলটির নামকরণ করা হয় রেডিয়াম। শব্দটির উৎস ল্যাটিন রেডিয়াস (রশ্মি) থেকে। রশ্মি রূপে মৌলটি শক্তি নির্গত করতে পারে বলেই এমন নামকরণ। কুরির মতে, ইউরেনিয়ামের চেয়ে রেডিয়ামের তেজস্ক্রিয় শক্তি দুই লাখ গুণ বেশি। আরও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কুরি বুঝতে পারেন, রাসায়নিক মৌলের ওপর তেজস্ক্রিয়তা নির্ভর করে না। অর্থাৎ পোলিনিয়াম, রেডিয়াম বা ইউরেনিয়াম যা–ই হোক না কেন, তেজস্ক্রিয়তা নিঃসরণের সত্যিকার একক হলো পরমাণু।
কিন্তু প্রশ্ন হলো, তেজস্ক্রিয় মৌলের ভেতর শক্তি আসে কোথা থেকে? পিয়েরে অনুমান করেছিলেন, তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো বাইরের কোনো বিকিরণ থেকে শক্তি ধার করে তা নিঃসৃত করে। এটাই ছিল সেকালের স্বস্তিদায়ক এবং প্রচলিত ধারণা। কোনো বস্তুকে কিছুক্ষণ উত্তপ্ত করা হলে কিছু পরে বস্তুটি তাপ নিঃসরণ করতে থাকে। তবে পিয়েরে আর কুরি এটাও জানতেন, তাঁরা যেসব তেজস্ক্রিয় মৌল নিয়ে কাজ করেছেন, সেগুলোর তাপশক্তি সাধারণ তাপশক্তির মতো নয়। কারণ, সেগুলোকে স্পর্শ করলেই গরম লাগত। দেখে মনে হতো, তেজস্ক্রিয় মৌলগুলো তাঁদের কাছ থেকে শক্তি টেনে নিয়ে তা নিঃসরণ করত। মাত্র কয়েক বছরে রেডিয়াম যে পরিমাণ তাপশক্তি নিঃসরণ করতে পারে, তা সমপরিমাণ অন্য যেকোনো বস্তুর রাসায়নিক বিক্রিয়ার তুলনায় অনেক অনেক গুণ বেশি।’
১৯০৩ সালে কঠোর পরিশ্রমের ফল পেলেন পিয়েরে ও মেরি কুরি দম্পতি। হেনরি বেকেরেলসহ তাঁদের পদার্থবিজ্ঞানে ওই বছর নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলো। পুরস্কারের অর্থ আর্থিকভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সহায়তা করল তাঁদের। সে বছরই ফ্রান্সের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর হিসেবে দায়িত্ব পেলেন ৪৫ বছর বয়স্ক পিয়েরে। সঠিকভাবে বলতে গেলে, আসলে তাঁর সম্মানে বিশেষভাবে সৃষ্টি করা হলো পদটি। আর মেরি কুরি বনে গেলেন তাঁর সহকারী। শিগগিরই আরেকটি সুখবর এল তাঁদের পরিবারে। জন্ম নিল তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান ইভ। তাঁদের প্রথম সন্তান আইরিনের বয়স তখন ছয় বছর।
তবে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর খ্যাতির কিছু বিড়ম্বনাও সহ্য করতে হলো তাঁদের। খবরের কাগজ থেকে বারবার সাক্ষাৎকার নেওয়ার অনুরোধ আর এখানে-ওখানে যখন-তখন অতিথি হওয়ার আমন্ত্রণ। শুরুতে ভালো লাগলেও অচিরেই বিরক্ত হলেন তাঁরা। এতে তাঁদের উপকারের বদলে গবেষণাকাজের ক্ষতি হচ্ছিল। তবে কাজের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছিল এত দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির কারণে ব্যথা আর অসুস্থতা ও অপুষ্টির কারণে। এ অসুস্থতার পেছনে অনেকাংশেই যে তেজস্ক্রিয় মৌলগুলো দায়ী, তা বলাই বাহুল্য।
কুরি দম্পতি সন্দেহ করেছিলেন, তাঁদের দুজনের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, তেজস্ক্রিয় মৌলের প্রভাবে আরও খারাপ অবস্থাও হতে পারে। তাই নোবেল বক্তৃতায় এ বিষয়ে হুঁশিয়ারিও করেন পিয়েরে কুরি। কিন্তু কেউই বলতে গেলে তাঁর কথাগুলোকে গুরুত্ব দেননি তখন। নোবেল বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, ‘মাত্র কয়েক গ্রাম রেডিয়াম লবণের ছোট অ্যাম্পুল কারও পকেটে থাকলে অল্প কয়েক ঘণ্টা তেমন কোনো খারাপ প্রভাব হয়তো দেখা যাবে না, কিন্তু কয়েক দিন থাকলে দেহের বহিঃত্বকে লালচে হয়ে যায়। এরপর সেখানে ঘায়ের মতো হয়ে যায়, যা সারানো খুব কঠিন। এর প্রভাবে প্যারালাইসিস ও মৃত্যুও হতে পারে। সে কারণে অবশ্যই ঘন সিসার তৈরি বাক্সে রেডিয়াম বহন করতে হবে।’
একবার নিজের দেহের সঙ্গে এক প্যাকেট রেডিয়াম কয়েক ঘণ্টা বেঁধে রেখেছিলেন পিয়ের কুরি। রেডিয়াম ব্যবহার করে ক্যানসারের কোষ ধ্বংস করা যায় কি না, সেটি এভাবে পরীক্ষা করেছিলেন তিনি। এদিকে বিছানায় বালিশের পাশে এক শিশি রেডিয়াম রাখতেন মেরি কুরি। মাত্র এক গ্রাম রেডিয়াম আলাদা করতে তাঁদের ৭ টন পিচব্লেন্ড লেগেছিল। মজার ব্যাপার হলো, অন্ধকারে নিজেদের কীর্তি জ্বলজ্বল করে জ্বলতে দেখতে বেশ পছন্দ করতেন মেরি। মেরি লিখেছেন, ‘আমাদের আনন্দের একটি ঘটনা ছিল রাতের বেলা নিজের কাজের ঘরে যাওয়া। সেখানে বোতল বা ক্যাপসুলের ভেতরে থাকা আমাদের তৈরি করা পদার্থগুলো দুর্বলভাবে আলো দিত। সেটা খুবই চমৎকার দৃশ্য। আমাদের কাছে সেগুলো সব সময়ই নতুন মনে হতো। আলোকোজ্জ্বল টিউবগুলোকে রূপকথার পরি মনে হতো আমাদের কাছে।’
৩.
১৯০৬ সালের ১৯ এপ্রিল। বৃহস্পতিবার। সেদিন বিজ্ঞানের অধ্যাপকদের সঙ্গে এক মিটিং শেষে নিজের প্রকাশিতব্য একটা বইয়ের প্রুফ কপি নিয়ে প্রকাশকের কাছে যাচ্ছিলেন পিয়েরে কুরি। এরপর কাজ শেষে পাশের একটা লাইব্রেরিতেও যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। আবার বিকেলে মেরিকে সঙ্গে নিয়ে বন্ধুদের আড্ডায় যোগ দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন।
প্রচণ্ড বৃষ্টি মাথায় নিয়ে প্রকাশকের দপ্তরে গিয়ে বিরক্ত আর হতাশ হলেন পিয়েরে। দেখলেন, দরজা বন্ধ। ভেতরেও কেউ নেই। ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্যে একরাশ হতাশা নিয়ে রাস্তায় খানিকটা পিছিয়ে এলেন তিনি। বৃষ্টির কারণে দৃষ্টি ঝাপসা হয়েই এসেছিল বোধ হয়, নইলে সামরিক সরঞ্জাম বোঝাই আস্ত ঘোড়ার ওয়াগনটা তাঁর চোখে পড়বে না কেন! কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুহূর্তেই ছয় টনি ওয়াগনটার চাকার নিচে পড়লেন তিনি। ঘটনাস্থলে সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেলেন তেজস্ক্রিয়তার অন্যতম পথিকৃৎ পদার্থবিজ্ঞানী পিয়েরে কুরি।
প্রিয়জনকে হারিয়ে দুঃখ-হতাশার মধ্যে দাঁতে দাঁত চেপে যেন নিজের ভেতর সব শক্তি জড়ো করলেন মেরি। পিয়েরের সঙ্গে যে কাজ শুরু করেছিলেন, তা একাই চালিয়ে যেতে লাগলেন তিনি। শোক ভুলতেই কাজে মনোযোগ বাড়িয়ে দিলেন। একসময় সরবোনের এক গবেষণাগারের প্রধান হলেন তিনি। সরবোনের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সেবারই প্রথম কোনো নারী লেকচারার এল। পিয়েরের বরাবর গবেষণা প্রবন্ধ লিখে একটু সান্ত্বনা পেতেন কুরি, যেন সবার আড়ালে থেকে তখনো নিজের পদেই কাজ করে যাচ্ছেন পিয়েরে। মেরি লিখেছেন, ‘তখন কোনো কিছুতে নজর না দিয়ে আমি সম্মোহিতের মতো হেঁটে যেতাম। নিজেকে আমি হত্যা করিনি। এমনকি আত্মহত্যারও কোনো ইচ্ছা জাগেনি। কিন্তু এত সব ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে একটাও কি আমাকে আমার প্রিয়তমর মতো ভাগ্য বরণ করতে দিতে পারত না?’
নিজের শিক্ষার্থীদের চোখেও আকর্ষণীয় ছিলেন মেরি কুরি। তাঁদেরই একজন স্মৃতিচারণা করেছেন, ‘তাঁকে খুব মলিন দেখাত। মুখটা নির্বিকার আর কালো পোশাকে খুবই সাধারণ দেখাত তাঁকে। কিন্তু ভুল ভাঙত তাঁর উজ্জ্বল বড় কপালটা দেখলে। তার ওপরেই একটা মুকুটের মতো মনে হতো অঢেল ছাইরঙা চুলগুলোকে। সেগুলোকে শক্ত করে পেছনে বেঁধে রাখলেও নিজের রূপ লুকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হতেন তিনি।’
সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯০৮ সালে পূর্ণ প্রফেসরের মর্যাদা পান মেরি কুরি। এরপর দ্বিতীয়বারের মতো নোবেল বিজয়ীর তালিকায় নাম ওঠে ১৯১১ সালে। এবার রসায়নে। রেডিয়াম আবিষ্কারের কারণে এই সম্মান। এর তিন বছর পরই শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ এক্স-রে ইউনিট নিয়ে আহত সেনাদের সহায়তায় এগিয়ে যান তিনি। এর মাধ্যমে অসংখ্য আহত সেনার জীবন বাঁচান মেরি।
পিয়েরেকে হারানোর শোকের স্মৃতি যেন হুট করে একদিন কাটিয়ে উঠলেন মেরি। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগে এক স্ক্যান্ডালে জড়িয়ে পড়েন তিনি। সেকালের বিধবাদের মতো নিজের রোমান্টিক জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন না মেরি। শুধু স্বামী মারা গেছে বলেই শোকের সাগরে ডুবে যেতে হবে, এমনটা বিশ্বাস ছিল না তাঁর। কারণ, তাঁরও তো জীবনের অনেকটা সময় বাকি আছে। ১৯১০ সালের দিকে দেখা গেল, বিধবাদের জন্য প্রচলিত কালো পোশাক ছেড়ে তিনি গায়ে চড়িয়েছেন রক্তগোলাপখচিত সাদা গাউন। আবার প্রেমে পড়লেন তিনি। এবারের প্রেমিক পিয়েরের সাবেক সহকর্মী পল ল্যাঞ্জভাঁ। শুধু মন দেওয়া-নেওয়া নয়, উদ্দাম প্রেমে জড়ালেন তিনি। শিগগিরই সরবোনের পাশেই একটা অ্যাপার্টমেন্টে দম্পতির মতো থাকতেও শুরু করলেন দুজন। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, ল্যাঞ্জভাঁ তখন স্ত্রীসহ চার সন্তানের জনক।
দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ঘোষণার পর মেরির জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠল। এ সময় তিনি অনেকের কাছেই কুখ্যাত হয়ে উঠলেন। কারণ, নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় তখন শুধু প্যারিস নয়, বলতে গেলে গোটা বিশ্বই তাঁর নাম জানে। পত্রপত্রিকায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অনেক ঘটনাই লেখা হতে থাকে। ঢিঁ ঢিঁ পড়ে গেল চারদিকে। গোটা বিশ্ববাসীই যেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে হামলে পড়ল। ফ্রান্সের জাতীয়বাদীরা তাঁকে পোলিশ নাগরিক হিসেবে সাব্যস্ত করল, নারীবাদ–বিরোধীরাও তাঁর ওপর খেপে উঠল—বিজ্ঞানের রাজ্যে এমন ব্যক্তিগত জীবনের লজ্জাজনক বিষয় ঢুকে পড়ায়। লোকজনও ঠিক বুঝতে পারছিল না, মেরি কুরি কোনো অশুভ মূর্তি, নাকি আকর্ষণীয় বৈজ্ঞানিক নায়িকা।
এ অবস্থায় স্টকহোমে ১৯১১ সালের নোবেল পুরস্কার নিতে যেতে নিষেধ করে মেরিকে একটা চিঠি লেখে ফ্রেঞ্চ ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস। জবাবে তিনি ভদ্রভাবে লেখেন, ‘পুরস্কারটা দেওয়া হচ্ছে রেডিয়াম আর পোলোনিয়াম আবিষ্কারের জন্য। আমার বিশ্বাস, এর মধ্যে আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং আমার ব্যক্তিগত জীবনের কোনো যোগাযোগ নেই। বৈজ্ঞানিক কাজের মূল্য কুৎসা আর পরনিন্দা দিয়ে প্রভাবিত হওয়া উচিত, এই ধারণা আমি মানতে পারছি না।’ ফরাসি একাডেমি মেরির এই অনবদ্য যুক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। তারপর যথাযথভাবে পুরস্কৃত করা হলো তাঁকে।
৪.
তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে দিনের পর কাজ করার কারণে একসময় লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত হন মেরি। আসলে তাঁর দেহে বিকিরণের প্রভাব ফুটে উঠতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। রোগে ভুগে ১৯৩৪ সালের ৪ জুলাই ৬৬ বছর বয়সে মারা যান প্রথম নারী নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী মেরি কুরি। তাঁর সময়ের অন্যান্য নারীর মতো তাঁর আয়ু নাটকীয়ভাবে কম বলা যায় না।
তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিরূপ প্রভাব শুরুতে কুরিও বুঝতে পারেননি। তাই নিজের বেডরুমে সেগুলো কাছে নিয়ে ঘুমাতেন, অন্ধকারে আলো জ্বলা দেখে মুগ্ধ হতেন। তবে মেরিকে একা দোষ দিয়ে লাভ নেই। তাঁর মতোই রেডিয়ামের এই আলোয় একসময় মেতে উঠেছিল ইউরোপ-আমেরিকার আরও অনেকে। রেডিয়াম পানিতে মেশালে তা অন্ধকারে জ্বলতে থাকে। তাই মৌলটি আবিষ্কারের পর একে বেশ কিছু রোগ নিরাময়ের অলৌকিক টনিক হিসেবে ভাবল কেউ কেউ। হাতুড়ে ডাক্তাররা অচিরেই লুফে নিল রেডিয়ামকে। তাদের কাছে নতুন এক মহৌষধ হিসেবে ধরা দিল মৌলটি। সে কারণে বিশ শতকের শুরুর দিকে আশ্চর্য ওষুধের উপাদান হিসেবে রেডিয়াম ব্যবহার করা হতো।
এ সময়ই রেডিয়াম চকলেট, রেডিয়াম ওয়াটার, রেডিয়াম ব্রেড নামের নিত্যনতুন পণ্যে বাজার ছেয়ে গেল। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল রেডিঅ্যান্ডোক্রিনেটর নামের একটি যন্ত্র। যৌবন ধরে রাখতে, সতেজ জীবন লাভের আশায় অনেকেই এই দামি যন্ত্রটি পেটের নিচে বেঁধে রাতে ঘুমাত। প্রায় ক্রেডিট কার্ডের সমান এই যন্ত্রে অনেকখানি রেডিয়াম ব্যবহার করা হতো। তাতে এটি বানানোর খরচও ছিল বেশি। তাই দামটাও অনেক বেশি হওয়ায় এর প্রধান ক্রেতা ছিল ধনীরা। অন্যদিকে সাধারণের জন্য সস্তায় কিছু ভুয়া রেডিঅ্যান্ডোক্রিনেটর যন্ত্রও বাজারে পাওয়া যেত। এগুলো রেডিয়াম থাকত খুব অল্প কিংবা কোনো কোনোটাতে থাকতই না। এই সস্তা যন্ত্রগুলোর স্বাভাবিকভাবেই ক্রেতা ছিল যৌবন ধরে রাখতে আগ্রহী গরিব বা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি। মজার ব্যাপার হলো, এই দরিদ্ররাই ছিল আসলে ভাগ্যবান। কারণ, তাদের যন্ত্রে রেডিয়াম কম থাকায় বা একেবারেই না থাকায় তাদের দেহে ক্ষতির পরিমাণও ছিল অনেক কম।
অন্ধকারে ঘড়ি দেখার সুবিধার্থে সে সময় ঘড়ির ডায়ালে রেডিয়াম মিশ্রিত রং ব্যবহার করা হতো। এসব রঙে প্রায় এক মাইক্রোগ্রাম রেডিয়াম থাকত। আর এ কাজে যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি কারখানায় তরুণ নারী কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছিল। ঘড়ির ডায়ালে রেডিয়ামমিশ্রিত আলোকপ্রভাযুক্ত রঙে রাঙাতে বিশেষ ধরনের ব্রাশ ব্যবহার করা হতো। ব্রাশগুলোর ডগা ঠিক রাখতে জিহ্বা দিয়ে চাটার নির্দেশনা ছিল ওই মেয়েদের। ইতিহাসে রেডিয়াম গার্ল নামে পরিচিত এই মেয়েদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, রেডিয়াম কোনো ক্ষতিকর পদার্থ নয়।
এই আশ্বাস পেয়ে অনেকে ফ্যাশন হিসেবেও রেডিয়াম ব্যবহার শুরু করছিল। এর অংশ হিসেবে অনেকেই চুলে, চোখের পাতায়, নখে, ঠোঁটে রেডিয়ামের প্রলেপ লাগাত। এমনকি দাঁতেও রেডিয়াম লাগাত অনেকে, যাতে অন্ধকারে সেখান থেকে প্রভা ছড়ায়। কিছুদিন পরই এর ফলাফল হাতে হাতে পেয়েছিল রেডিয়াম ব্যবহারকারীরা। শুরুতেই অনেকের দাঁত পড়ে গেল, দেহে রক্তশূন্যতা দেখা দিল। এ ছাড়া চোয়ালে পচন, তারপর ক্যানসার ধরা পড়ল। নিউ জার্সির একটি কারখানায় এভাবে শতাধিক মেয়ে মারা গিয়েছিল। এসব ঘটনায় একসময় হুঁশ ফেরে মানুষের। এরপর ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে যুক্তরাষ্ট্রের ফেলা পারমাণবিক বোমায় তেজস্ক্রিয় পদার্থের চরম ভয়াবহ রূপ দেখে মানুষ। সেটা আরেক গল্প।


লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, বিজ্ঞানচিন্তা
সূত্র:
♣ ইন সার্চ অব কোয়ান্টাম ক্যাট/ জন গ্রিবিন
♣ অ্যাটম/ পিয়ার্স বিজোনি
♣ আবিষ্কারের নেশায়/ আবদুল্লাহ আল মুতি
♣ উইকিপিডিয়া
♣ https://www.facebook.com/bigganchinta/
♣ http://visioncreatesvalue.blogspot.com/2020/08/blog-post.html
♥♪♥
VCV Technical Communications:
Received From Abul Bashar via email: 20200902
Converted by Unicode Converter – Bijoy to Unicode: 20200902
Published: Abul Bashar, FB Biggani.org Group: 20200822
Last Edited: 20200904
Last Updated: 20201003


































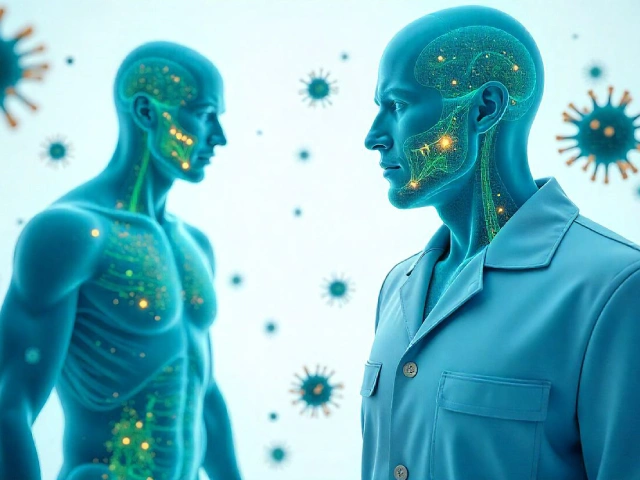



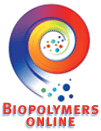











Leave a comment