যখন আমরা কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে পাই না, তখন সাধারণত আমরা ধরে নিই—সমস্যাটা আরও জটিল বা গভীর। অথচ অনেক সময় সমস্যার প্রকৃতি নয়, বরং সমস্যাটিকে দেখার পদ্ধতিই আমাদের মূল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞানী ও গবেষক ডোনেলা হ. মিডোজ এই দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন তার বই Thinking in Systems-এ। তিনি দেখিয়েছেন, আমাদের চারপাশের জগতটি শুধুই আলাদা আলাদা উপাদানে গঠিত নয়, বরং সেগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রতিক্রিয়াগুলোর একটি জটিল নকশায় তৈরি।
একটি সমাজব্যবস্থা, একটি বাস্তুতন্ত্র, একটি শহরের পরিবহন ব্যবস্থা, এমনকি একটি পরিবারের অভ্যন্তরীণ গতিশীলতাও আসলে একেকটি সিস্টেম—যার প্রতিটি উপাদান অন্য উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং একটির পরিবর্তন অন্যকে প্রভাবিত করে। মিডোজের মতে, আমরা যদি কোনো জটিল সমস্যার সমাধান চাই, তবে প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে, আমরা সেই সিস্টেমটির কোন অংশে দাঁড়িয়ে আছি এবং কোন উপাদানগুলো একে অন্যকে চালিত করছে।
বাংলাদেশের মতো একটি দেশ, যেখানে পরিবেশ, জনসংখ্যা, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষা—সবকিছুই একে অপরের ওপর নির্ভরশীল, সেখানে সিস্টেম চিন্তা শুধুমাত্র বিজ্ঞানীদের জন্য নয়, বরং নীতিনির্ধারকদের, উন্নয়নকর্মীদের এবং সাধারণ মানুষের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। ধরুন, আপনি যদি কেবলমাত্র রাজধানীতে যানজট কমাতে চান, তবে আপনি নতুন রাস্তা নির্মাণের কথা ভাববেন। কিন্তু আপনি যদি পুরো সিস্টেমটি বোঝেন—যেখানে মানুষ কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কোন সময়ে বেশি যানবাহন চলাচল করে, পাবলিক ট্রান্সপোর্টের অবস্থান কেমন—তবে আপনি দেখতে পাবেন, সমাধানটি শুধুমাত্র অবকাঠামো নয়, বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত।
মিডোজ তাঁর লেখায় বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন সিস্টেমের ফিডব্যাক লুপগুলোর ওপর। সহজভাবে বললে, ফিডব্যাক লুপ হলো এমন এক প্রক্রিয়া, যেখানে একটি পরিবর্তন আবার নিজের উৎসকে প্রভাবিত করে। যেমন, যখন কোন এলাকায় পানি সরবরাহ বাড়ে, তখন কৃষিকাজ বাড়ে। কিন্তু যদি সেটি অনিয়ন্ত্রিত হয়, তবে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর কমে যায় এবং পরবর্তীতে পানির ঘাটতি দেখা দেয়। এভাবেই একটি পজিটিভ পরিবর্তনও নেতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারে, যদি আমরা সিস্টেমটির ফিডব্যাক বোঝার চেষ্টা না করি।
বাংলাদেশের কৃষিনীতিতে একসময় সবুজ বিপ্লবের আদলে উচ্চফলনশীল বীজ ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। শুরুতে উৎপাদন বেড়েছিল, কিন্তু পরে দেখা গেল মাটির উর্বরতা কমে যাচ্ছে, পানির দূষণ বাড়ছে, কৃষকের খরচ বাড়ছে। মিডোজ হয়তো বলতেন, এটি একটি সিস্টেমের ‘লেটেন্ট ফিডব্যাক’—যা আমরা দেখতে পাই অনেক পরে, কিন্তু তখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এই বাস্তবতা আমাদের শেখায়, কোনো সমস্যার স্বল্পমেয়াদি সমাধান খুঁজতে গিয়ে দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়াগুলো উপেক্ষা করলে সেগুলোই একদিন আরও বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।
সিস্টেম চিন্তার অন্যতম শক্তিশালী দিক হলো এর ‘লিভারেজ পয়েন্ট’ চিহ্নিত করার ক্ষমতা। একটি জটিল সিস্টেমে সব জায়গায় হস্তক্ষেপ সমান ফল দেয় না। কিছু কিছু জায়গায় ছোট্ট পরিবর্তন করলেই পুরো সিস্টেমে বড় রকমের প্রভাব পড়তে পারে। ধরুন, শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি আপনি শুধু পরীক্ষার পদ্ধতিই বদলে দেন—যেমন মুখস্থের বদলে বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন যোগ করেন—তবে শিক্ষার্থীর ভাবনার প্যাটার্ন, শিক্ষকতার ধরন, এমনকি অভিভাবকের প্রত্যাশাও বদলাতে পারে। মিডোজ এটিকেই বলতেন ‘লিভারেজ’। মূল কথা হলো, আপনি যদি সঠিক জায়গায় পরিবর্তন আনেন, তবে সেটি অনেক বৃহৎ প্রভাব ফেলতে পারে, অনেকটা ডোমিনো এফেক্টের মতো।
সিস্টেম চিন্তা আমাদের একটি নতুন মনস্তত্ত্বও দেয়। এটি আমাদের শেখায়, জটিলতা মানেই সমস্যার সমাধান নেই—বরং সেটি মানে হলো, আমাদের আরও ভালোভাবে দেখতে হবে, বুঝতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যদি শিক্ষার্থীদের সিস্টেম চিন্তার ক্ষমতা তৈরি করতে পারে, তবে তারা জীবনের নানা সমস্যা—হোক তা প্রযুক্তি, সমাজ বা পরিবেশ—এসবকে কেবল সমস্যা হিসেবে না দেখে একে একটি প্যাটার্ন হিসেবে বুঝতে শিখবে। এর ফলে ভবিষ্যতের নীতিনির্ধারক, বিজ্ঞানী কিংবা উদ্যোক্তারা হবে আরও দূরদর্শী, আরও সমন্বিত চিন্তার অধিকারী।
মিডোজ তাঁর জীবন ও লেখার মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছেন, সত্যিকারের পরিবর্তন আসে তখনই, যখন মানুষ বুঝতে শেখে যে সে একটি বড় ব্যবস্থার অংশ। তিনি কোনো সময় প্রযুক্তিকে অস্বীকার করেননি, বরং প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু তাঁর মূল যুক্তি ছিল—প্রযুক্তির চেয়ে বড় হলো দৃষ্টিভঙ্গি। আপনি যদি সমস্যাকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বদলান, তবে সমাধান অনেক সময় নিজেই সামনে এসে দাঁড়ায়।
বিশ্ব আজ জলবায়ু পরিবর্তন, স্বাস্থ্য সংকট, আর্থ-সামাজিক বৈষম্য—এসব একত্রিত সমস্যা নিয়ে লড়ছে। এসব সমস্যা কোনো একক জাতি বা বিজ্ঞান দিয়ে সমাধান সম্ভব নয়। মিডোজের ‘Thinking in Systems’ আমাদের শেখায়—কিভাবে পারস্পরিক সংযোগ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করে, তথ্য ও ফিডব্যাক লুপের মাধ্যমে, ধাপে ধাপে একটি জটিল ব্যবস্থাকে বোঝা ও পুনর্গঠন করা যায়। এই ধারণাটি এখন শুধু গবেষণার বিষয় নয়, বরং একটি বাঁচার কৌশল।
বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে, যেখানে সীমিত সম্পদ, ঘনবসতি ও বহুবিধ সামাজিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সেখানে সিস্টেম চিন্তা একটি অপরিহার্য দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠতে পারে। শুধু প্রযুক্তিনির্ভর সমাধান নয়, বরং পারস্পরিক সম্পর্ক, দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ও পরিবর্তনের জায়গা খুঁজে বের করাই হতে পারে আমাদের টেকসই উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি।
ডোনেলা হ. মিডোজ হয়তো আমাদের মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, পৃথিবীটা আসলে এক বিশাল, পরস্পর-সংযুক্ত জীবন্ত সিস্টেম। আর আমরা, তার অংশ হয়ে, কেবল পর্যবেক্ষক নই—আমরাই সেই সিস্টেমকে গঠন ও পুনর্গঠনের কারিগর। আমাদের কাজ হলো সেই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, যেখান থেকে আমরা সমাধানের পথ খুঁজে পাই—না যে কেবল সমস্যার গভীরতা বেড়েই চলে, বরং নতুন এক পথও খুলে যায়।






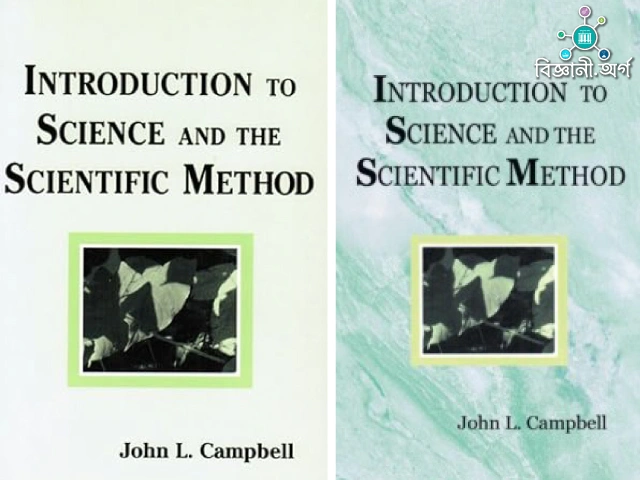

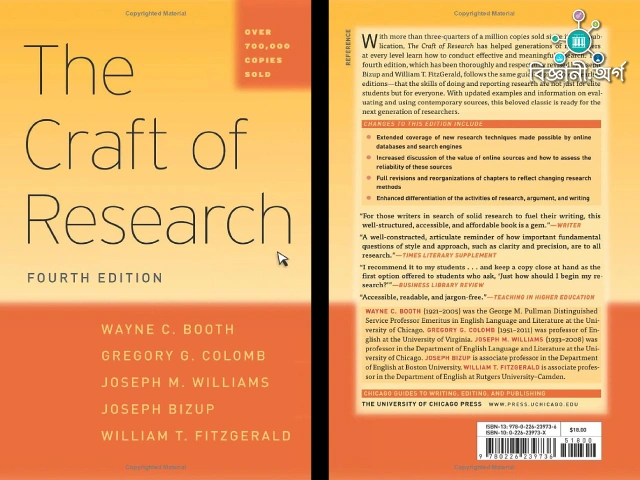
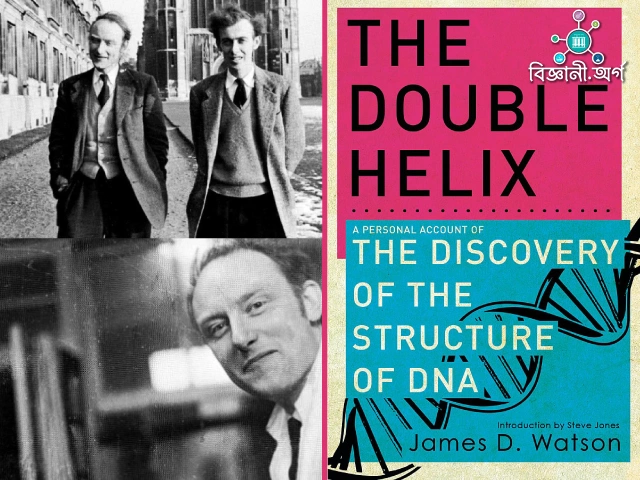
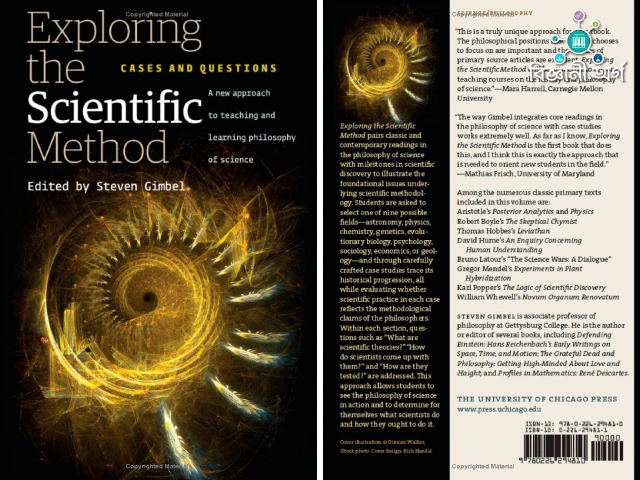
Leave a comment