১৯৪৫ সালের জুলাই মাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ তখনও থামেনি পুরোপুরি, কিন্তু যুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্ব গঠনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। সেই সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টের অনুরোধে একটি বিশেষ প্রতিবেদন তৈরি করেন বিজ্ঞানী ও প্রশাসক ভ্যানিভার বুশ। প্রতিবেদনটির নাম— Science, the Endless Frontier। এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে জন্ম নেওয়া এই দলিলটি ছিল কেবল যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির ভবিষ্যৎ নির্দেশকই নয়, গোটা আধুনিক দুনিয়ার জন্য এক বৈপ্লবিক চিন্তার ভিত্তিপ্রস্তর।
এই প্রতিবেদনের কেন্দ্রীয় বার্তা ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার: কোনো জাতির টেকসই অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি হলো মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণায় বিনিয়োগ। ভ্যানিভার বুশ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উদ্দেশে বলেছিলেন— যুদ্ধকালে যেভাবে বিজ্ঞান আমাদের অস্ত্রের দক্ষতা বাড়াতে সহায়তা করেছে, ঠিক তেমনিভাবে শান্তিকালেও বিজ্ঞান হতে পারে জনকল্যাণ, স্বাস্থ্য এবং শিল্পোন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। বুশের এই বক্তব্য একটি ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হয়; যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তোলে National Science Foundation (NSF), এবং পরবর্তী দশকগুলোতে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে দুনিয়ার শীর্ষ অর্থনীতিতে পরিণত হয়।
আমরা যদি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ফিরে তাকাই, দেখতে পাই— স্বাধীনতার পর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হলেও তার ধারাবাহিকতা, পরিকল্পনা ও বিনিয়োগের ঘাটতি দীর্ঘদিন ধরে স্পষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার অবকাঠামো দুর্বল, শিল্প ও একাডেমিয়ার মধ্যে যোগাযোগ প্রায় অনুপস্থিত, আর সরকারিভাবে গবেষণার জন্য বরাদ্দ খুবই সীমিত। অথচ আমাদের কৃষি বিপ্লব, গার্মেন্টস শিল্প, ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে যেসব অগ্রগতি হয়েছে, তার পেছনেও বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও প্রযুক্তির বড় ভূমিকা ছিল। আমরা যদি এই সাফল্যগুলোকে কাঠামোবদ্ধভাবে বিশ্লেষণ করি, তাহলে স্পষ্ট বোঝা যায়— বিজ্ঞানভিত্তিক বিনিয়োগ হলে বাংলাদেশও একটি উদ্ভাবনী ও জ্ঞাননির্ভর জাতিতে পরিণত হতে পারে।
ভ্যানিভার বুশ যখন বলেছিলেন, “নতুন জ্ঞানের সঞ্চয়ই ভবিষ্যতের মূল পুঁজি,” তখন তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, মৌলিক বিজ্ঞান—যা আপাতদৃষ্টিতে কোনো নির্দিষ্ট পণ্যের দিকে পরিচালিত নয়—সেই বিজ্ঞানেই থাকে ভবিষ্যৎ বিপ্লবের বীজ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোয়ান্টাম মেকানিক্স, জেনেটিক্স বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স—প্রথমে একাডেমিক গবেষণার মাধ্যমে যাত্রা শুরু করলেও, পরে তা হয়ে উঠেছে শিল্প ও অর্থনীতির চালিকা শক্তি। বাংলাদেশে বর্তমানে যে তরুণরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত বা জীববিজ্ঞানে স্নাতক করছে, তারা হয়তো সামনের দশকে এই সমাজে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে পারবে—যদি আমরা আজই তাদের জন্য গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করি।
ভ্যানিভার বুশের লেখার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল ‘স্বাধীন গবেষণার গুরুত্ব’। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, গবেষণাকে কোনো রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক স্বার্থের অধীন করা উচিত নয়। গবেষণার প্রকৃতি হওয়া উচিত অনুসন্ধানী, স্বাধীন এবং মৌলিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। আমাদের দেশের গবেষণা কাঠামোতে এই জায়গাটি এখনও স্পষ্টভাবে গড়ে ওঠেনি। অনেক ক্ষেত্রেই গবেষণা হয় নির্দিষ্ট প্রকল্প বা দাতার চাহিদা অনুযায়ী, যার ফলে গবেষকরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না আনলে, গবেষণা কেবল এক ধরনের প্রশাসনিক কার্যকলাপ হয়েই থাকবে, উদ্ভাবনের প্রকৃত আলো সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না।
‘Science, the Endless Frontier’ শুধু বিজ্ঞানচর্চার পক্ষে একটি যুক্তির দলিল নয়, এটি একই সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের এক নিখুঁত পাঠ। কারণ বুশ দেখিয়েছিলেন, বিজ্ঞান কেবল ল্যাবরেটরিতে সীমাবদ্ধ নয়; এটি নীতিনির্ধারণ, অর্থনীতি, শিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। একটি দেশের টেকসই উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন বিজ্ঞানকে সমাজের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এই কথাটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য, যেখানে প্রতিটি সমস্যা—পরিবেশ দূষণ, স্বাস্থ্য সংকট, কৃষির উৎপাদনশীলতা বা নগরায়ণের জটিলতা—সমাধানের জন্য প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও প্রযুক্তিভিত্তিক সমাধান।
বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায়, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া বা ইসরায়েলের মতো দেশগুলো কিভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে রাষ্ট্রনীতির স্তরে নিয়ে গিয়ে অভূতপূর্ব উন্নয়নের পথে হাঁটছে। চীন প্রতি বছর তার GDP-এর উল্লেখযোগ্য অংশ গবেষণা ও উন্নয়নের পেছনে ব্যয় করছে। ইসরায়েল বিশ্বের শীর্ষ স্টার্টআপ দেশগুলোর একটি, যেখানে প্রতিটি সমস্যাকে সমাধান করার জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি তৈরি হচ্ছে। এই দেশগুলো ভ্যানিভার বুশের সেই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তব রূপ দিয়েছে—যেখানে গবেষণা কেবল বিজ্ঞানীদের বিষয় নয়, বরং রাষ্ট্র ও সমাজের দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ।
বাংলাদেশেও ইতিমধ্যে কিছু পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইনোভেশন সেন্টার তৈরি হচ্ছে, শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে অংশ নিচ্ছে, এবং কিছু কিছু উদ্যোগ আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্রেও স্থান পাচ্ছে। তবে এই ধারা একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে হলে প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, কাঠামোগত পরিকল্পনা এবং গবেষণাকে জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে গ্রহণ করার মানসিকতা। যেমন বুশ বলেছিলেন, “এই কাজটি কেবল বিজ্ঞানীদের নয়; এটি জাতির সকল স্তরের নেতৃত্বের সম্মিলিত উদ্যোগের ফল হওয়া উচিত।”
‘Science, the Endless Frontier’ এর বার্তা আমাদের মনে করিয়ে দেয়— বিজ্ঞান কোনো বিলাসিতা নয়, এটি এক জরুরি প্রয়োজন। আমরা যদি ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে চাই, যদি আমাদের সমাজে দারিদ্র্য হ্রাস করতে চাই, স্বাস্থ্যসেবার মান বাড়াতে চাই, এবং একটি জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে চাই, তাহলে আমাদের আজকেই বিজ্ঞান ও গবেষণাকে জাতীয় উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করতে হবে। এটি কেবল একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত নয়, এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন—যা আমাদের তরুণদের প্রশ্ন করতে শেখাবে, আবিষ্কার করতে উৎসাহ দেবে, এবং ভাবতে শেখাবে—একটি ভালো সমাজ কীভাবে গড়ে তোলা যায়।
ভ্যানিভার বুশ যখন বলেছিলেন, “বিজ্ঞান এক অন্তহীন সীমানা,” তখন তিনি কেবল আকাশ কিংবা মহাকাশের কথা বলেননি। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন মানুষের কল্পনার পরিধি, চর্চার দৃঢ়তা, এবং প্রশ্ন করার সাহস—এই তিনের সম্মিলনেই গড়ে ওঠে সেই বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, যা একটি জাতিকে আলোকিত করতে পারে। আজকের বাংলাদেশে এই আলো ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের সকলের।




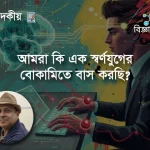

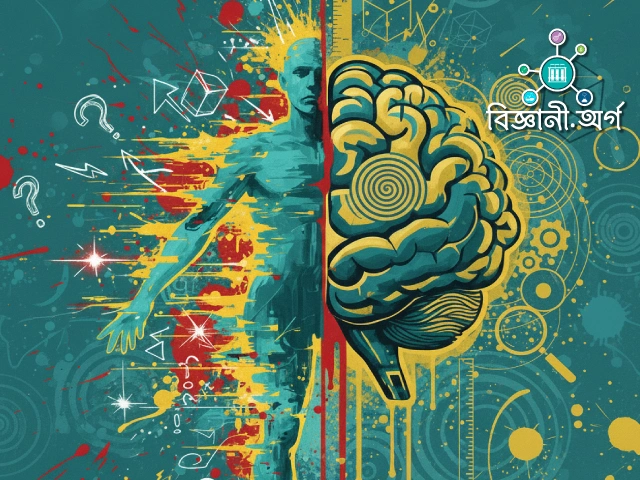
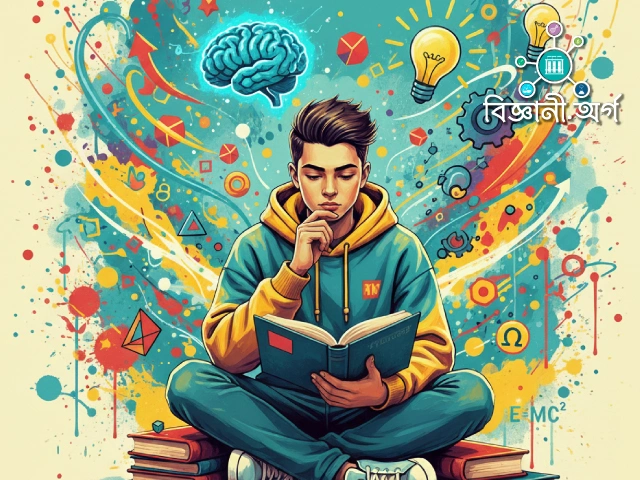



Leave a comment