নিউজ ডেস্ক, বিজ্ঞানী অর্গ | [email protected]
প্রতি চার বছরে একবার ফুটবল বিশ্বমঞ্চে ঘটে মহাযজ্ঞ—FIFA বিশ্বকাপ। এ ক্রীড়াযজ্ঞের মতোই আলোচনার কেন্দ্রে থাকে একটি নতুন জিনিস—আধুনিক প্রযুক্তিতে নির্মিত নতুন ম্যাচ বল। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে এবারের বল ‘Trionda’ (ট্রিওন্ডা) শুধুমাত্র দৃষ্টিনন্দন নয়, এটি গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের অভিনব প্রয়োগে তৈরি এক চমৎকার উদ্ভাবন।
এই বলটির প্যানেল সংখ্যা মাত্র চারটি, যা আগের যেকোনো বিশ্বকাপ বলের চেয়ে কম। উদাহরণস্বরূপ, ২০২২ সালের বল Al Rihla-তে ছিল ২০টি প্যানেল। এবার এক নতুন মাইলফলকে পৌঁছেছে Trionda, যার নির্মাণ-প্রক্রিয়া, নকশা এবং এর বৈজ্ঞানিক দিকগুলো সত্যিই তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো।
প্লেটোনিক সলিডস এবং বলের গণিত
একটি গোলক কি আদৌ সমতল জ্যামিতি দিয়ে বানানো সম্ভব? ফুটবলের বলের ইতিহাসে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই গণিতবিদরা প্লেটোনিক সলিডস (Platonic solids) নামের কিছু আকৃতির দিকে ফিরে গেছেন। এগুলো এমন কিছু ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিক আকৃতি যেগুলো একই মাপের এবং আকারের বহু কৌণিক পৃষ্ঠের সমন্বয়ে গঠিত।
প্রথাগত ফুটবল, যেমন ১৯৭০ সালের টেলস্টার (Telstar) বল, মূলত truncated icosahedron ভিত্তিক। এই আকৃতিতে ২০টি ষড়ভুজ এবং ১২টি পঞ্চভুজ প্যানেল থাকে, যা বলটিকে একটি গোলকীয় রূপ দেয়। সেই সময় এই বলটি ছিল কালো-সাদা রঙে, কারণ তখন টেলিভিশনগুলো ছিল সাদা-কালো এবং এই রঙ বেশি স্পষ্টভাবে দেখা যেত।
ট্রিওন্ডার ভিন্নতা: টেট্রাহেড্রন ও বাঁকানো প্যানেল
ট্রিওন্ডা বলের ভিত্তি টেট্রাহেড্রন (Tetrahedron) নামক একটি প্লেটোনিক সলিড, যা চারটি ত্রিভুজ দ্বারা গঠিত এবং তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম গোলকীয় আকৃতি। কিন্তু এখানেই রয়েছে ডিজাইনের চমক। Trionda-এর প্রতিটি প্যানেল ত্রিভুজাকৃতি হলেও তার প্রান্তগুলো সোজা নয়, বরং বাঁকানো। এই বাঁকানো প্রান্তগুলো মিলিয়ে বলটিকে একটি গোলাকার এবং aerodynamically কার্যকর রূপ দেওয়া হয়েছে।
এই নকশা ২০১৪ সালের ব্রাজিল বিশ্বকাপের বল Brazuca-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। সেই বলটি ছয়টি প্যানেলে গঠিত ছিল এবং এর ভিত্তিও ছিল আরেকটি প্লেটোনিক সলিড—কিউব (Cube)।
জাবুলানি বল এবং টানাপোড়েনের ইতিহাস
টেট্রাহেড্রনের ভিত্তিতে তৈরি আগের একটি বল ছিল ২০১০ সালের বিশ্বকাপের বল—Jabulani। নামের অর্থ “আনন্দিত হও”। তবে খেলোয়াড়দের জন্য এই আনন্দ বেশিরভাগ সময়ই হয়ে উঠেছিল বিভ্রান্তির নামান্তর। বলটি অত্যন্ত গোলাকার হলেও এর উড়ন্ত গতিপথ ছিল অত্যন্ত অনির্দেশ্য। খেলোয়াড়রা বলছিলেন, এটি বাতাসে আচমকা বাঁক নেয়।
এই সমস্যার মূল কারণ ছিল ড্র্যাগ (drag)—যা হলো বাতাসের কণার দ্বারা বলের ওপর প্রতিক্রিয়াশীল চাপ। সাধারণত একটি বল যত দ্রুত চলে, ড্র্যাগ তত বাড়ে। তবে কোনো একটি নির্দিষ্ট গতিবেগের পর বলের ওপর ড্র্যাগ হঠাৎ কমে যেতে পারে, একে বলে “critical speed”। গোল এবং মসৃণ বলের ক্ষেত্রে এই ক্রিটিকাল স্পিড অনেক বেশি হয়, অর্থাৎ তারা হঠাৎ করেই ড্র্যাগ কমিয়ে দেয় এবং অপ্রত্যাশিতভাবে আচরণ করে। এজন্যই গলফ বলের গায়ে থাকে ছোট ছোট গর্ত বা dimples—যাতে করে তারা দ্রুত ও সঠিকভাবে চলতে পারে।
জাবুলানি ছিল অতি গোলাকার, অতএব এটি বাতাসে অতিরিক্ত মসৃণ আচরণ করত, যার ফলে খেলোয়াড়রা এর আচরণ পূর্বানুমান করতে পারতেন না।
ট্রিওন্ডার ডিজাইনে পৃষ্ঠতলের টেক্সচার ও সিম স্ট্রাকচার
ট্রিওন্ডা এই সমস্যা থেকে শিক্ষা নিয়ে তৈরি করা হয়েছে কিছু নতুন বৈশিষ্ট্যে—এর পৃষ্ঠে রয়েছে ছোট গর্ত, যা ড্র্যাগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এছাড়াও, এর সেলাই বা সিমের আকৃতি এবং গভীরতা এমনভাবে তৈরি যাতে করে বলটি যথাযথভাবে বাতাসে চলতে পারে, কিন্তু আচরণে অপ্রত্যাশিত না হয়।
তবে এখানেও রয়েছে কিছু ঝুঁকি। ট্রিওন্ডার ঘূর্ণন সংক্রান্ত symmetrical behavior আগের কিছু বলের চেয়ে কম। উদাহরণস্বরূপ, Telstar বল ঘূর্ণন করলে ৬০টি সম্ভাব্য ভিন্ন অবস্থানেও একইরকম দেখায়, কিন্তু Trionda এরকম ১২টি মাত্র সমান্তরাল ঘূর্ণন পায়।
কম ঘূর্ণন এবং কম symmetrical design-এর কারণে বলের ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে “knuckleball effect”—যা একটি বিশেষ ধরনের বেসবল পিচিং টেকনিক থেকে আগত। যেখানে বলটি অল্প স্পিনে বাতাসে ঘোরে এবং এর অসমান পৃষ্ঠতলগুলো ভিন্ন ভিন্ন ড্র্যাগ তৈরি করে, ফলে বলটি আচমকা বাঁক নেয়।
এই ধরনের আচরণ বেসবলে চাইতেও ফুটবলে অপছন্দনীয়, কারণ খেলোয়াড় চান বল যেন ঠিক যেদিকে কিক করা হয় সেদিকেই যায়। তাই ফুটবলে চেষ্টা করা হয় বলকে যতটা সম্ভব symmetrical রাখা।
খেলোয়াড়দের প্রতিক্রিয়া ও প্রস্তুতি
বল পরিবর্তন মানেই খেলোয়াড়দের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ। সাবেক গোলকিপার ব্র্যাড ফ্রিডেল বলেছিলেন, “নতুন বল নিয়ে অনুশীলন করাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই বল শুকনা অবস্থায় কেমন, ভেজা অবস্থায় কেমন আচরণ করে, তা বোঝা দরকার।”
কানাডিয়ান মিডফিল্ডার জুলিয়া গ্রোসো বলেন, “আমরা যেকোনো বলেই খেলতে প্রস্তুত, তবে নতুন বলের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে প্র্যাকটিস সত্যিই সাহায্য করে।”
বিজ্ঞানীদের আগ্রহ: বলের সাফল্য মানেই তাদেরও জয়
বল মাঠে কেমন আচরণ করছে তা শুধু খেলোয়াড়েরাই নয়, বিজ্ঞানীরাও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। ওয়াশিংটনের ইউনিভার্সিটি অফ পিউজেট সাউন্ড-এর স্পোর্টস ফিজিসিস্ট জন এরিক গফ বলেন, “আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি Trionda হাতে নেওয়ার জন্য—এর পৃষ্ঠ, সিম কেমন, সেটা দেখার জন্য।”
বলটি অফিসিয়ালি প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা এটি নিয়ে উইন্ড টানেল পরীক্ষা করবেন, যাতে করে এর অ্যারোডাইনামিক বৈশিষ্ট্য বিস্তারিতভাবে বোঝা যায়।
শেষ কথা: খেলাটা শুধু মাঠেই নয়, গণিত-ভিত্তিক প্রযুক্তিতেও
ফুটবল মানেই শুধু কৌশল আর দৌড় নয়—এর পেছনে রয়েছে গণিতের পরিমিত জ্যামিতি, পদার্থবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম সন্নিবেশ, এবং ডিজাইন ও প্রযুক্তির শৈল্পিক প্রয়োগ। Trionda বল তার প্রকৌশলগত সৌন্দর্য দিয়ে হয়তো নতুনভাবে লিখে দেবে বিশ্বকাপের ইতিহাস। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে খেলা যেমন উত্তেজনাপূর্ণ হবে, তেমনি বলটির প্রতি বিজ্ঞানমনস্ক দর্শকেরও আগ্রহ থাকবে সর্বোচ্চ পর্যায়ে।
বিশ্ব যখন তাকিয়ে থাকবে স্কোরবোর্ডের দিকে, তখন আরেকদল মানুষ খেয়াল রাখবে বলের গতিপথ, ঘূর্ণন আর প্রতিক্রিয়ায়। কারণ, এই Trionda শুধুই একখানি বল নয়—এ এক চলমান বিজ্ঞান।
© বিজ্ঞানী অর্গ, ২০২৫ | সম্পাদক: [email protected]





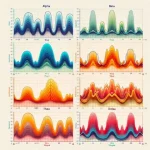


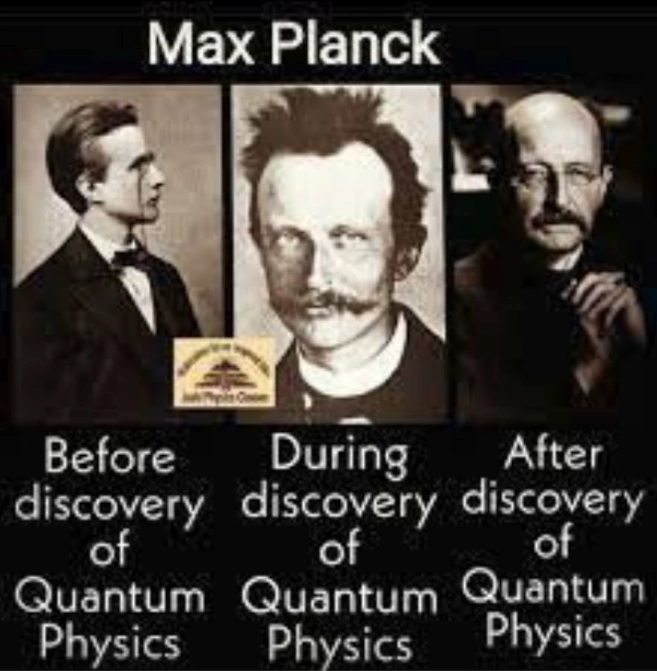


Leave a comment