যুব গবেষকরা যখন প্রথমবার গবেষণার পথে হাঁটতে শুরু করেন, তখন সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলোর একটি হলো গবেষণা-পদ্ধতি বা মেথডোলজি নির্বাচন করা। তারা জানেন না কোন পথে হাঁটবেন, কোন যন্ত্র বা উপকরণ ব্যবহার করবেন, কিংবা কোন ধরণের তথ্য তাদের জন্য সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। এই বিভ্রান্তি অনেক সময় এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে যে অনেকেই গবেষণা শুরু করার আগেই হতাশ হয়ে পড়েন। অথচ বিষয়টি এত জটিল নয়—প্রশ্নটিই গবেষণার পথ নির্দেশ করে। আপনার গবেষণা-প্রশ্নই আসলে কম্পাসের মতো কাজ করবে, যা আপনাকে সঠিক পথে চালিত করবে।
গবেষণা শুরু করার সময় আমাদের প্রথমেই নিজেদের কাছে প্রশ্ন রাখতে হয়—আমি আসলে কী জানতে চাই? আমি কি কোনো অভিজ্ঞতা বা ধারণা অনুসন্ধান করতে চাই? আমি কি কোনো সম্পর্ক বা প্রভাব মাপতে চাই? নাকি দুটোই করতে চাই? এই প্রশ্নগুলোই ধীরে ধীরে আমাদের গবেষণার ধরণ নির্ধারণ করে দেয়। কেউ কেউ হয়তো ভাবেন, আগে পদ্ধতি ঠিক করে তারপর গবেষণা-প্রশ্ন দাঁড় করানো সহজ হবে। কিন্তু বাস্তবে এর উল্টোটা সত্য। সঠিক প্রশ্নই গবেষণার নকশা নির্ধারণ করে।
গবেষণার জগতে মূলত দুটি বড় রাস্তা খোলা থাকে—গুণগত (Qualitative) ও পরিমাণগত (Quantitative) গবেষণা। গুণগত গবেষণাকে বলা যেতে পারে ‘কেন’ ও ‘কীভাবে’-এর পথ। এখানে গবেষক বোঝার চেষ্টা করেন কোনো অভিজ্ঞতার গভীরতা, কোনো ঘটনার ব্যাখ্যা, বা মানুষের চিন্তার অন্তর্নিহিত অর্থ। এই গবেষণায় তথ্য আসে মানুষের কথায়, আচরণে, ছবি বা পর্যবেক্ষণ থেকে। একজন গবেষক হয়তো দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিলেন, যেখানে একজন মানুষ তার জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন। আবার কেউ হয়তো একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে একত্রিত করে মতামত শুনলেন, যাকে আমরা ফোকাস গ্রুপ আলোচনা বলি। কখনো বা একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা ঘটনার ওপর গভীর কেস স্টাডি করা হয়। আর অনেক সময় গবেষক শুধু পর্যবেক্ষণ করেন—কে কিভাবে আচরণ করছে, কোন প্রেক্ষাপটে কী ঘটছে। এভাবেই ধীরে ধীরে বাস্তবের ভেতর থেকে উঠে আসে নতুন অর্থ, নতুন ব্যাখ্যা।
অন্যদিকে, পরিমাণগত গবেষণা হলো ‘কত’ ও ‘কি’ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পথ। এখানে লক্ষ্য থাকে একটি হাইপোথিসিস বা অনুমান যাচাই করা, ভেরিয়েবল মাপা, কিংবা প্যাটার্ন খুঁজে বের করা। তথ্য আসে সংখ্যা, গ্রাফ বা টেবিলের আকারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন গবেষক হয়তো একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করলেন এবং একশ জনের কাছে সেটি পূরণ করতে দিলেন, যাতে বোঝা যায় কতজন শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সমস্যায় পড়ছে। আবার কেউ হয়তো নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরীক্ষা চালালেন, যেখানে নির্দিষ্ট ভেরিয়েবল পরিবর্তন করে দেখা হলো কেমন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। পরে এই সংখ্যাগুলোকে পরিসংখ্যান বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা হয় কোন প্যাটার্ন বেরিয়ে আসছে, কোন সম্পর্ক দৃশ্যমান হচ্ছে।
কিন্তু বাস্তব জীবন তো শুধু শব্দ বা সংখ্যা দিয়ে গড়া নয়। অনেক সময়ই একটি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেতে আমাদের উভয় পথের সমন্বয় করতে হয়। একে বলা হয় মিশ্র-পদ্ধতি (Mixed Methods) গবেষণা। ধরুন, আপনি প্রথমে একটি সমীক্ষা করলেন, যেখানে দেখা গেল অনেক শিক্ষার্থী গবেষণার প্রশ্ন নির্ধারণে সমস্যায় পড়ে। কিন্তু কেন এমন হয়, তা জানতে আপনাকে হয়তো কয়েকজন শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার নিতে হলো। সংখ্যার পেছনের গল্প খুঁজে বের করাই হলো মিশ্র-পদ্ধতির আসল শক্তি।
আজকের যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও (AI) গবেষণার সহযোগী হয়ে উঠছে। গুণগত গবেষণায় যেখানে বিপুল সাক্ষাৎকারের টেক্সট বিশ্লেষণ করতে হতো হাতে হাতে, সেখানে এখন অ্যালগরিদম সাহায্য করছে দ্রুত থিম বের করতে। আবার পরিমাণগত গবেষণায় বিপুল পরিসংখ্যান বিশ্লেষণকে অনেক সহজ করে দিচ্ছে AI টুলস। একসময়ের ক্লান্তিকর কাজগুলো এখন অনেকটা সহজ ও দ্রুত সম্পন্ন হচ্ছে। তবে এই সহজলভ্যতা যেন গবেষণার মৌলিক প্রশ্নকে আড়াল না করে।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, গবেষণা-পদ্ধতি যেন গবেষণার প্রশ্ন দ্বারা চালিত হয়, উল্টোটা নয়। যদি আপনার প্রশ্ন হয় মানুষের অভিজ্ঞতার ভেতরে লুকানো অর্থ খুঁজে বের করা, তবে গুণগত গবেষণাই সঠিক পথ। আর যদি আপনার প্রশ্ন হয় একটি নির্দিষ্ট ভেরিয়েবল কিভাবে অন্য ভেরিয়েবলকে প্রভাবিত করছে তা যাচাই করা, তবে সংখ্যার জগতে নামতে হবে। অনেক সময় দুটোই দরকার হয়—তখন দুই পথের সমন্বয়ই সবচেয়ে ফলপ্রসূ হয়।
বাংলাদেশের তরুণ গবেষকদের জন্য এই উপলব্ধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রায়ই দেখি, শিক্ষার্থীরা পদ্ধতিকে সামনে রেখে প্রশ্নকে সাজাতে চায়। এতে গবেষণা জটিল হয়ে পড়ে, অনেক সময় উদ্দেশ্য অস্পষ্ট থেকে যায়। অথচ একটি সঠিক প্রশ্নই গবেষণার জন্য সবচেয়ে বড় দিশারি। প্রশ্নটি যদি সঠিক হয়, তবে পথও নিজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
গবেষণার শুরুতে পথ হারিয়ে ফেলার অনুভূতি স্বাভাবিক। নতুন গবেষকদের জন্য বিভ্রান্তি বরং একধরনের পরিণত হওয়ার ধাপ। কিন্তু যে মুহূর্তে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার গবেষণার আসল প্রশ্ন কী, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই আপনার যাত্রাপথ নির্ধারিত হয়ে যাবে। তখন আর আপনাকে পদ্ধতি খুঁজতে হবে না, বরং পদ্ধতিই আপনাকে খুঁজে নেবে।


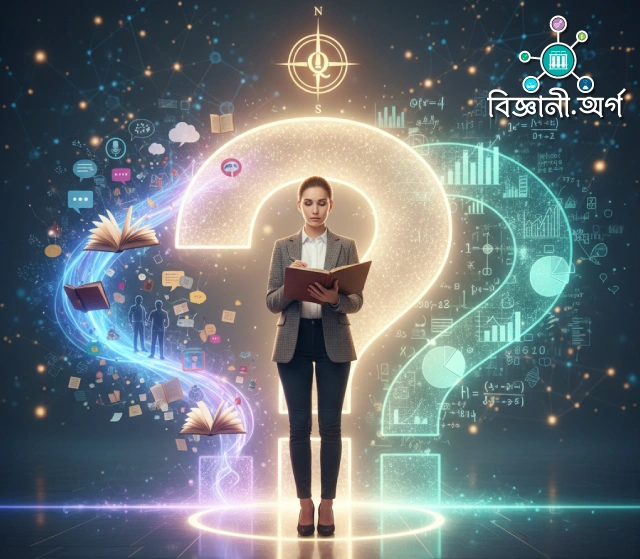


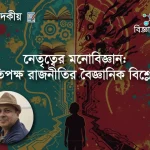


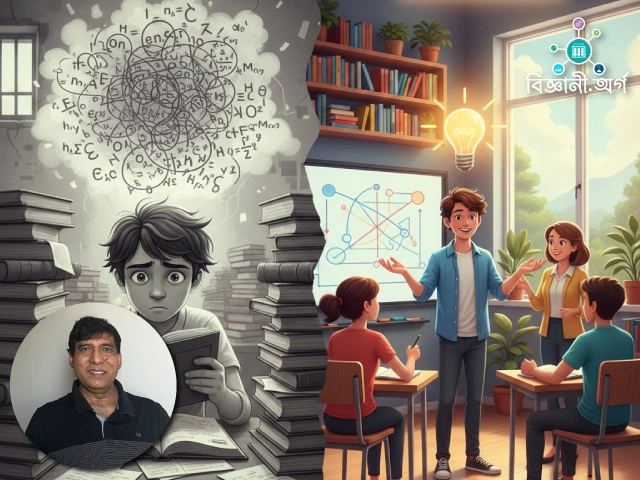
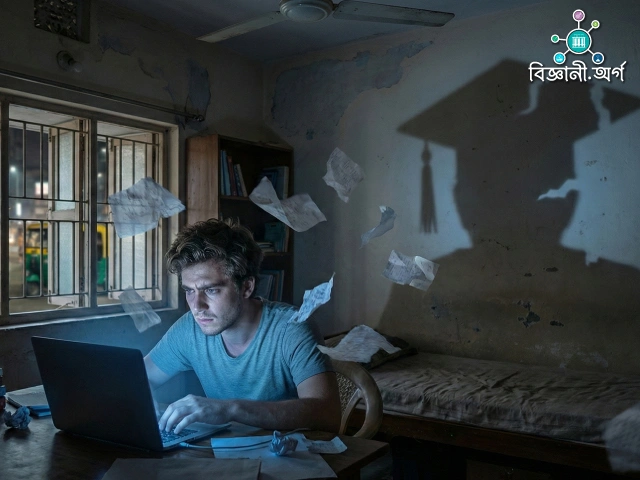
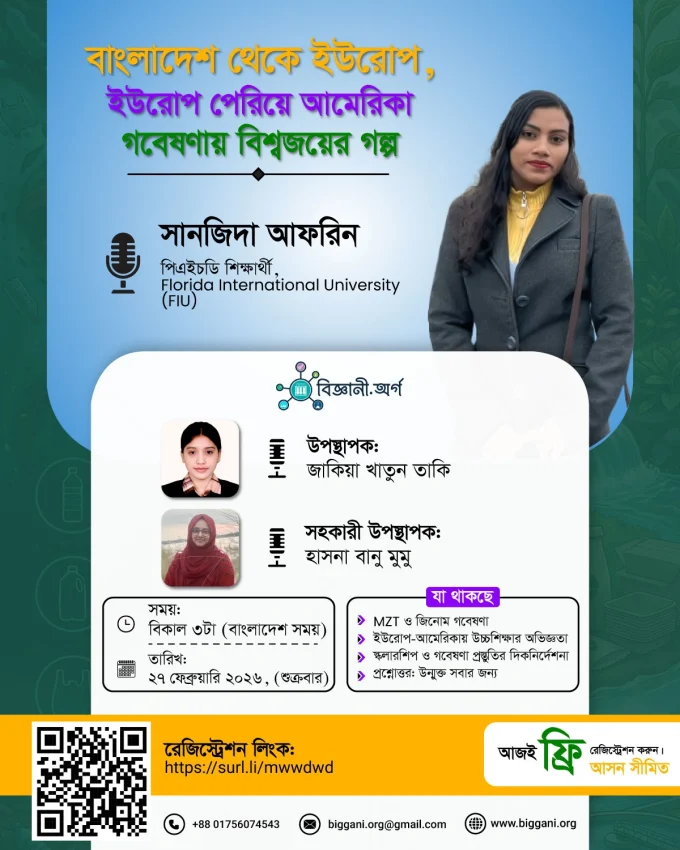
Leave a comment