বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত টেনিস তারকাদের জীবনকথা ঘাঁটলে একটি সাদৃশ্য চোখে পড়ে—তারা প্রায় সবাই ছোটবেলা থেকেই নির্দিষ্ট একটি খেলার প্রতি নিবেদিত থেকেছেন। গল্ফের টাইগার উডস, টেনিসের সেরেনা উইলিয়ামস—এই নামগুলো যেন প্রমাণ করে যে প্রতিভার পরিচর্যা শুরু হয় একদম শিশু বয়স থেকেই, আর বিশেষায়নের পথেই লুকিয়ে থাকে সাফল্যের চাবিকাঠি। কিন্তু এই ভাবনাটিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন ডেভিড এপস্টিন তাঁর বই Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World–এ। তিনি বলছেন, সাফল্যের রাস্তা শুধু বিশেষায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং বিভিন্ন পথ ঘুরে দেখে, নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তারপর নিজের জায়গা খুঁজে নেওয়াই অনেক সময় দীর্ঘস্থায়ী এবং বিস্তৃত সাফল্যের দ্বার খুলে দেয়।
বইটি শুরু হয় দুটি প্রতিযোগিতার গল্প দিয়ে—টাইগার উডস বনাম রজার ফেদেরার। টাইগার উডস শৈশব থেকেই গল্ফে ডুবে যান; তাঁর বাবা ছিলেন প্রথম কোচ, এবং মাত্র দুই বছর বয়সেই উডস গল্ফ ক্লাবে সাড়া ফেলেন। বিপরীতে, রজার ফেদেরার শৈশবে নানা ধরনের খেলায় অংশ নিতেন—ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল—সবকিছুর সাথে সময় কাটিয়েছেন, এবং অনেক পরে গিয়ে টেনিসকে নিজের মূল খেলা হিসেবে বেছে নেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, উভয়েই নিজের ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু ফেদেরারের যাত্রা আমাদের এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি উপহার দেয়—সেটি হলো সাধারণত নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেই অনেক সময় মানুষ নিজেকে আরও ভালোভাবে চিনে নিতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদে আরও সফল হতে পারে।
বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা এবং কর্মসংস্থানের প্রেক্ষাপটে এপস্টিনের এই যুক্তি অনেকটাই নতুন আলো ফেলে। আমাদের দেশে সাধারণত মাধ্যমিক কিংবা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনার বিষয় নির্বাচন হয়ে যায়, এবং তারপর থেকে শিক্ষার্থীরা একটি নির্দিষ্ট পথে চলতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই বিশেষায়নের চাপ অনেককেই অস্থির করে তোলে। একজন ছাত্র যখন বিজ্ঞানের ছাত্র, তখন তার সৃজনশীল লেখালেখির প্রতি আগ্রহ বা সংগীতের প্রতি অনুরাগকে যেন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আবার কেউ যদি বাণিজ্য নিয়ে পড়ে, তাহলে তার জন্য বিজ্ঞান কিংবা প্রযুক্তিবিষয়ক কৌতূহলকে ‘অপ্রাসঙ্গিক’ বলে খাটো করা হয়। অথচ বাস্তব জগতে সমস্যাগুলো আর এতটা সীমিত নয়; সেখানে প্রায়ই বিজ্ঞানের সাথে সমাজবিজ্ঞান, প্রযুক্তির সাথে নীতিশাস্ত্র, অর্থনীতির সাথে পরিবেশবিদ্যার সম্মিলিত প্রয়োগ দরকার হয়।
Range–এ এপস্টিন দেখিয়েছেন, যারা জীবনের শুরুতে বিভিন্ন ধরনের কাজ ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়, তারা নাকি পরবর্তীতে সমস্যার নতুন ও সৃজনশীল সমাধান খুঁজে পেতে বেশি সক্ষম হন। কারণ, তাদের চিন্তাধারায় একটি খোলামেলা দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়। তারা একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্যে আটকে পড়ে না, বরং নানা প্রেক্ষাপট থেকে ধারণা নিয়ে সেটিকে নতুনভাবে প্রয়োগ করতে পারে। এই ‘দর্শন’ আসলে আধুনিক সমস্যাবিষয়ক গবেষণাতেও প্রাসঙ্গিক। উদাহরণস্বরূপ, একজন স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী যদি সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান রাখেন, তবে তিনি জনস্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সমস্যাগুলো বুঝতে ও সমাধান করতে অনেক বেশি সক্ষম হবেন। এক্ষেত্রে তাঁর ‘range’ বা বহুমুখী অভিজ্ঞতা তাঁকে বাড়তি শক্তি দেয়।
এই ধারণাটি কেবল ব্যক্তিগত সাফল্যের ক্ষেত্রেই নয়, বরং বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটেও গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি বৈশ্বিক প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও এখন ক্রমেই দেখা যাচ্ছে, তারা কেবল প্রযুক্তি দক্ষতা খুঁজছেন না—তারা এমন কর্মী চাইছেন যারা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান রাখেন, সমস্যার বহুমাত্রিক দিক বুঝতে পারেন এবং নতুন পরিবেশের সাথে দ্রুত মানিয়ে নিতে পারেন। গুগল, আমাজনের মতো জায়ান্টরাও এখন ‘T-shaped’ মানুষ খোঁজেন—যাদের কোনো একটি বিষয়ে গভীর দক্ষতা আছে, কিন্তু অন্য অনেক বিষয়ে একটি সামগ্রিক ধারণাও রয়েছে। এই ধরনের সাধারণতন্ত্র-ভিত্তিক মনোভাবই আজকের পৃথিবীতে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।
তবে প্রশ্ন আসে—এই ‘range’ অর্জনের পথ কী? আমাদের শিক্ষা ও সামাজিক কাঠামো কি আদৌ এমন সুযোগ দেয় যেখানে একজন ছাত্র বা ছাত্রী নিজের পছন্দের বিষয়গুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে পারেন? উত্তরটি সহজ নয়। পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সমাজ—সবকিছুই যেন আমাদের দ্রুত ‘দক্ষ’ হতে বাধ্য করে। তরুণদের বলা হয়, “সময় নষ্ট করো না”, “একটি লক্ষ্য স্থির করো”, “তাড়াতাড়ি ক্যারিয়ার গড়ো।” অথচ এপস্টিন বলছেন, ধীরে চলাও অনেক সময় লাভজনক হতে পারে, যদি সেই সময়টা সত্যিকারের অনুসন্ধান আর আত্ম-অনুধাবনের মধ্যে কাটানো যায়।
বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি মুক্তির বার্তা হতে পারে। বিশেষ করে যারা একাধিক বিষয়ে আগ্রহী, কিন্তু সমাজ বা পরিবার তাদের শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট পথে চলতে বাধ্য করছে, তারা এই বই থেকে সাহস পেতে পারেন। একজন ছাত্র হয়তো গণিত ভালোবাসেন, কিন্তু একইসাথে গল্প লিখতেও ভালোবাসেন—তাঁর এই বহুমুখী আগ্রহকে আর ‘দ্বিধা’ হিসেবে দেখা উচিত নয়, বরং এটিই হতে পারে তাঁর সাফল্যের মূলধন। ভবিষ্যতের গবেষক, উদ্যোক্তা বা নীতিনির্ধারক—যেই হোন না কেন—নানামুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বড় হওয়া মানুষগুলোই নেতৃত্ব দিতে পারেন একটি আরও সুস্থ, উদ্ভাবনী সমাজ গঠনে।
এপস্টিনের যুক্তিগুলো কেবল ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়; তারা আমাদের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাকেও প্রশ্ন করে। প্রযুক্তির বিকাশ, জলবায়ু পরিবর্তন, জনস্বাস্থ্য সমস্যা, শিক্ষা সংস্কার—এসব চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় একক কোনো বিষয়ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট নয়। দরকার বহুবিধ চিন্তার মিলনস্থল। যেখানে প্রকৌশলী এবং শিল্পী, চিকিৎসক এবং দার্শনিক, পরিসংখ্যানবিদ এবং লেখক—সবাই একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শিখে, একে অপরকে সম্পূরক করে একটি বড় চিন্তা গঠন করতে পারেন।
আমাদের প্রজন্মের কাছে, বিশেষত যারা এখনো নিজেদের পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, Range এক অনুপ্রেরণার নাম। এটি একধরনের আত্মবিশ্বাস তৈরি করে—যেখানে জীবনের ঘুরপথগুলো কোনো ‘বিপথ’ নয় বরং একেকটি মূল্যবান অভিজ্ঞতা, যেগুলোর মাধ্যমে ভবিষ্যতের দৃঢ় ভিত্তি গড়ে ওঠে। এই ঘুরে দেখার সাহস, এই অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে চলার ধৈর্যই আজকের জটিল পৃথিবীতে আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি হতে পারে।
এজন্যই আজকের দিনে আমরা যদি আমাদের শিক্ষার্থীদের, তরুণদের এবং এমনকি নিজেরাও কিছুটা ধৈর্য নিয়ে নানা বিষয় শিখি, পড়ি, ভাবি—তাহলে হয়তো আমরাও হয়ে উঠতে পারি সেই প্রজন্ম, যাদের সাফল্যের গোঁড়ায় থাকবে একটি কথাই—বিশেষায়নের আগে সাধারণতার শক্তি বুঝতে শেখা। আজকের বাংলাদেশকে গড়তে হলে দরকার এমন তরুণদের, যারা বইয়ের বাইরে গিয়েও ভাবতে পারেন, অনিশ্চয়তার মধ্যে নিজেদের খুঁজে পান, আর একাধিক শাখায় জ্ঞানের শিকড় বিস্তার করে একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়তে ভূমিকা রাখতে পারেন। Don’t be afraid to explore—এটাই হোক আমাদের আগামী পথচলার মূলমন্ত্র।






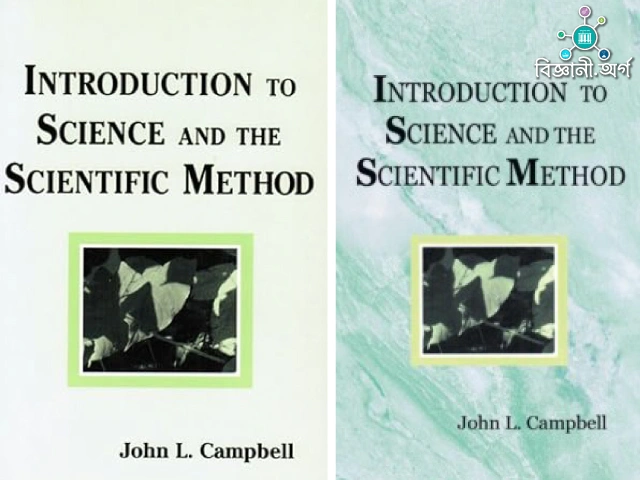

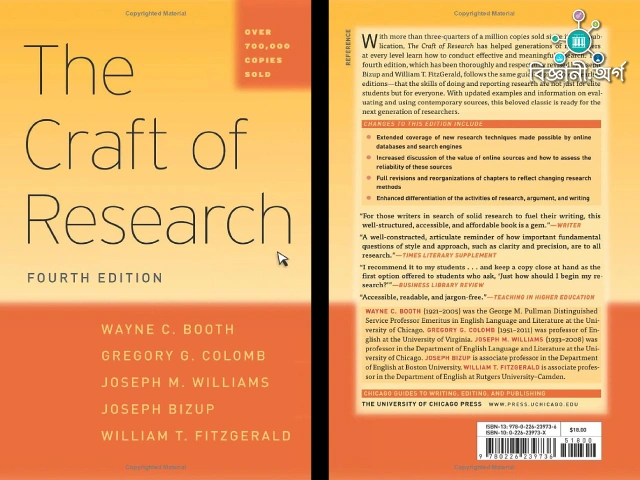
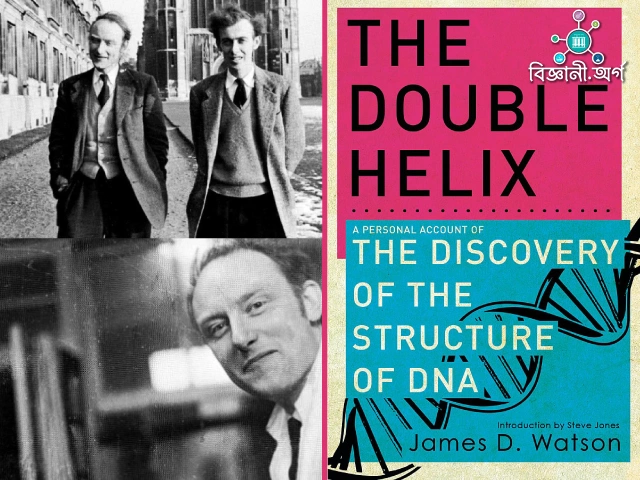
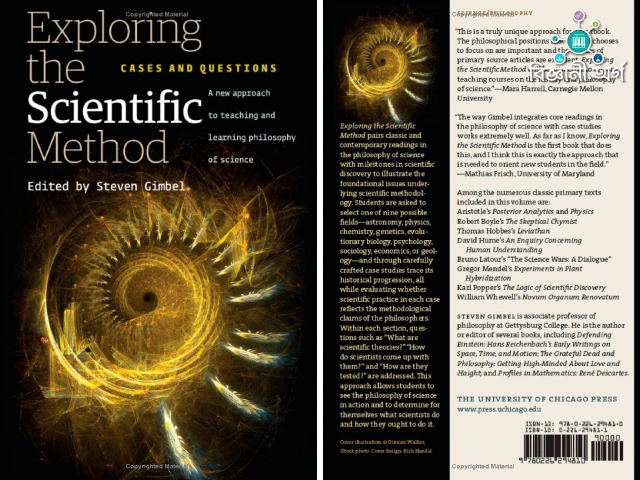
Leave a comment