শেখার অর্থ কি শুধুই বইয়ের পাতা ওল্টানো আর ক্লাসরুমে বসে নোট নেওয়া? নাকি আমাদের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে এমন এক জটিল ও রহস্যময় প্রক্রিয়া চলে, যা আমরা নিজেও পুরোপুরি বুঝে উঠি না? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতেই বিজ্ঞান সাংবাদিক বেনেডিক্ট কেয়ারি তাঁর আলোচিত বই How We Learn–এ আমাদের নিয়ে যান শেখার বিজ্ঞানের অন্তর্জগতে। বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই বইটি শুধু একটি পড়ার অভিজ্ঞতা নয়, বরং শেখার পদ্ধতি নিয়ে নতুন করে ভাবার একটি দরজা খুলে দেয়। একবিংশ শতাব্দীর প্রতিযোগিতামূলক সমাজে কেবল কঠোর পরিশ্রম নয়, বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ অধ্যয়নও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কেয়ারির বইটি যেন সেই ‘বুদ্ধিমত্তার মানচিত্র’।
আমরা সাধারণত মনে করি, নিরবিচারে পড়া, নির্দিষ্ট সময় ধরে প্রতিদিন পড়া, একঘণ্টা মানেই একঘণ্টা মনোযোগ—এসবই ভালো ছাত্র হবার মূল চাবিকাঠি। কিন্তু কেয়ারি এই প্রচলিত ধারণাগুলোকেই চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি বলেন, শেখা হচ্ছে একটি জীবন্ত প্রক্রিয়া—যেখানে বিশ্রাম, ভুল, বিস্মরণ এমনকি সময়ের অপচয় বলেও যা আমরা ভাবি, সেগুলোও শেখার অংশ। কেয়ারি দেখান, ঘুম এবং শেখার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে। পরীক্ষার আগের রাতভর না পড়ে বরং সঠিক সময়ে ঘুমিয়ে নেওয়া অনেক বেশি কার্যকর হতে পারে, কারণ ঘুমের মধ্যেই আমাদের মস্তিষ্ক জ্ঞানের পুনর্বিন্যাস করে, তথ্য গুছিয়ে রাখে।
এ বইটি শেখার ক্ষেত্রে “ভুল করাকে” এক অসাধারণ শক্তি হিসেবে তুলে ধরে। আমরা অনেকেই ভুল করলে লজ্জা পাই, মনে করি ভুল মানেই ব্যর্থতা। কিন্তু কেয়ারি বলেন, ভুল হলো শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। কোনো তথ্য যদি আমরা প্রথমবার ভুল করি, পরবর্তীতে সেটা শিখে নিলে স্মৃতিতে তার গভীর ছাপ পড়ে। অর্থাৎ ভুল এক ধরনের “স্মৃতি প্রবেশদ্বার” হিসেবেও কাজ করতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে পরীক্ষায় নম্বর হারানোর ভয়ে অনেকেই প্রশ্ন করতে বা চিন্তা করতে সাহস পায় না।
শেখার বিজ্ঞান নিয়ে আরও একটি চমৎকার বিষয় বইটিতে উঠে এসেছে—তথাকথিত “মাল্টিটাস্কিং” বা একসাথে একাধিক কাজ করার অভ্যাস আসলে কীভাবে শেখাকে বাধাগ্রস্ত করে। মোবাইল ফোন হাতে রেখে পড়া, কিংবা ফেসবুক চালিয়ে বই পড়া—এই আধুনিক অভ্যাসগুলো আমাদের মনোযোগকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। কেয়ারি বলেন, মনোযোগ একটি সীমিত সম্পদ। একে একাধিক দিকে টান দিলে কোনো একটি কাজেই পরিপূর্ণ ফোকাস দেওয়া সম্ভব হয় না। বাংলাদেশে মোবাইল-নির্ভরতার এই যুগে এ বার্তাটি কিশোর-তরুণদের কাছে গভীর গুরুত্ব বহন করে।
এ বইয়ের আরেকটি অনন্য দিক হলো “spacing effect” এবং “interleaving” নামের কৌশলগুলি। অনেকেই এক বিষয়ে একটানা পড়ে শেষ করে ফেলতে চায়, যেমন ইতিহাস বা গণিত এক বসাতেই শেষ করে ফেলা। কিন্তু গবেষণা বলছে, বিষয়গুলোকে ফাঁকফাঁক করে পড়া এবং বিভিন্ন বিষয়কে পর্যায়ক্রমে ঘুরিয়ে পড়া মস্তিষ্কের জন্য অনেক বেশি কার্যকর। এই কৌশলগুলো বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ঐতিহ্যগত ধারার বাইরে গিয়ে নতুনভাবে প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করতে পারে, বিশেষ করে যারা বিসিএস, মেডিকেল, বা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার মতো দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তুতির সাথে যুক্ত।
বইটি শুধু কৌশলগত পরামর্শেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং শেখা-সংক্রান্ত বেশ কিছু মনস্তাত্ত্বিক দিকও স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। যেমন, অনেকে মনে করে যে তারা “ভিজ্যুয়াল লার্নার” বা “অডিও লার্নার”—যেমন কেউ চোখ দিয়ে ভালো শেখে, কেউ কানে শুনে। কিন্তু কেয়ারি জানান, এসব শ্রেণিবিভাগের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি খুব দুর্বল। বরং যেভাবে শেখা হচ্ছে, তার পরিবর্তন ঘটিয়ে শেখার প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করলেই তথ্য দীর্ঘস্থায়ীভাবে স্মৃতিতে গেঁথে যায়।
এই বইয়ের সবচেয়ে বড় শক্তি সম্ভবত এর সহজবোধ্যতা। কঠিন নিউরোসায়েন্স বা মনস্তত্ত্বীয় তত্ত্ব নয়, বরং বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া উদাহরণ, শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা এবং খোলামেলা ভাষায় লেখা এই বইটি বিজ্ঞানভিত্তিক হলেও দারুণভাবে মানবিক। বাংলাদেশে যেখানে শিক্ষা মানেই এখনো অনেকাংশে মুখস্থনির্ভরতা, সেখানে এই বই এক নতুন আলো নিয়ে হাজির হতে পারে—একটি মানবিক, বৈজ্ঞানিক ও কার্যকর শেখার দর্শন।
এ কথা বলাই যায়, How We Learn বইটি কেবল শিক্ষার্থীদের জন্য নয়, শিক্ষকদের, অভিভাবকদের এমনকি নীতিনির্ধারকদের জন্যও এক ধরনের চমকপ্রদ বাস্তবতা তুলে ধরে। আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির প্রতিটি স্তরে যদি শেখার প্রকৃত বিজ্ঞানকে গুরুত্ব দেওয়া হতো, তবে শুধু শিক্ষার মান নয়, শিখন আনন্দও বহু গুণে বেড়ে যেত। শিশুদের শেখানোর ধরন হতো আরও ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আরও সহানুভূতিপূর্ণ।
শুধু স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, এই বই প্রমাণ করে যে শেখার কোনও নির্দিষ্ট বয়স নেই। জীবনের প্রতিটি স্তরেই আমাদের শেখার প্রক্রিয়া চলমান, এবং সেই প্রক্রিয়াকে আরও দক্ষ ও আনন্দদায়ক করে তুলতে আমরা সকলে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারি। একবিংশ শতাব্দীতে যেখানে জ্ঞানই সবচেয়ে বড় শক্তি, সেখানে শেখার কৌশল জানাটা হয়ে দাঁড়ায় সবচেয়ে জরুরি বিষয়গুলোর একটি।
বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি এই বইয়ের ধারণাগুলো ধীরে ধীরে প্রবেশ করানো যায়—যেমন পরীক্ষানির্ভরতা কমিয়ে শেখার গভীরতাকে গুরুত্ব দেওয়া, ভুলকে ভয় না করে গ্রহণ করা, বিশ্রামের গুরুত্ব অনুধাবন করা, এবং শেখাকে একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখার অভ্যাস গড়ে তোলা—তাহলে হয়তো আমাদের তরুণ প্রজন্ম আরও স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখবে, আরও গভীরভাবে প্রশ্ন করতে পারবে।
শেষ পর্যন্ত, How We Learn একটি আহ্বান—নিজেকে জানার, শেখার অভ্যাসকে বৈজ্ঞানিকভাবে বুঝে তোলার এবং নিজের শেখাকে নিজের মতো করে গড়ে তোলার। এটি কেবল একটি বই নয়, বরং একটি বিপ্লব—শেখার বিপ্লব। একজন শিক্ষার্থী, একজন শিক্ষক কিংবা একজন কৌতূহলী পাঠক হিসেবে আমরা সবাই এই বিপ্লবের অংশ হতে পারি। শেখা যদি জীবনের যাত্রা হয়, তবে এই বইটি সেই যাত্রার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য মানচিত্র।


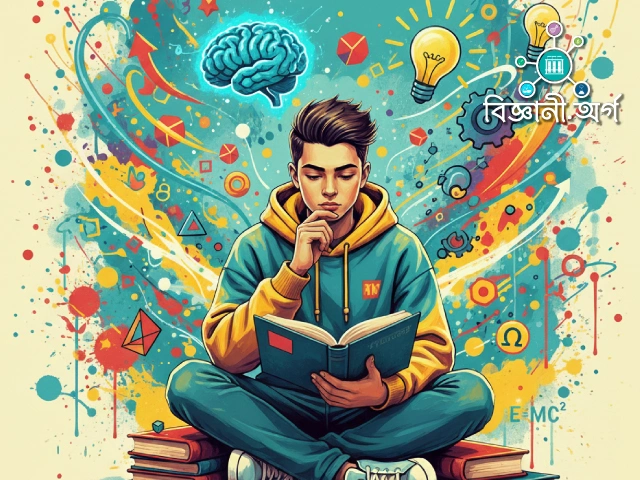



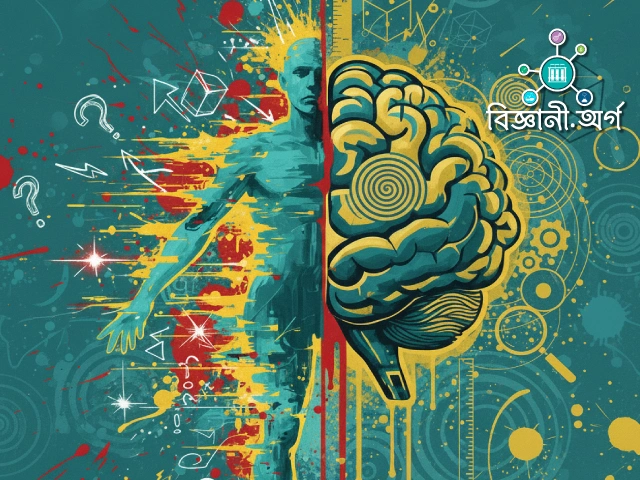




Leave a comment