বিজ্ঞান নিয়ে লেখা বই পড়তে গিয়ে আমরা অনেক সময় খটমটে ভাষা, তত্ত্বে ভরপুর জটিল ব্যাখ্যা কিংবা গুরুগম্ভীর গবেষণার ভারে বিপর্যস্ত হই। অথচ বিজ্ঞান তো কেবল গবেষণাগার কিংবা পরীক্ষাগারের সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়—এর শিকড় মানুষের কৌতূহলের গভীরে, আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি স্তরে। এই ব্যাপারটিকে দুর্দান্তভাবে ধরে এনেছেন বিল ব্রাইসন তাঁর ব্যতিক্রমী বই A Short History of Nearly Everything-এ। এমন একটি বই, যেখানে মহাবিশ্বের জন্ম থেকে শুরু করে মানবদেহের কোষ-পর্যন্ত, সবকিছুকে দেখা হয়েছে একরাশ বিস্ময়, হাস্যরস আর গভীর অনুসন্ধিৎসার চোখে।
ব্রাইসনের এই বই মূলত একটি বিজ্ঞানভিত্তিক ভ্রমণকাহিনি। তবে এটি কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয়। পদার্থবিজ্ঞান থেকে শুরু করে জীববিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান থেকে রসায়ন—বিজ্ঞানের সব শাখাই যেন তার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রবাহিত। ব্রাইসন নিজে কোনো পেশাদার বিজ্ঞানী নন, বরং একজন সাহিত্যের মানুষ। এটাই সম্ভবত তাঁর বিশেষত্ব। কারণ, বিজ্ঞান নিয়ে লেখার সময় তিনি যেখানে বিভ্রান্ত হতে পারতেন, ঠিক সেই জায়গাগুলোতেই তিনি আরও বেশি প্রশ্ন তুলেছেন। আর এই প্রশ্নগুলোই পাঠকের মনে তৈরি করেছে কৌতূহলের সিঁড়ি।
বইটির শুরুই এক চমৎকার প্রশ্ন দিয়ে—“আমরা এখানে কিভাবে এলাম?” এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে লেখক পৌঁছে যান বিগ ব্যাং তত্ত্বে, সেখানে থেকে গ্রহ-নক্ষত্রের জন্ম, এরপর পৃথিবীর গঠন, প্রাণের উদ্ভব, প্রাণীর বিবর্তন, এবং মানব সভ্যতার সূচনালগ্নে। কিন্তু যেভাবে তিনি এগিয়েছেন, তা কখনোই একঘেয়ে নয়। বরং তিনি প্রতিটি তত্ত্বের পেছনের মানুষদের গল্প বলেছেন—সেইসব বিজ্ঞানী, যারা তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, সমাজের বিদ্রূপ উপেক্ষা করে বা নিছক কৌতূহল থেকে একের পর এক আবিষ্কার করে গেছেন।
সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো, ব্রাইসন বিজ্ঞানের ভুলগুলো নিয়েও কথা বলেন। যেসব বিজ্ঞানী কখনো ভুল পথে হেঁটেছেন, কিংবা যাদের তত্ত্ব পরে ভুল প্রমাণিত হয়েছে—তাদের ব্যর্থতাও তিনি গল্পের মতো বর্ণনা করেন। এতে পাঠক বোঝে, বিজ্ঞান কোনো অলৌকিক কাহিনি নয়, বরং এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া, যেখানে ভুল আর সংশোধনের মধ্য দিয়েই এগোয় জ্ঞানের জয়যাত্রা। আর এখানেই বইটি হয়ে ওঠে একটি চিন্তনশীল শিক্ষা। পাঠক শেখে, ভুল করাটা দোষ নয়, বরং ভুল থেকে শিখে আবারও সামনে এগিয়ে যাওয়াটাই বিজ্ঞানচর্চার প্রকৃত রূপ।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই বইটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রায়শই পরীক্ষার প্রস্তুতির উপকরণ হিসেবে দেখা হয়, উৎসাহ ও কৌতূহল জাগানোর মাধ্যম হিসেবে নয়। ফলে অনেক ছাত্রছাত্রীর কাছে বিজ্ঞান এক নিষ্প্রাণ বিষয় হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি তারা ব্রাইসনের মতো লেখকের লেখা পড়ে, তাহলে তারা বুঝতে পারবে—একজন সাধারণ মানুষও বিজ্ঞানের ব্যাপারে জানার অধিকার রাখে, এবং বিজ্ঞানকে বোঝা যায় হৃদয় দিয়ে, কেবল মস্তিষ্ক দিয়ে নয়।
এই বইয়ে আমরা যেমন পাই হ্যালি নামক সেই জ্যোতির্বিদকে, যিনি নিকটতম বন্ধুকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন যাতে সে তার মহাকর্ষ তত্ত্ব প্রকাশ করতে পারে—সেই বন্ধু যার নাম নিউটন। আবার পাই মারি কিউরি কিংবা হিউমবোল্টের মতো বিজ্ঞানীদের, যাঁরা একদিকে ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাবান, অন্যদিকে সমাজের প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে গিয়ে নিজেদের চিন্তা দিয়ে পৃথিবীকে পাল্টে দিয়েছেন। ব্রাইসন আমাদের মনে করিয়ে দেন, প্রতিটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পেছনে থাকে একজন মানবিক মানুষ, যার জীবনও ছিল ভুলে, দ্বিধায়, সংকটে আর স্বপ্নে পরিপূর্ণ।
এ বইয়ে শুধু বিজ্ঞান নয়, মানুষের চিরন্তন জিজ্ঞাসারও খোঁজ রয়েছে। আমরা কেন এখানে? পৃথিবী কেন এমন? জীবন কি নিছকই এক দৈব ঘটনা? আমরা কতটা ক্ষুদ্র এই মহাবিশ্বের তুলনায়? আবার আমরা কতটা বিশাল, যদি আমাদের কল্পনা ও অনুসন্ধিৎসার পরিধি বিবেচনা করি? এইসব মৌলিক প্রশ্নকে ব্রাইসন এমনভাবে উপস্থাপন করেন, যা কিশোর থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাইকে ভাবায়। আর এটাই তাঁর লেখার সবচেয়ে বড় শক্তি—সে আপনাকে শেখায়, আবার হাসায়, আবার অজান্তেই আপনাকে বৈজ্ঞানিক ভাবনার দিগন্তে পৌঁছে দেয়।
বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য এই বইটি এক দুর্দান্ত অনুপ্রেরণা হতে পারে। বিশেষ করে যারা বিজ্ঞানে আগ্রহী, অথচ একে কঠিন মনে করে দূরে সরে যায়—তাদের জন্য এটি এক নতুন দরজা খুলে দিতে পারে। এই বই পড়ে বিজ্ঞানী হওয়ার আগেই একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ হওয়ার পথ খুলে যায়। আর এই মনোভাবটাই দরকার একটি সচেতন, প্রশ্নবোধসম্পন্ন প্রজন্ম গড়ে তুলতে।
এছাড়া নারী পাঠকদের জন্যও বইটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ব্রাইসন এমন অনেক নারী বিজ্ঞানীর গল্প বলেছেন, যাদের অবদান যুগের পর যুগ অস্বীকৃত থেকেছে কেবল লিঙ্গবৈষম্যের কারণে। এই অনালোচিত ইতিহাসগুলি বর্তমান সমাজে নারীদের বিজ্ঞানচর্চায় আরও দৃঢ় মনোবল যোগাতে পারে। বাংলাদেশে যেখানে বিজ্ঞানের জগতে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে, সেখানে এই ধরনের উদাহরণ নতুন প্রজন্মকে সাহস ও আত্মবিশ্বাস দিতে পারে।
আমাদের উচিত এমন বইকে পাঠ্যবইয়ের বাইরে পাঠ্যসূচিতে যুক্ত করা। ব্রাইসনের লেখা একদিকে যেমন সহজবোধ্য, অন্যদিকে তা চিন্তার খোরাক জোগায়। এরকম রচনাই পারে একজন শিক্ষার্থীকে পরীক্ষার চাপে নয়, বরং আনন্দে, বিস্ময়ে, জিজ্ঞাসায় বিজ্ঞান চর্চার দিকে ধাবিত করতে।
শেষ কথা হলো, A Short History of Nearly Everything কোনো একাডেমিক পাঠ্যবই নয়, বরং এটি বিজ্ঞান নিয়ে লেখা এক প্রেমপত্র। এতে আছে বিস্ময়, রস, প্রশ্ন, উত্তর, আর সর্বোপরি আছে মানুষের চিরন্তন কৌতূহলের উদযাপন। যদি আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের এই কৌতূহল বাঁচিয়ে রাখতে চাই, যদি আমরা চাই তারা শুধু পরীক্ষায় পাস করাই নয়, বিশ্বকে জানার এবং বোঝার এক অনুসন্ধানী মানসিকতা নিয়ে বড় হোক, তাহলে এই বইয়ের মতো সাহচর্য দরকার আমাদের প্রতিটি তরুণের পড়ার তালিকায়। বিজ্ঞান তখনই বাঁচে, যখন সে প্রশ্ন করতে শেখায়। আর ব্রাইসনের বই আমাদের শেখায় সেই প্রশ্ন করাটা আসলে কতটা আনন্দের, কতটা মানবিক।






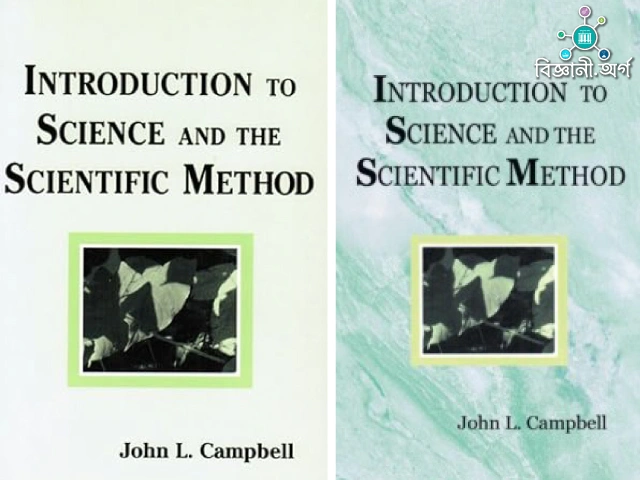

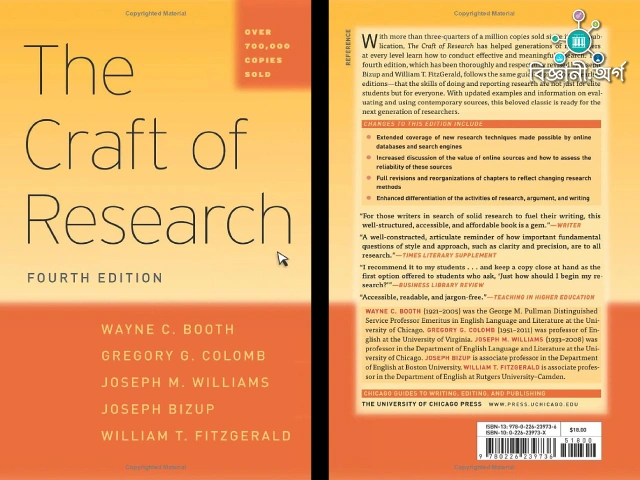
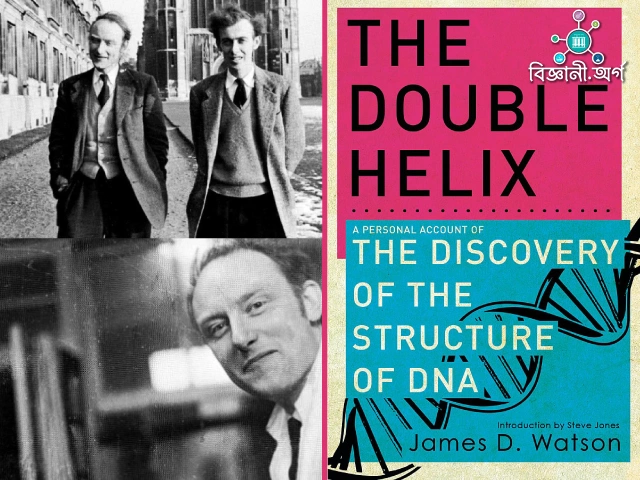
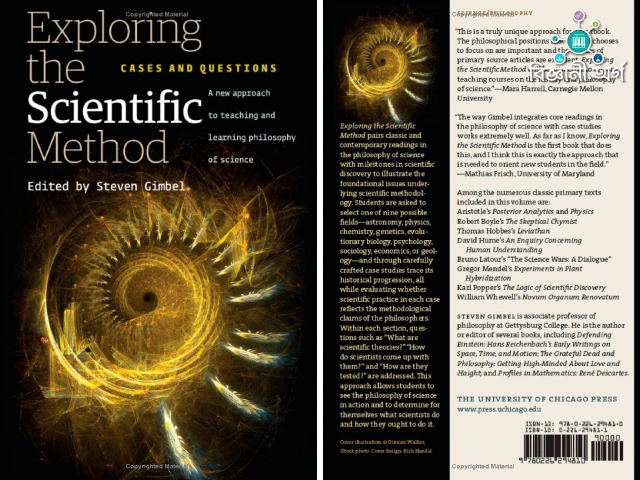
Leave a comment