ড. মশিউর রহমান
বাংলাদেশের রাজনীতি হোক বা বিশ্বের অন্যান্য দেশের ইতিহাস, বারবার একটি পরিচিত দৃশ্য আমরা দেখতে পাই। কোনো নেতা তাঁর নিজের ব্যর্থতা, অব্যবস্থাপনা বা অদূরদর্শিতার দায়ভার নিতে অস্বীকার করে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে একটি দুর্বল কিংবা কল্পিত গোষ্ঠীকে ‘প্রতিপক্ষ’ হিসেবে দাঁড় করান। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে এটি নিছক কৌশল মনে হলেও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এর পেছনে রয়েছে মানব মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং মস্তিষ্কের নিউরোকেমিস্ট্রি। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে এই প্রক্রিয়াকে বুঝে তবেই সঠিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব।
রূপান্তরমূলক নেতৃত্ব: ফ্রন্টাল লোবের শক্তি
মনোবিজ্ঞানের ভাষায় রূপান্তরমূলক নেতা (Transformational Leader) সেই ব্যক্তি, যিনি একটি জাতিকে মহৎ ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করেন। এমন নেতা মানুষকে শেখান—কীভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে নিজেদের উন্নত করা যায়।
আমাদের মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোব (Frontal Lobe) হলো যুক্তিবোধ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা এবং নৈতিকতার কেন্দ্র। কোনো নেতা যখন দূরদর্শী স্বপ্ন দেখান, তখন মানুষের ফ্রন্টাল লোব সক্রিয় হয়ে ওঠে। মস্তিষ্কে ডোপামিন নিঃসরণ হয়, তবে এটি এক ধরনের সাফল্যভিত্তিক ডোপামিন—যা লক্ষ্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রমে অনুপ্রাণিত করে। এর ফলে মানুষ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সাহসী হয়, নতুন পথ তৈরি করে এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে।
এই ধরনের নেতার কাছে প্রতিপক্ষ হলো কাঠামোগত সমস্যা—দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, বৈষম্য বা অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা। অর্থাৎ, তিনি মানুষের শক্তিকে ঘৃণার দিকে নয়, বরং উন্নতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পরিচালিত করেন।
ফটকা নেতৃত্ব: অ্যামিগডালার ভয়ভিত্তিক খেলা
অন্যদিকে, আরেক ধরনের নেতাকে আমরা বলতে পারি ‘ফটকা নেতা’। এঁদের কৌশল হলো একটি দুর্বল, কল্পিত কিংবা অপ্রাসঙ্গিক প্রতিপক্ষ তৈরি করা। তাঁরা জানেন, সেই প্রতিপক্ষ বাস্তবে কোনো বড় ক্ষতি করতে পারবে না। তবুও জনগণের সামনে সেটিকে বারবার তুলে ধরা হয়।
এটি আসলে আমাদের মস্তিষ্কের প্রাচীন অংশ অ্যামিগডালা (Amygdala)-কে সক্রিয় করার কৌশল। অ্যামিগডালা হলো ভীতি, রাগ আর হুমকির প্রতিক্রিয়া কেন্দ্র। কোনো নেতা যখন বলেন—“বিদেশি চক্রান্ত চলছে” বা “অমুক গোষ্ঠী দেশ ধ্বংস করতে চাইছে”—তখন সাধারণ মানুষের অ্যামিগডালা সক্রিয় হয়। যুক্তিবোধের জায়গা দখল করে নেয় ‘বাঁচাও বা পালাও’ (Fight or Flight) প্রবৃত্তি।
আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের এক গবেষণায় দেখা গেছে, হুমকির মুখে পড়লে মানুষের জটিলভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা (Cognitive Load) কমে যায়। অর্থাৎ তখন আর যুক্তিনির্ভর আলোচনায় মানুষের মন যায় না; বরং আবেগই মূল চালিকা শক্তি হয়ে ওঠে। এই দুর্বল মুহূর্তকেই ফটকা নেতারা কাজে লাগান।
ইতিহাসের পাতা: হিটলার থেকে বর্তমান
মানব ইতিহাসে এর বহু দৃষ্টান্ত আছে। সবচেয়ে ধ্রুপদী উদাহরণ হলো আডলফ হিটলার। যিনি ব্যবহার করেছিলেন ‘বলির পাঁঠা’ রাজনীতি।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানি ছিল চরম অর্থনৈতিক মন্দা আর সামাজিক হতাশায় ভরা। জনগণের ক্ষোভ ও অনিশ্চয়তাকে হিটলার ইহুদি জনগোষ্ঠীর ওপর চাপালেন। বাস্তবে ইহুদিরা জার্মানির অর্থনৈতিক মন্দার জন্য দায়ী ছিল না, কিন্তু হিটলার তাদেরকে ‘শত্রু’ বানালেন। ফলে সাধারণ মানুষ জটিল সমস্যাগুলো ভুলে গিয়ে একটি দৃশ্যমান প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলো। এখানে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায়—হিটলার জনগণের অ্যামিগডালার ভীতি প্রতিক্রিয়া সক্রিয় করেছিলেন। যুক্তিসঙ্গত সমাধান না দিয়ে তিনি ভয়ের আবেগকে কাজে লাগিয়েছিলেন।
আজকের পৃথিবীতেও এর ব্যতিক্রম নেই। দক্ষিণ এশিয়া থেকে শুরু করে ইউরোপ-আমেরিকা পর্যন্ত বহু নেতাকে দেখা যায় যারা বারবার ‘বিদেশি ষড়যন্ত্র’, ‘বিগত সরকার’, কিংবা ‘বিশেষ মতাদর্শের গোষ্ঠী’-কে দায়ী করে নিজের ব্যর্থতা আড়াল করেন।
এটি মূলত জনগণের মনে ধ্রুবক ভয় তৈরি করার কৌশল। ভয় থাকলেই নেতা নিজেকে ‘রক্ষাকর্তা’ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারেন। এভাবে জনগণ নেতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং তাঁকে সমালোচনা করার প্রবণতা হারায়।
ফটকা নেতাদের কি অস্ত্র?
দ্বিতীয় শ্রেণীর এই ফটকাবাজ নেতাদের মূলথ দুটি অস্ত্র। প্রথমটি হল স্কেপগোটিং (Scapegoating) অর্থাৎ ব্যর্থতার দায় অন্য কারও ওপর চাপানো। যেমন—অর্থনৈতিক দুর্দশার দায় প্রতিপক্ষ দলের ওপর ফেলা। এবং দ্বিতীয় অস্ত্রটি হল কর্তৃত্ববাদে আকর্ষণ (Authoritarian Appeal) অর্থাৎ মানুষকে বোঝানো যে শক্ত হাতে শাসনই নিরাপত্তার একমাত্র ভরসা। ভয়ের মুহূর্তে জনগণ স্বাধীনতার বিনিময়ে নিরাপত্তা চাইতে শুরু করে।
শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজমনোবিজ্ঞানী ড. এলেন ফস্টার ব্যাখ্যা করেছেন, ভয়ভিত্তিক রাজনীতি মানুষকে কর্তৃত্ববাদী শাসনের দিকে টেনে নেয়। মানুষ তখন জটিল সমস্যাকে সরল করে দেখতে চায় এবং এমন নেতার কাছে আত্মসমর্পণ করে যিনি ‘শক্ত হাতে ব্যবস্থা নেবেন’ বলে আশ্বাস দেন।
বিজ্ঞান যা শেখায়: সচেতন নাগরিকের ভূমিকা
এখন প্রশ্ন হলো—আমরা কীভাবে বুঝব কোনো নেতা রূপান্তরমূলক নাকি ফটকা নেতা? এখানে বিজ্ঞানের শিক্ষা জরুরি। প্রথমত, দায়ভারের স্বচ্ছতা। নেতা কি ব্যর্থ হলে তথ্য-প্রমাণ দিয়ে ব্যাখ্যা করেন, নাকি সবসময় অন্যের দিকে আঙুল তোলেন? দ্বিতীয়ত, লক্ষ্যের প্রকৃতি। তিনি কি দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা ও উন্নয়ন নিয়ে কথা বলেন, নাকি কেবল প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার পরিকল্পনা করেন? তৃতীয়ত আবেগের ধরণ। তাঁর বক্তব্য কি আশা ও সাহস জাগায়, নাকি ভীতি ও ঘৃণা উসকে দেয়?
একজন বিজ্ঞানমনস্ক তরুণ যদি নিজের ফ্রন্টাল লোব সক্রিয় রাখেন—অর্থাৎ যুক্তি, প্রমাণ ও দীর্ঘমেয়াদী চিন্তাভাবনা ব্যবহার করেন—তাহলে তিনি প্রতিপক্ষ রাজনীতির ফাঁদে পা দেবেন না।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষা
বাংলাদেশ একটি তরুণপ্রধান দেশ। এখানে প্রায় অর্ধেক জনগণ ৩০ বছরের নিচে। এই তরুণ প্রজন্ম যদি ভীতি ও বিভাজনের রাজনীতির শিকার হয়, তাহলে উন্নয়নের পথে বাধা তৈরি হবে। কিন্তু যদি তারা বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নেতৃত্বকে মূল্যায়ন করতে শেখে, তবে রাজনীতি হবে আরও জবাবদিহিমূলক।
তরুণদের জন্য তাই কিছু করণীয় হল, প্রথমত, সামাজিক মাধ্যমে যেসব প্রচারণা শুধু ভয় বা ঘৃণা ছড়ায়, তা চিনে ফেলা। দ্বিতীয়ত, নেতার কথার পেছনে যুক্তি খুঁজে দেখা—কেবল আবেগে ভেসে যাওয়া নয়। এবং তৃতীয়ত, তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে মত গঠন করা।
পরিশেষে বলবো, নেতৃত্বের মনোবিজ্ঞান আমাদের শেখায়—ভয় ও আশা একই সঙ্গে মানুষের মস্তিষ্ককে চালিত করে। প্রকৃত নেতা মানুষের আশা জাগায়, আর ফটকা নেতা মানুষের ভয়কে কাজে লাগান।
যে নেতা আপনাকে উন্নয়নের স্বপ্ন দেখান না, কেবল একটি শত্রুর দিকে আঙুল তোলেন—তিনি আসলে আপনার মস্তিষ্কের অ্যামিগডালাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান। আর যে নেতা শিক্ষা, উন্নয়ন ও সমাধানের পথে আহ্বান জানান—তিনি আপনার ফ্রন্টাল লোবকে সক্রিয় করতে চান।
বিজ্ঞান আমাদের শেখায়, কোন পথ বেছে নিলে সমাজ এগোবে, আর কোন পথে গেলে আমরা বারবার একই ফাঁদে আটকে যাব। তাই একজন তরুণ নাগরিকের দায়িত্ব হলো—ভয়ের রাজনীতি চিনে নেওয়া এবং আশার রাজনীতি দাবি করা। কেবল তাহলেই আমরা একটি স্বপ্নময়, উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারব।


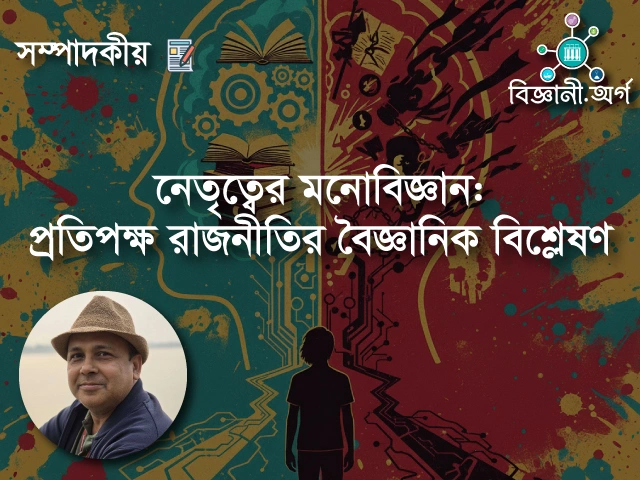



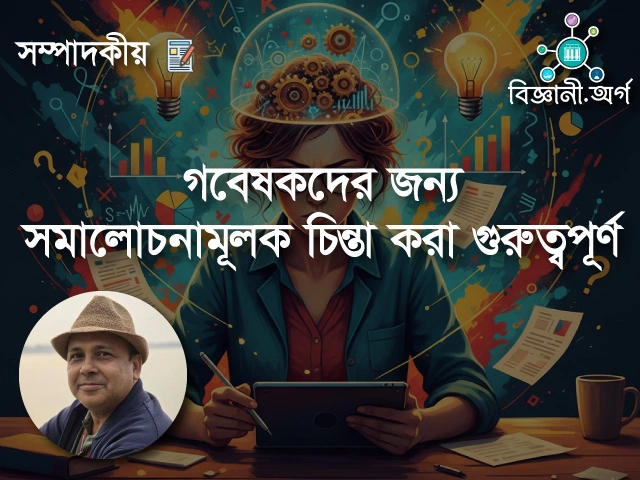
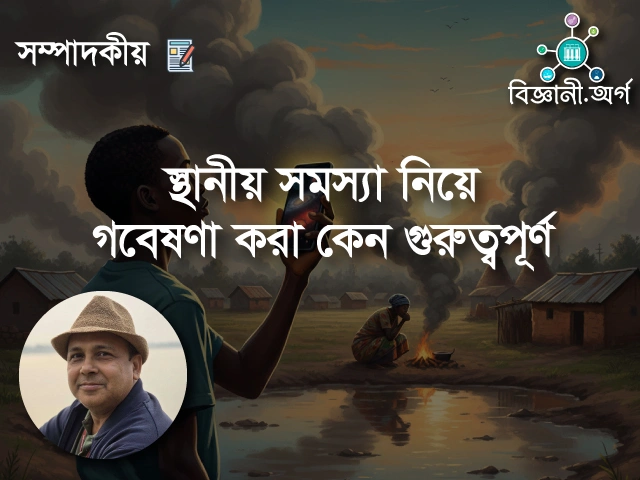
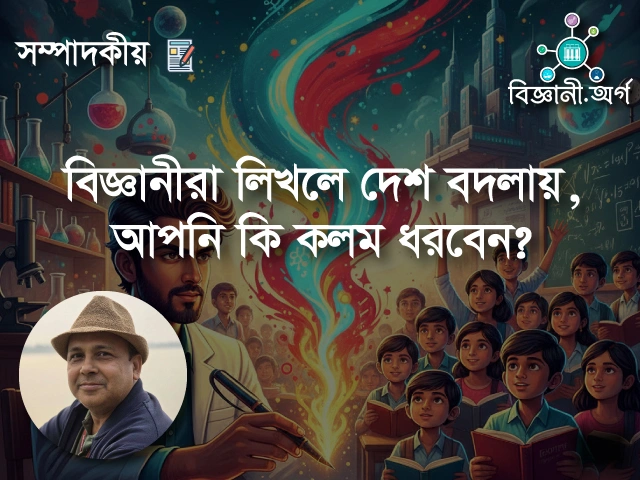
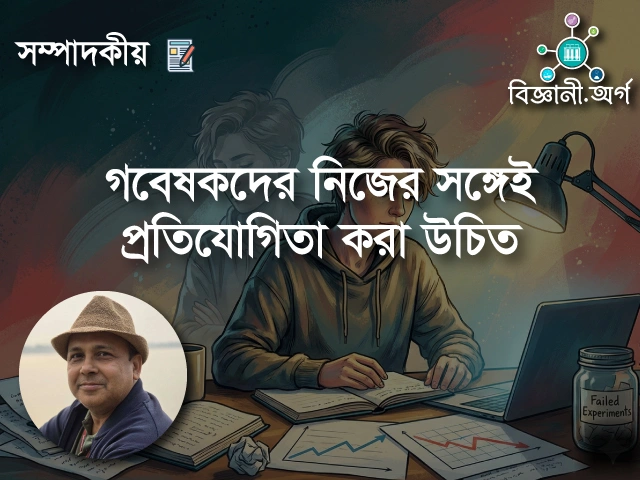
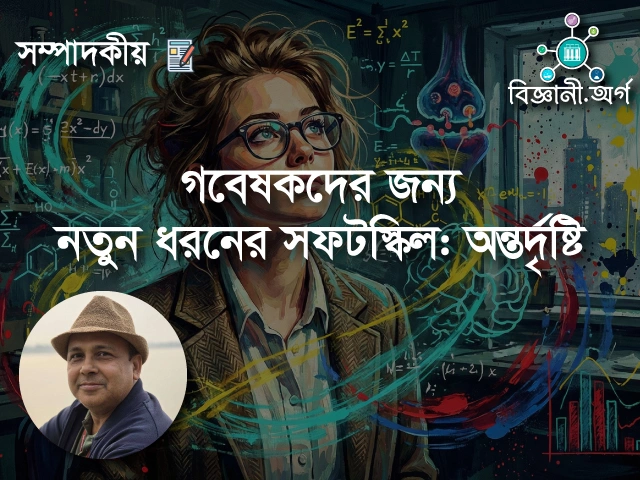
Leave a comment