ড. মশিউর রহমান
বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা নিয়ে আমরা অনেক কথা বলি। কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো নিয়ে, কখনো বাজেট কিংবা গবেষণা অনুদান নিয়ে। কিন্তু এক মৌলিক প্রশ্ন আমাদের অদেখাই থেকে যায়—আমরা কি কেবল গবেষণার সংখ্যা বাড়াচ্ছি, নাকি সত্যিকার অর্থে গবেষক তৈরি করছি? গবেষণা আর গবেষক—এই দুইয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম কিন্তু গভীর পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটি তথ্য ও উপাত্ত উৎপাদন করে, দ্বিতীয়টি সমাজে রূপান্তর আনে। আমরা কি এই পার্থক্যটি বুঝতে শিখেছি?
গবেষক উন্নয়ন কী?
গবেষক উন্নয়ন কেবল একটি পিএইচডি ডিগ্রি বা গবেষণাপত্র প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়া যেখানে একজন তরুণ গবেষক তাঁর ব্যক্তিগত দক্ষতা, পেশাগত প্রস্তুতি, নেতৃত্ব, সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও সমাজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ক্ষমতা অর্জন করেন। সহজ ভাষায় বললে, গবেষণা মানে তথ্য তৈরি করা, আর গবেষক উন্নয়ন মানে সেই তথ্যকে জ্ঞান, আর সেই জ্ঞানকে সমাজের প্রয়োজনীয় সমাধানে রূপান্তর করার সামর্থ্য তৈরি করা।
আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট
২০০২ সালে যুক্তরাজ্যের Set for Success নামক একটি রিপোর্টে বলা হয়েছিল, পিএইচডি শিক্ষার্থীরা শুধু একাডেমিক জগতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, অথচ তাদের বেশিরভাগকে পরে শিল্প, নীতি কিংবা ভিন্ন খাতে কাজ করতে হয়। ফলে নেতৃত্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, কিংবা নেটওয়ার্কিংয়ের অভাবে তারা পিছিয়ে পড়ছে। সেই প্রতিবেদন থেকেই যুক্তরাজ্যে ‘Vitae’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গবেষক উন্নয়নকে কাঠামোবদ্ধ করে। এখন ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক উন্নয়ন একটি নীতিগত অঙ্গ।
ভারতও এই দিকটিতে এগিয়ে গেছে। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স (IISc) কিংবা আইআইটি-গুলোতে এখন গবেষণা-প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ‘ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সেল’ চালু রয়েছে। সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (NUS) গবেষকদের জন্য বাধ্যতামূলক নেতৃত্ব ও উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করেছে। চীনে “ট্যালেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম” এখন জাতীয় গবেষণা নীতির অংশ, যেখানে পিএইচডি ও পোস্টডক গবেষকদের বিদেশে সহযোগিতা, শিল্পের সঙ্গে যৌথ গবেষণা এবং নীতি-পরামর্শে যুক্ত করা হয়।
তাহলে প্রশ্ন হলো—বাংলাদেশে আমরা কী করছি? আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি গবেষক উন্নয়নকে গুরুত্ব দিচ্ছে, নাকি এখনও কেবল থিসিস জমা আর ডিগ্রি প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ?
বাংলাদেশের বাস্তবতা
আমাদের গবেষণা তহবিল সীমিত, অবকাঠামো দুর্বল। তবুও আমাদের তরুণরা মেধাবী। তারা প্রতিনিয়ত আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের প্রমাণ করছে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, তারা গবেষণায় দক্ষ হলেও বৈশ্বিক পরিসরে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে হিমশিম খাচ্ছে। এর পেছনে কারণ হলো দুর্বল ইংরেজি লেখনী, প্রেজেন্টেশন দক্ষতার অভাব, আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কে প্রবেশের সীমাবদ্ধতা এবং নেতৃত্বে অদক্ষতা।
বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি শিক্ষার্থীদের এই বাস্তবতার জন্য প্রস্তুত করছে? নাকি তারা শুধু পরীক্ষার নম্বর আর থিসিস পৃষ্ঠার সংখ্যা গুনছে? এ প্রশ্ন আজ আমাদের করতেই হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব
বিশ্ববিদ্যালয় কোনো ডিগ্রি-বিতরণ যন্ত্র নয়। এটি সমাজের জ্ঞান উৎপাদনের কেন্দ্র। তাই এর দায়িত্ব কেবল গবেষণা নয়, গবেষক তৈরি করা। এজন্য প্রয়োজন—
- নেতৃত্ব, যোগাযোগ ও লেখালিখি নিয়ে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ।
- ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, আন্তর্জাতিক মেন্টরশিপ ও ইন্টার্নশিপ সুযোগ।
- শিল্প ও নীতি পর্যায়ের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ তৈরি।
- আন্তঃবিষয়ক গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে দলগত কাজ শেখানো।
সিঙ্গাপুরের মতো দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষকদের জন্য ‘ডিজিটাল টুইন’ প্ল্যাটফর্মে শহর পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করার সুযোগ দেয়। ভারতে গবেষকরা স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে যুক্ত হয়। আর আমরা? আমাদের গবেষকরা কতটা প্রস্তুত বৈশ্বিক মঞ্চে এসব প্রতিযোগিতার জন্য?
গবেষক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা
আজকের পৃথিবীতে একা একা গবেষণা করার যুগ শেষ। জলবায়ু পরিবর্তন, মহামারি, খাদ্য সংকট, কিংবা জ্বালানি নিরাপত্তা—এসব সমস্যার সমাধানে একাধিক বিষয়ে দক্ষতা এবং বহুজাতিক সহযোগিতা দরকার। তাই একজন গবেষকের কেবল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকলেই চলবে না, তাকে হতে হবে দলনেতা, যোগাযোগকারী, এমনকি কখনো নীতিনির্ধারকদেরও পরামর্শদাতা। গবেষক উন্নয়ন ছাড়া আমরা কেবল অর্ধেক গবেষক তৈরি করি—যারা হয়তো বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রবন্ধ ছাপাতে পারবে, কিন্তু সমাজে প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনতে পারবে না।
নীতিনির্ধারকদের প্রতি বার্তা
বাংলাদেশ যদি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির স্বপ্ন দেখে, তবে এখনই সময় গবেষক উন্নয়নকে শিক্ষা নীতির মূল অংশ করা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC) ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একসাথে নীতিগত পদক্ষেপ নিতে পারে। প্রয়োজন হবে—
১. জাতীয় পর্যায়ে গবেষক উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন।
২. প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে “Researcher Development Cell” চালু।
৩. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বিনিময় প্রোগ্রামের সম্প্রসারণ।
৪. গবেষক উন্নয়ন প্রশিক্ষণকে পিএইচডি ও এমএসসি প্রোগ্রামের বাধ্যতামূলক অংশ করা।
শেষকথা
আমাদের তরুণরা অত্যন্ত মেধাবী। তারা যদি সঠিক প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনা পায়, তবে তারা কেবল বাংলাদেশ নয়, বৈশ্বিক মঞ্চে দেশের নাম উজ্জ্বল করবে। কিন্তু যদি আমরা এখনো গবেষক উন্নয়নকে অবহেলা করি, তবে আমরা হয়তো অনেক ডিগ্রি বিতরণ করব, অনেক গবেষণাপত্র ছাপাব, কিন্তু বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশকে যে জ্ঞানসমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চাই—সেই স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যাবে।
প্রশ্ন হলো— আমরা কি প্রস্তুত আমাদের তরুণদের মধ্যে এই বিনিয়োগ করতে?


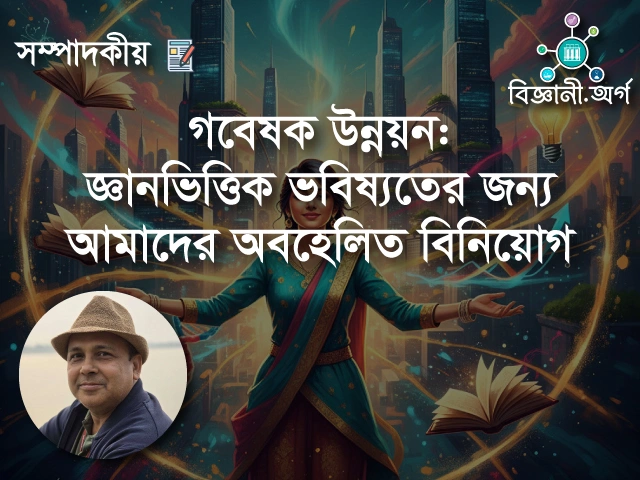

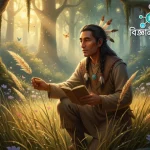

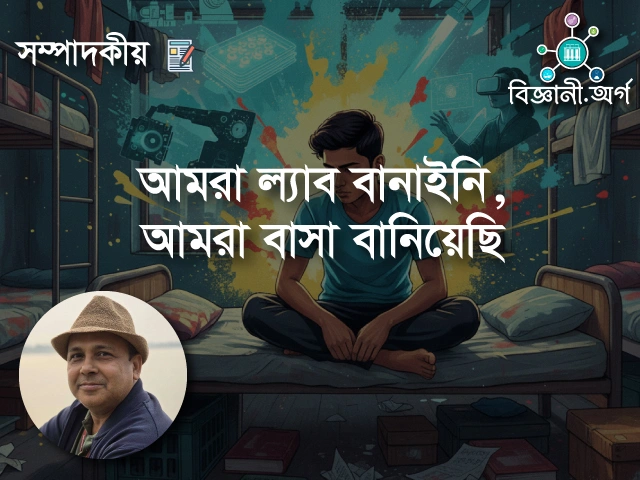
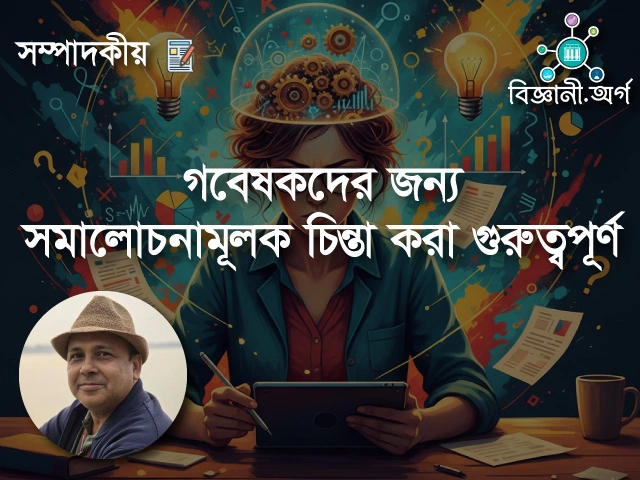
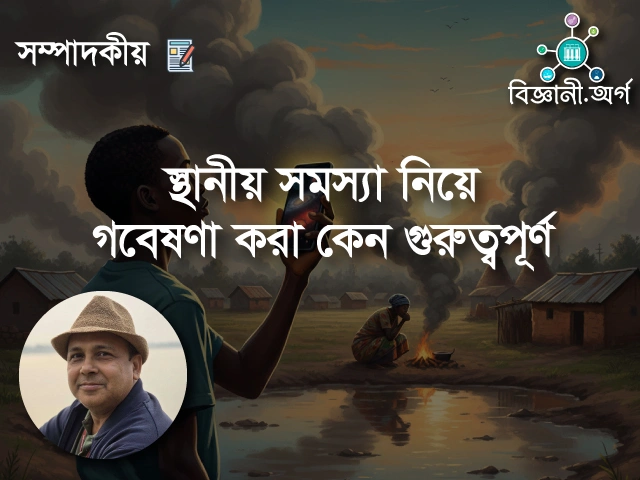
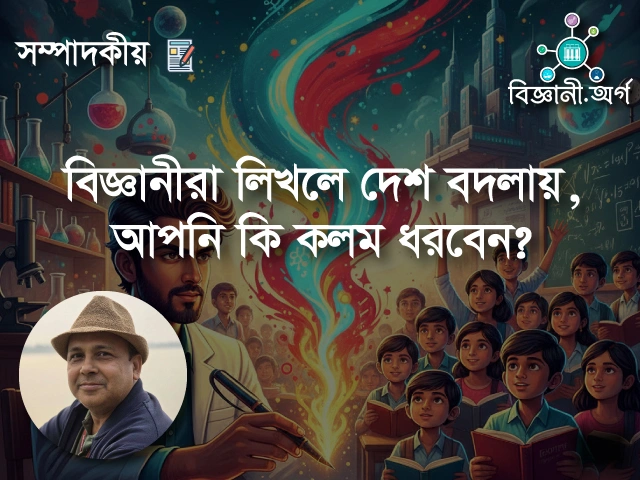
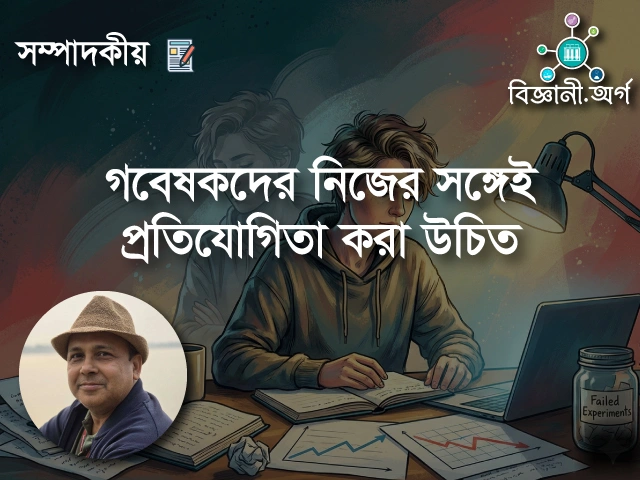
Leave a comment