১৯৯০-এর দশকে ব্রেইন স্টেম স্ট্রোকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন ফরাসি সাংবাদিক জঁ-দমিনিক বোবি। কথা বলতে বা লিখতে না পারলেও, তিনি এক অসাধারণ পদ্ধতিতে নিজের গল্প লিখে গেছেন—সহকারী বারবার অক্ষরমালা পড়ে শোনাতেন, আর তিনি কেবল বাম চোখের পলক ফেলে সঠিক অক্ষরটি বেছে নিতেন। সেই ধৈর্য ও কষ্টের কাহিনি দ্য ডাইভিং বেল অ্যান্ড দ্য বাটারফ্লাই বই হয়ে আমাদের সামনে এসেছে। কিন্তু আজ, তিন দশক পর, প্রযুক্তি অনেকদূর এগিয়েছে। যারা ALS (অ্যামিওট্রফিক ল্যাটারাল স্ক্লেরোসিস) বা ব্রেইন স্টেম স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে কথা বলার ক্ষমতা হারিয়েছেন, তারা এখন অনেক দ্রুত ও স্বাচ্ছন্দ্যে যোগাযোগ করতে পারছেন, কখনও কেবল চোখের নড়াচড়া দিয়ে, কখনও সূক্ষ্ম মাংসপেশির টান দিয়ে। আর এইসবের অগ্রভাগে রয়েছে ব্রেইন-কম্পিউটার ইন্টারফেস বা BCI প্রযুক্তি।
সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এক ধাপ এগিয়ে গেলেন—এবার কথা বলার চেষ্টাও নয়, শুধু মনে মনে ভাবলেই কম্পিউটার তা রিয়েল-টাইমে লিখে দেবে। নতুন এই ‘ইনার স্পিচ’ বা মনের ভাষা পাঠোদ্ধার প্রযুক্তি আমাদের যোগাযোগের ধারা আমূল বদলে দিতে পারে। এতদিন যে BCI ডিভাইসগুলো ‘অ্যাটেম্পটেড স্পিচ’ বা উচ্চারণের চেষ্টার উপর নির্ভর করত, তা ব্যবহারকারীর জন্য অনেক সময় ক্লান্তিকর ছিল। কারণ এই ডিভাইসগুলো মোটর কর্টেক্সে বসানো সেন্সর থেকে সংকেত নিয়ে তা শব্দে রূপান্তর করে। ব্যবহারকারীকে শ্বাস নিয়ে মুখের পেশি নড়ানোর মতো আচরণ করতে হত, যদিও শব্দ বের হত না। শ্বাসকষ্ট বা শারীরিক সীমাবদ্ধতার কারণে একটি শব্দ বলতেও কয়েকবার শ্বাস নিতে হত। তাছাড়া মুখভঙ্গি ও অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দ ব্যবহারকারীর অস্বস্তির কারণ হতো।
কিন্তু মোটর কর্টেক্স কেবল উচ্চারণের চেষ্টায়ই সক্রিয় হয় না, কল্পিত উচ্চারণ বা মনে মনে কথা বলার সময়ও এর কিছু অংশ সক্রিয় থাকে। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক এরিন কুনজ ও তাঁর সহকর্মীরা সেই বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করেছেন নতুন ‘ইনার স্পিচ’ ডিকোডার। সম্প্রতি Cell জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণায় চারজন অংশগ্রহণ করেছিলেন—তিনজন ALS রোগী ও একজন ব্রেইন স্টেম স্ট্রোকে আক্রান্ত ব্যক্তি—যাদের আগেই মোটর কর্টেক্সে সেন্সর বসানো ছিল। পরীক্ষায় দেখা গেছে, তারা শুধু একটি বাক্য মনে মনে ভাবলেই স্ক্রিনে তা তৎক্ষণাৎ ভেসে উঠছে। আগের প্রযুক্তিতে যেখানে শব্দভাণ্ডার সীমিত ছিল কয়েক ডজন শব্দে, সেখানে নতুন সিস্টেমে ১ লক্ষ ২৫ হাজার শব্দের অভিধান ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে।
সবচেয়ে বড় সাফল্য এসেছে গতির দিক থেকে। আগে যেখানে মিনিটে মাত্র কয়েকটি শব্দ বলা যেত, নতুন প্রযুক্তিতে মিনিটে ১২০ থেকে ১৫০ শব্দ বলা সম্ভব হয়েছে—প্রায় স্বাভাবিক কথোপকথনের সমান। এবং এর জন্য প্রয়োজন কেবল মনের মধ্যে বাক্যটি গঠন করা, মুখের পেশি নড়ানোর বা শ্বাসের কোনও বাড়তি প্রচেষ্টা নয়। এক অংশগ্রহণকারী মজা করে বলেছেন, এতদিন ধীরগতির কারণে কথোপকথনে অন্যকে থামিয়ে নিজের কথা বলার সুযোগই মিলত না, এখন আবার তিনি সেটা করতে পারবেন।
তবে এই প্রযুক্তি সবার জন্য কার্যকর নয়। বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক আলেকজান্ডার হাথের ব্যাখ্যায়, কথা বলার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া শুরু হয় মনের মধ্যে একটি ধারণা দিয়ে, যা পরে রূপ নেয় উচ্চারণের জন্য প্রয়োজনীয় পেশি নড়ানোর পরিকল্পনায়, আর শেষে সেই পরিকল্পনা কার্যকর হয়। অনেক রোগীর ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা-প্রস্তুতির ধাপ অক্ষত থাকে, কিন্তু পরিকল্পনা থেকে পেশি-নড়াচড়ার ধাপটি নষ্ট হয়ে যায়। নতুন ‘ইনার স্পিচ’ প্রযুক্তি সেই প্রথম ধাপটিকে ধরতে পারে, তাই যাদের ক্ষেত্রে ধারণা থেকে পরিকল্পনায় রূপান্তর ঠিকঠাক হয়, তারাই এ থেকে উপকৃত হবেন।
ব্যক্তিগত পর্যায়ে এই গবেষণার সাথে কুনজের সম্পর্কও গভীর। তাঁর বাবা ALS-এ আক্রান্ত হয়ে কথা বলার ক্ষমতা হারিয়েছিলেন। জীবনের শেষ দিকে কুনজই বাবার ব্যক্তিগত ‘স্পিচ ট্রান্সলেটর’ হয়ে উঠেছিলেন, কারণ তাঁর কথাই বাবার ভাষা সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারত। এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে ব্রেইন-প্রস্থেটিক্স গবেষণায় নিয়ে এসেছে। তাই তিনি জানেন, কারও হারানো কণ্ঠ ফিরিয়ে আনার মূল্য কতটা।
অবশ্যই, মনের কথা পড়ার প্রযুক্তি মানসিক গোপনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এই কারণে গবেষক দল একটি বিশেষ ‘কোড ফ্রেজ’ যুক্ত করেছে—যেমন “চিটি চিটি ব্যাং ব্যাং”—যা মনে মনে বললে ডিভাইস লেখা শুরু বা বন্ধ করবে। ফলে ব্যবহারকারী ঠিক করতে পারবেন কখন তিনি নিজের ভাবনা প্রকাশ করতে চান।
গবেষকরা বলছেন, এই গবেষণার সবচেয়ে বড় অবদান আসলে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে। তারা হয়তো নিজেরা তাৎক্ষণিকভাবে বড় কোনও সুবিধা পাবেন না, তবু ভবিষ্যতের জন্য, পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যে, স্বেচ্ছায় সময় ও প্রচেষ্টা দিয়েছেন। কুনজের ভাষায়, “তারা অসাধারণ মানুষ, এবং এই প্রযুক্তির বিকাশে তাদের অবদান অনন্য।”
এই উদ্ভাবন কেবল চিকিৎসা প্রযুক্তির একটি মাইলফলক নয়, মানবিক যোগাযোগের ধারণাকেও পুনর্নির্মাণ করছে। ভবিষ্যতে হয়তো আমরা এমন এক পৃথিবীতে পৌঁছাব, যেখানে কথা বলার জন্য কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন থাকবে না—শুধু ভাবলেই তা অন্যের কাছে পৌঁছে যাবে। তবে সেই সঙ্গে থাকবে নৈতিক ও গোপনীয়তার জটিল প্রশ্ন, যার সঠিক উত্তর খুঁজতে হবে বিজ্ঞানী ও সমাজকে মিলেই। প্রযুক্তি যত উন্নত হবে, ততই এই ভারসাম্য রক্ষা করা হবে আসল চ্যালেঞ্জ।










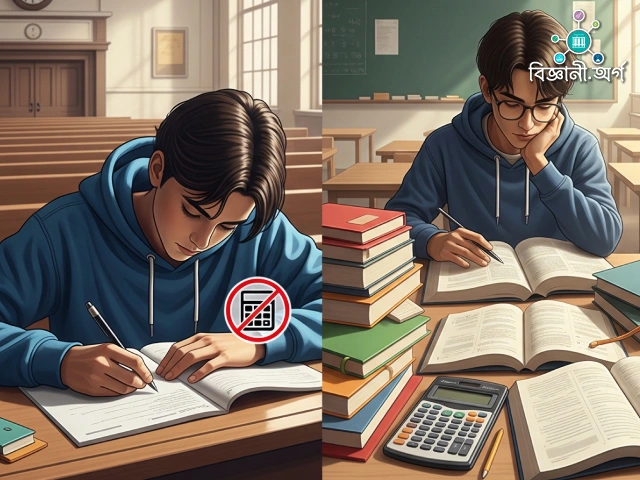
Leave a comment