ড. মশিউর রহমান
আন্তর্জাতিক গবেষণা আজ এমন এক বাস্তবতা, যা কোনো দেশের সীমারেখায় আটকে নেই। নতুন জ্ঞান সৃষ্টির প্রতিটি প্রচেষ্টা এখন আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—কীভাবে একজন তরুণ গবেষক নিজেকে এই বৈশ্বিক নেটওয়ার্কে যুক্ত করতে পারে? সম্প্রতি জাপানের JST Plus Alpha Series–এর একটি সেমিনারে কয়েকজন গবেষক তাঁদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন। তাঁদের কথাগুলো শুধু জাপানি গবেষক নয়, বাংলাদেশের তরুণ বিজ্ঞানীদের জন্যও প্রাসঙ্গিক ও অনুপ্রেরণাদায়ক।
কোয়ান্টাম কম্পিউটারের গবেষক রিকেন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক এরিকা কাওয়াকামি তাঁর অভিজ্ঞতা শোনাতে গিয়ে বলেন, নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে গবেষণার মূল বিষয়কে কেন্দ্র করেই। তিনি ইউরোপ ও জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা ও গবেষণার সময় যেভাবে সাহস করে অচেনা মানুষকে ই-মেইল করেছেন, বা আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আগে বক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন—তা এক ধরণের সক্রিয় মানসিকতার দিকনির্দেশনা। অনেক সময় উত্তর পাওয়া যায়নি, আবার কখনো সে যোগাযোগই হয়ে উঠেছে সহযোগী গবেষণার ভিত্তি। তাঁর মতে, গবেষণার প্রতি আন্তরিকতা ও কৌতূহলই আসল শক্তি, যা অচেনা দরজা খুলে দেয়।
অন্যদিকে, সুকুবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিরোকো তেরাজাওয়া আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক তৈরির আগে নিজের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্যে ভরপুর ছিল আত্মবিশ্বাস হারানো তরুণদের জন্য পরামর্শ। গবেষণার শুরুতে অনেকেই নিজেদের অযোগ্য মনে করেন, অথচ নেটওয়ার্কিং শুরু হয় নিজেকে মেনে নেওয়া থেকে। নিজের দুর্বলতাকে আড়াল না করে বরং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মানুষের সঙ্গে কথা বলাই তাঁকে সাহায্য করেছে দীর্ঘস্থায়ী বৈজ্ঞানিক বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে। তাঁর কথায়, “নেটওয়ার্কিং মানে বিখ্যাত কারও সঙ্গে সম্পর্ক গড়া নয়, বরং যাদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে বোঝাপড়া হয়, তাদের সঙ্গেই সম্পর্ক টিকে যায়।”
ওয়াশিংটনে অবস্থিত JST–এর প্রতিনিধি ইউকো সুদা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ, আমেরিকায় গবেষণার পরিবেশ এমনিতেই আন্তর্জাতিক। গবেষণার তহবিল, মানবসম্পদ এবং বহুমুখী কর্মপথ এই নেটওয়ার্ককে সবসময় প্রসারিত করেছে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, বিশেষ করে রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ, সহযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন সীমারেখা তৈরি করেছে। অনেক মার্কিন প্রতিষ্ঠান এখন রাশিয়া বা চীনের গবেষকদের সঙ্গে যৌথ প্রকল্পে অংশ নিতে দ্বিধাগ্রস্ত। এ অভিজ্ঞতা শুধু আমেরিকাই নয়, ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশেও প্রতিফলিত হচ্ছে, যা আন্তর্জাতিক গবেষণা নেটওয়ার্কের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই আলোচনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের তরুণ গবেষকরা প্রায়ই বিদেশে পড়াশোনা বা কনফারেন্সে অংশগ্রহণের সুযোগ পান না। অনেকে মনে করেন, বিদেশে না গেলে আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক তৈরি সম্ভব নয়। কিন্তু আলোচনায় উঠে এসেছে, বিদেশে না গিয়েও নেটওয়ার্ক গড়া সম্ভব। সাহস করে একটি ই-মেইল পাঠানো, গবেষণার প্রশ্ন শেয়ার করা, কিংবা অনলাইন কনফারেন্সে সক্রিয় থাকা—এসবই কার্যকর পদক্ষেপ। আসল শর্ত হলো আন্তরিক গবেষণা-উদ্দীপনা ও ক্রমাগত শেখার মানসিকতা।
তবে শুধু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা নয়, নীতি পর্যায়েও এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বৈশ্বিক পরিস্থিতি বদলাচ্ছে দ্রুত। একদিকে প্রযুক্তি সহযোগিতা হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির হাতিয়ার, অন্যদিকে গবেষণা সহযোগিতা সীমিত হয়ে পড়ছে জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে। বাংলাদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো যদি সত্যিকার অর্থে আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কে নিজেদের যুক্ত করতে চায়, তবে প্রয়োজন হবে একটি কৌশলগত অবস্থান গ্রহণের। অর্থাৎ কোন কোন দেশে বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা স্থাপন করা হবে, সেটি স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা জরুরি।
এখানে তরুণ গবেষকদের জন্য একটি বড় শিক্ষা হলো—আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গড়া কেবল বৈজ্ঞানিক দক্ষতার ব্যাপার নয়, বরং কূটনৈতিক প্রজ্ঞা ও আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগেরও অনুশীলন। গবেষণায় আগ্রহী একজন বাংলাদেশি ছাত্রের হয়তো এখনই ল্যাবে বড় আবিষ্কার করার সুযোগ নেই। কিন্তু সে সাহস করে বিদেশি গবেষককে প্রশ্ন পাঠাতে পারে, কনফারেন্সে আলোচনায় অংশ নিতে পারে, কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় যুক্ত হতে পারে। এভাবেই ছোট ছোট পদক্ষেপ থেকে জন্ম নেয় বৈশ্বিক সহযোগিতার গল্প।
অবশেষে, এই আলোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পথনির্দেশনা। একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান একা চলার পথ নয়। সীমান্ত অতিক্রম করে যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা তৈরি হয়, সেটিই আজকের গবেষণার আসল সম্পদ। বাংলাদেশের তরুণরা যদি এখন থেকেই নিজেদেরকে এই বৈশ্বিক আলোচনার অংশীদার হিসেবে গড়ে তোলে, তবে বিজ্ঞান শুধু তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে নয়, জাতীয় অগ্রগতিতেও অবদান রাখবে।
সূত্র: Japan Science and Technology Agency এর একটি অনুষ্ঠানের বক্তব্য থেকে লেখাটি লিখিত


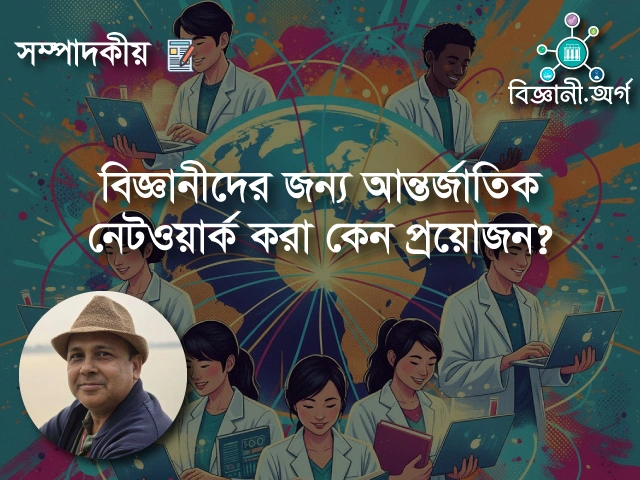



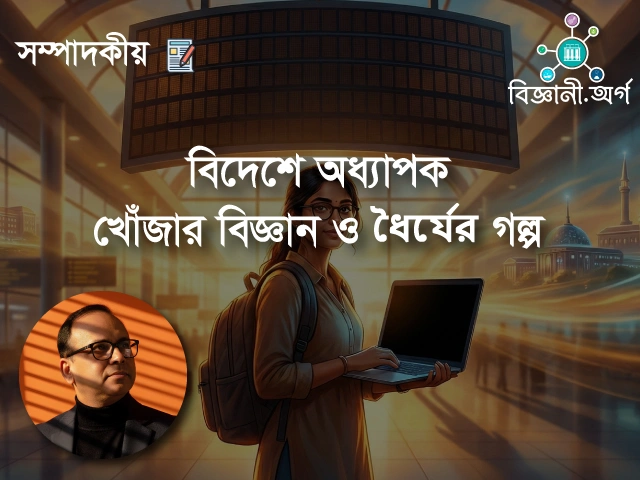
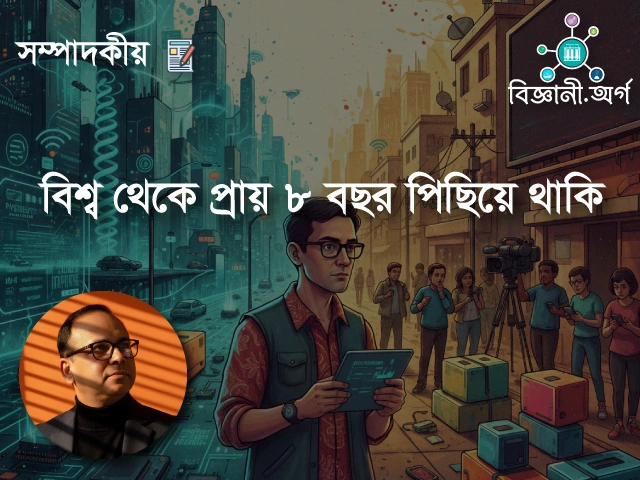
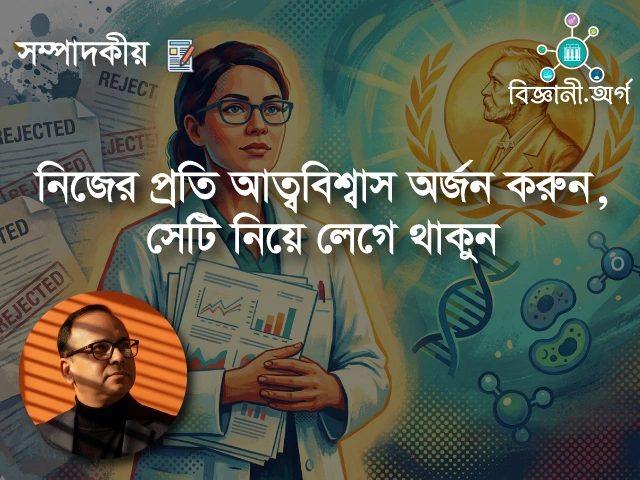

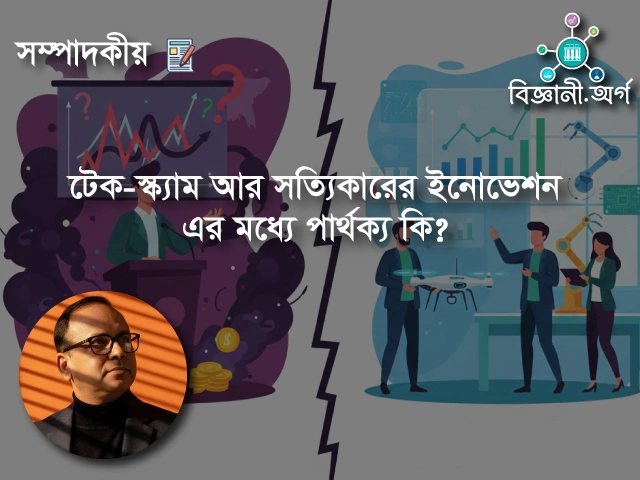
Leave a comment