বাংলাদেশের উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যবইয়ের পাতা উল্টালেই আজকাল একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়। বিজ্ঞানের মতো স্থির ও পরীক্ষিত সত্যকেও সেখানে যেন বারবার নতুন করে সাজানো হচ্ছে। গত বছর যা সত্য ছিল, এ বছর এসে সেটি মিথ্যা হয়ে যায়। আবার নতুন কোনো সংস্করণ হাতে নিলে দেখা যায়, পুরোনো তথ্য কেটে দিয়ে বসানো হয়েছে একেবারে ভিন্ন সংখ্যা। শিক্ষার্থীর চোখে তখন বই নয়, মনে হয় যেন এটি বিজ্ঞানের নামধারী কোনো পরীক্ষাগার, যেখানে প্রতি বছর নতুন করে তথ্যের টুকরো টুকরো খেলা চলে।
প্রাণিবিজ্ঞানের বইতে এর অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। আগে যেখানে লেখা ছিল,একটি নতুন হাইড্রা মাতৃ হাইড্রা থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীন জীবনযাপন করতে প্রায় তিন সপ্তাহ সময় নেয়, সেখানে সর্বশেষ সংস্করণে বলা হচ্ছে এখন লাগে মাত্র চার থেকে সাত দিন। পুরুষের ইউরেথ্রার দৈর্ঘ্যও যেন বইয়ের সংস্করণ বদলানোর সাথে সাথে বদলে যাচ্ছে। কোনো এক সংস্করণে তা ছিল ১৮ থেকে ১৯ সেন্টিমিটার, আর নতুন সংস্করণে তা নাকি বেড়ে হয়েছে ১৮ থেকে ২২ সেন্টিমিটার। আবার শিশু জন্মের সময় অস্থির সংখ্যা নিয়েও মত পাল্টেছে বই: একসময় পড়ানো হতো শিশু জন্মায় ৩০০টি অস্থি নিয়ে, এখন বলা হচ্ছে ২৭০টি। প্রশ্ন জাগে, হাইড্রার জীবনচক্র কি প্রতি বছর পাল্টে যাচ্ছে, নাকি শিশুর দেহে হাড়ের সংখ্যা হঠাৎ করেই কমে গেছে? নাকি এগুলো কেবল বই লেখার অসতর্কতা আর অনিয়মিত যাচাই-বাছাইয়ের ফল?নাকি পাঠ্যবইয়ের ঘন ঘন সংস্করণ কেবল নতুন বই বিক্রির কৌশল?
শিক্ষার্থীর কাছে বিজ্ঞান হওয়া উচিত স্থির ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞান। কিন্তু বইয়ের পাতায় যদি বারবার তথ্য উল্টে যায়, তাহলে তারা কাকে বিশ্বাস করবে? এক বছর পড়ে শেখা তথ্য পরের বছরই বাতিল হয়ে যাচ্ছে, অথচ বিজ্ঞানের আসল সত্য তো এমন নয়। এর প্রভাব শুধু মানসিক বিভ্রান্তি নয়, অর্থনৈতিক চাপও বটে। অভিভাবকরা প্রতিবছর নতুন বই কিনতে বাধ্য হচ্ছেন, শিক্ষকেরা আগের বছরের পাঠদানের অভ্যাস গুছিয়ে উঠতেই আবার নতুন করে পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চাপে পড়ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় কোন তথ্য সঠিক ধরা হবে, পুরনোটা, নাকি নতুনটা এই দোলাচলও শিক্ষার্থীর জন্য অযথা এক অস্থিরতা তৈরি করছে।
বইয়ের এহেন ঘন ঘন পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছে বাণিজ্যিক কোচিং সেন্টারগুলো। কোচিং সেন্টারগুলোর ভূমিকা এই প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তারা এমসিকিউ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করার সময় আগের সংস্করণের তথ্য যেমন রাখছে, একই প্রশ্নে আবার নতুন সংস্করণের তথ্যমূলক রেশিওও যুক্ত করছে। ফলে একটি প্রশ্নের জন্য শিক্ষার্থীকে একসাথে দুই সংস্করণের উত্তর মুখস্থ করতে হচ্ছে। এতে কোচিং সেন্টারের ব্যবসা আরও বিস্তৃত হচ্ছে, কারণ তারা শিক্ষার্থীদের বোঝাচ্ছে, “আপডেটেড তথ্য ছাড়া পরীক্ষায় সফল হওয়া সম্ভব নয়।” এইভাবে বইয়ের ঘন ঘন পরিবর্তন আর কোচিং সেন্টারের ব্যবসায়িক স্বার্থ যেন পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে।
অথচ যাদের জন্য এই সমস্ত আয়োজন, সেই শিক্ষার্থীরা প্রকৃতপক্ষে কতটা উপকৃত হচ্ছে, সে প্রশ্নের উত্তর অমীমাংসিতই থেকে যায়। তাদের কেবল বিভ্রান্তি, আর্থিক চাপ আর অতিরিক্ত মানসিক দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হচ্ছে। অথচ এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে নীতিনির্ধারকরা কি কখনও ভেবেছেন? শিক্ষার মূল লক্ষ্য কি জ্ঞানের স্থায়িত্বশীলতা, নাকি বারবার পরিবর্তনের নামে এক প্রকার ব্যবসায়িক চক্রকে টিকিয়ে রাখা? যদি শিক্ষার জায়গাটা সত্যিই শিক্ষার্থীর কল্যাণের জন্য হয়, তবে এই অনিয়মিত পরিবর্তন আর এর সঙ্গে যুক্ত বাণিজ্যিকীকরণের প্রবণতা নিয়ে পুনর্বিবেচনা করা এখন জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা যখন জ্ঞানের চেয়ে ব্যবসার জায়গায় পরিণত হয়, তখন সেখানে বিজ্ঞানের আসল মহিমা থাকে না, থেকে যায় কেবল বিভ্রান্তি আর চাপ।
বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের জায়গায় ফিরিয়ে আনা জরুরি। বই পরিবর্তন অবশ্যই হতে পারে, তবে তা হতে হবে সুপরিকল্পিত, দীর্ঘমেয়াদি এবং যথাযথ যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে। বিজ্ঞানের মৌলিক সত্যগুলোকে বারবার পাল্টে দিয়ে পাঠ্যবইকে পরীক্ষার খাতায় পরিণত করার প্রবণতা বন্ধ না হলে, শিক্ষার্থী শিখবে না জ্ঞান, বরং শিখবে কেবল অনিশ্চয়তা।
মো. ইফতেখার হোসেন
চিকিৎসা শিক্ষার্থী, কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ |





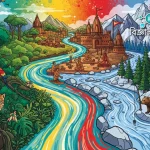
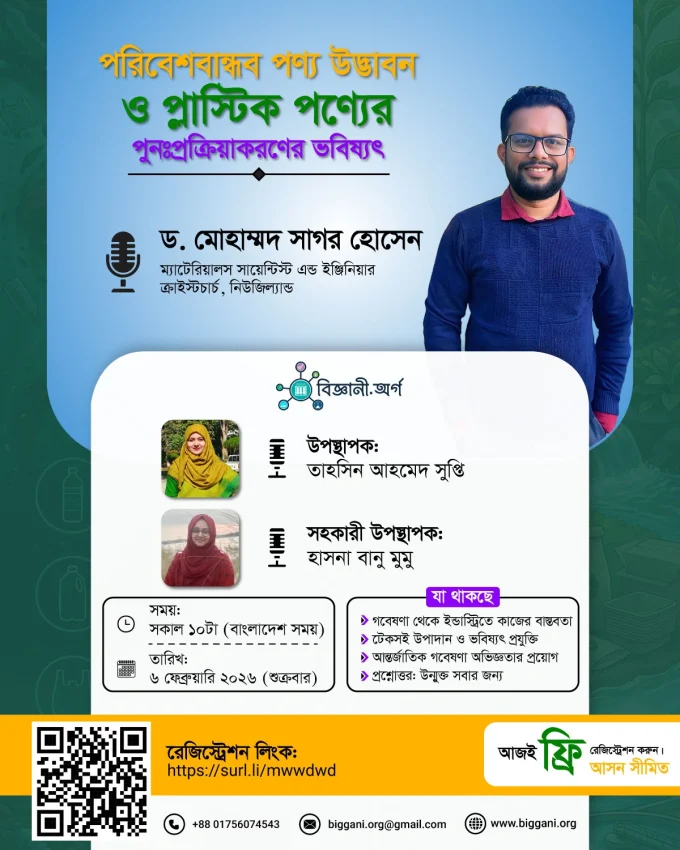




Leave a comment