প্রতিটি শিল্পবিপ্লবের জন্ম হয়েছে প্রযুক্তির নতুন দিগন্ত উন্মোচনের মধ্য দিয়ে। বাষ্পীয় ইঞ্জিন একসময় বদলে দিয়েছিল উৎপাদনের ধারা, বৈদ্যুতিক শক্তি খুলে দিয়েছিল উৎপাদনশীলতার নতুন দ্বার। আজ আমরা এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স ও স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি একত্রে তৈরি করছে শিল্পবিপ্লব ৪.০ ও ৫.০-র ভিত্তি। এই পরিবর্তনের ঢেউ কেবল শিল্পায়নের গতি বাড়াবে না, বরং অর্থনৈতিক কাঠামো, কর্মসংস্থান ও জাতীয় প্রতিযোগিতার সংজ্ঞাকেও পুনর্লিখন করবে। আর সেই স্বপ্নের রূপরেখা আঁকার জন্যই ২০২৫ সালের ১৬ জুলাই ঢাকায় অনুষ্ঠিত হলো BEAR Summit ও National Semiconductor Symposium—যেখানে “Robotics for Resilience, Labor, and Industry Revolution 4.0 & 5.0” শীর্ষক এক উচ্চপর্যায়ের প্যানেল আলোচনায় মিলিত হয়েছিলেন দেশের শীর্ষ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা।
প্যানেলে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ ও নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির অভিজ্ঞ শিক্ষক ও গবেষকরা। আলোচনাটি সঞ্চালনা করেন ড. শাহনেওয়াজ সিদ্দিকী—যিনি রোবটিক্স গবেষণা ও শিল্পে এক উদীয়মান নেতৃত্বের নাম। তাঁদের বক্তব্য শুধু নীতিগত পর্যালোচনায় সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তারা বিশ্লেষণ করেছেন বাস্তব সমস্যার মূলে পৌঁছে, সেই সমস্যার সমাধানে কী ধরনের নীতি, উদ্যোগ ও শিল্প-গবেষণা সমন্বয় প্রয়োজন হতে পারে।
প্রথম ও সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উঠে এসেছে রোবটিক্স কম্পোনেন্ট আমদানির জটিলতা ও উচ্চ খরচ। আন্তর্জাতিক মানের সেন্সর, অ্যাকচুয়েটর কিংবা এমবেডেড সিস্টেমের জন্য ২-৩ গুণ শুল্ক গুণতে হয়, যা তরুণ উদ্ভাবক ও স্টার্টআপদের জন্য প্রায়ই অসহনীয় হয়ে দাঁড়ায়। দেশে উচ্চপ্রযুক্তি যন্ত্রাংশ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারিং জনবল এখনও পর্যাপ্ত নয়। ফলে অনেক উদ্যোগ প্রোটোটাইপের সীমানা পেরোতে পারে না—যা শিল্পায়নের জন্য এক মারাত্মক বাধা।
এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরেকটি পুরোনো সমস্যা—বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পখাতের দুর্বল সংযোগ। গবেষণা প্রায়শই ল্যাবরেটরির দেয়াল ছাড়িয়ে বাজারে পৌঁছায় না, আর শিল্পখাতের প্রয়োজনীয়তাও গবেষণার পরিসরে তেমনভাবে প্রবেশ করে না। এই বিচ্ছিন্নতা বাংলাদেশের রোবটিক্স খাতকে সম্ভাবনাময় হলেও অসম্পূর্ণ রেখেছে। সরকারের নীতি ও বেসরকারি বিনিয়োগের ঘাটতি এ বাস্তবতাকে আরও কঠিন করে তুলেছে।
তবে প্যানেলের আলোচনায় কেবল সমস্যাই নয়, সমাধানের রূপরেখাও উঠে এসেছে। প্রস্তাবিত হয়েছে একটি জাতীয় কৌশলগত টাস্কফোর্স—যা গবেষণা, ডিজাইন, ফ্যাব্রিকেশন, সফটওয়্যার উন্নয়ন ও অ্যাসেম্বলির প্রতিটি ধাপে আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। এই টাস্কফোর্স দক্ষ জনবল তৈরির পাশাপাশি গবেষণাকে বাস্তব প্রয়োগে রূপ দিতে পথনির্দেশ দেবে।
এছাড়াও প্রস্তাব করা হয়েছে একটি অ্যাডভান্সড ম্যানুফ্যাকচারিং হাব স্থাপনের, যা দেশে সেন্সর ও এমবেডেড সিস্টেমের মতো গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট উৎপাদন করতে পারবে। শতভাগ আত্মনির্ভরতা হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে সম্ভব নয়, কিন্তু কিছু মূল কম্পোনেন্টের দেশীয় উৎপাদন আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে “Made in Bangladesh” রোবটের স্বপ্নকে বাস্তবতার দিকে নিয়ে যাবে। যদি নীতিমালায় অন্তত ৫০ শতাংশ দেশীয় অবদান বাধ্যতামূলক করা যায়, তবে তা হবে জাতীয় গর্ব ও বৈশ্বিক স্বীকৃতির এক শক্তিশালী বার্তা।
এই শিল্পবিপ্লবের জন্য প্রয়োজন শুধু প্রযুক্তি নয়, বরং মানুষের দক্ষতা। প্যানেল প্রস্তাব করেছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ডক্টরাল লেভেলের প্রফেশনাল ডিগ্রি প্রদানের সুযোগ দিলে গবেষণার গভীরতা ও মান দুইই বাড়বে। এর সঙ্গে উন্নত গবেষণাগার স্থাপন ও শিল্পাঞ্চলে হাতে-কলমে প্রোটোটাইপ তৈরির সুযোগ নিশ্চিত করাও জরুরি। এই সমন্বিত ইকোসিস্টেমে গবেষণা, শিক্ষা, শিল্প ও ব্যবসা একে অপরকে শক্তি যোগাবে।
তবে দক্ষ জনবল তৈরি করাই যথেষ্ট নয়; তাদের ধরে রাখার পথও তৈরি করতে হবে। আকর্ষণীয় ক্যারিয়ার সুযোগ ও স্থিতিশীল কর্মপরিবেশ না থাকলে তরুণ প্রতিভা বিদেশে চলে যাবে—যা শুধু রোবটিক্স নয়, গোটা প্রযুক্তিখাতের জন্য ক্ষতিকর। একইসঙ্গে রোবটিক্স কম্পোনেন্ট আমদানিতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমাতে হবে, যাতে ছোট উদ্যোগ ও স্টার্টআপগুলো সহজে প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে পারে।
প্যানেল কিছু অগ্রাধিকারমূলক খাতও চিহ্নিত করেছে, যেখানে দ্রুত সাফল্য সম্ভব। যেমন, স্মার্ট ফ্যাক্টরির জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট, যা গার্মেন্টস ও ইলেকট্রনিক্স খাতের উৎপাদনশীলতা বাড়াবে; AI-সমৃদ্ধ কৃষি ড্রোন, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফসলের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ ও সার-বীজ প্রয়োগ করবে; দুর্যোগ মোকাবেলায় উদ্ধার ও ত্রাণ সরবরাহের রোবট; এবং স্বাস্থ্যসেবায় স্মার্ট ওষুধ সরবরাহ ও বৃদ্ধসেবায় সহায়ক রোবট। পরিবেশ রক্ষায়ও রোবটিক্সের ব্যবহার কল্পনাযোগ্য—নদী পরিষ্কারকারী আন্ডারওয়াটার রোবট কিংবা বায়ু বিশ্লেষণকারী UAV হতে পারে তার উদাহরণ।
সবশেষে, আলোচনাটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—প্রযুক্তি ও শিল্পবিপ্লব কেবল যন্ত্র বা কোডের সমষ্টি নয়, বরং তা মানুষের সিদ্ধান্ত, সাহস ও সহযোগিতার ফল। সরকারের দূরদৃষ্টি, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-সংস্কৃতি, শিল্পখাতের বিনিয়োগ এবং তরুণ প্রজন্মের উদ্ভাবনী শক্তি—এই চারটি স্তম্ভ একসঙ্গে দাঁড়াতে পারলেই বাংলাদেশ রোবটিক্সে দক্ষিণ এশিয়ার নেতৃত্ব নিতে পারবে। পথ সহজ নয়, কিন্তু সম্ভাবনা অসীম। এবং ঠিক এইখানেই আমাদের ভবিষ্যতের কাহিনি লেখা শুরু হতে পারে—একটি উদ্ভাবন-নির্ভর, আত্মনির্ভর বাংলাদেশের কাহিনি।







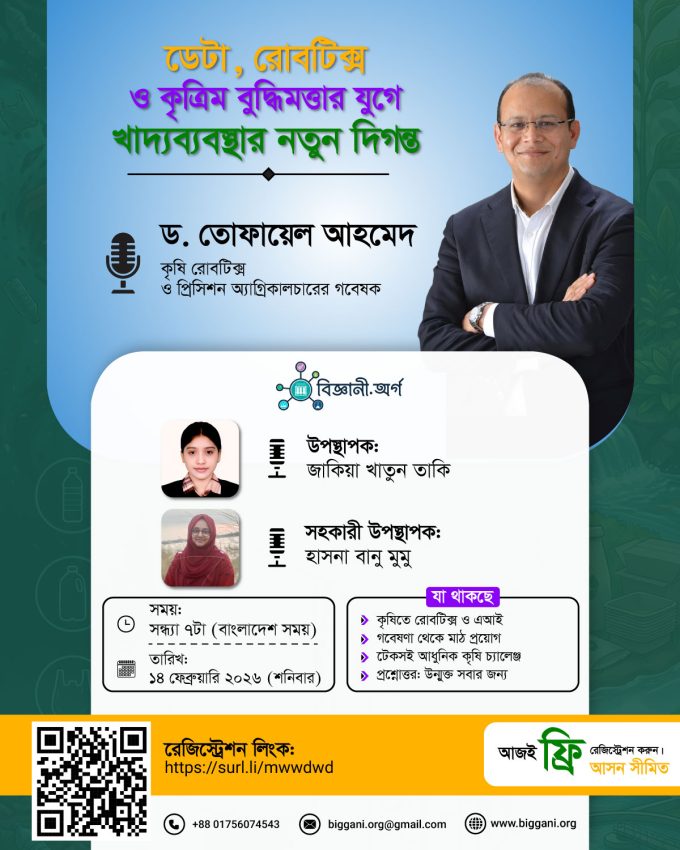

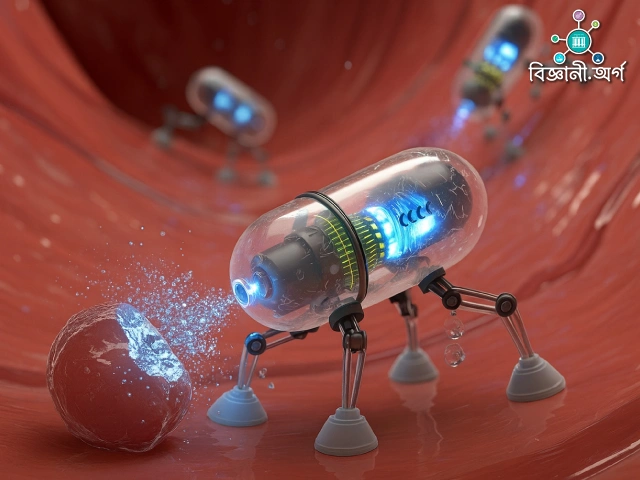

Leave a comment