ওপেনএআই–এর জিপিটি–৫ প্রকাশের পর মানবসভ্যতা যেন আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল সেই দিনের দিকে—যেদিন আমরা এমন এক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সামনে দাঁড়াব, যা আমাদের প্রত্যেককে চিন্তা, পরিকল্পনা, বিশ্লেষণ ও সৃষ্টিশীলতায় বহু দূর পেছনে ফেলে দেবে। সেই দিন যত কাছে আসছে, আমার মনে উদ্বেগ তত বাড়ছে। অথচ এই উদ্বেগের কারণ হয়তো আপনার প্রত্যাশিত কারণ নয়।
আপনি যদি কারও কাছে জানতে চান, এআই নিয়ে তার ভয় কী, বেশিরভাগ মানুষই বলবেন—চাকরির বাজারে ব্যাপক বিপর্যয়, ‘ডিপফেক’ প্রযুক্তির বিভ্রম সৃষ্টি, কিংবা হাতে গোনা কিছু বড় কোম্পানির হাতে বিপুল ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে, খুব কম মানুষই ভেবে দেখেছেন—যে দিন কৃত্রিম সুপারইন্টেলিজেন্স সবার হাতের নাগালে চলে আসবে, সেই পরদিন তাদের জীবন কেমন হবে।
কৃত্রিম সুপারইন্টেলিজেন্স বা এএসআই বলতে আমরা বুঝি এমন এক সিস্টেম, যা মানুষকে প্রায় সবক্ষেত্রেই চিন্তাশক্তিতে ছাড়িয়ে যাবে—যেমন জটিল পরিকল্পনা তৈরি, যৌক্তিক বিশ্লেষণ, সমস্যার সমাধান, কৌশলগত ভাবনা কিংবা সৃষ্টিশীল উদ্ভাবন। এমন এক সিস্টেম সেকেন্ডের ভগ্নাংশে এমন সমস্যার সমাধান করবে, যা একজন প্রতিভাবান বিশেষজ্ঞের হয়তো মাস বা বছরের পর বছর সময় লাগত। ভয়ের কারণ এখানে ‘ডুমসডে’ দৃশ্যপট নয়; বরং ভয়ের বিষয় হলো—যদি এই বুদ্ধিমত্তা আমাদের জন্য সহায়ক ও সদয় হয়, তবুও তা আমাদের মানুষের মৌলিক সত্ত্বাকে নাড়িয়ে দিতে পারে। কারণ তখন আমরা সবাই জানব, আমাদের নিজের মস্তিষ্কের ভেতরের ক্ষমতার চেয়ে মোবাইল ডিভাইসের এআই সহকারী অনেক বেশি দ্রুত, বুদ্ধিমান ও সৃষ্টিশীল।
তখন প্রশ্ন দাঁড়াবে—আমরা কি প্রতিটি ছোট-বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এআই–এর কাছে পরামর্শ চাইতে শুরু করব? নাকি আরও ভয়ংকরভাবে, আমরা আমাদের নিজের চিন্তাভাবনার ওপর ভরসা না করে এআই–এর ওপর বেশি নির্ভর করব? বাস্তবে, আমাদের এআই–এর সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া এখনো মূলত প্রশ্ন–উত্তরের কাঠামোয় সীমাবদ্ধ, ঠিক যেমন ‘স্টার ট্রেক’-এর ক্যাপ্টেন কার্ক ১৯৬৬ সালে করতেন। কিন্তু সেই যুগ শেষ হতে চলেছে। খুব শিগগিরই এআই এমনভাবে শরীরে ধারণযোগ্য ডিভাইসে সংহত হবে—যার সঙ্গে থাকবে ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন—যাতে এআই আমাদের দেখা-শোনা সবকিছু বুঝতে পারবে, আর আমাদের না জিজ্ঞেস করেই কানে কানে বলে দেবে কী করতে হবে।
এটাই হলো ‘অগমেন্টেড মেন্টালিটি’র যুগ—যেখানে এআই–সক্ষম চশমা, ইয়ারবাড বা ছোট পেন্ডেন্ট আমাদের প্রতিটি অভিজ্ঞতার সঙ্গে মুহূর্তে মুহূর্তে যুক্ত থাকবে। মেটা, গুগল, স্যামসাং, অ্যাপল—সবাই এখন প্রতিযোগিতায় নেমেছে এই ‘কনটেক্সট–অওয়্যার’ এআই ডিভাইসের বাজার দখল করতে, যা শিগগিরই হাতে ধরা ফোনের জায়গা নেবে।
ভাবুন, আপনি রাস্তায় হাঁটছেন। সামনে আপনার এক সহকর্মী আসছেন, কিন্তু নাম মনে পড়ছে না। আপনার এআই সহকারী সঙ্গে সঙ্গে সেই নাম বলে দিচ্ছে, সঙ্গে জানাচ্ছে—তার স্ত্রীর অস্ত্রোপচারের খবর নিতে ভুলবেন না। সহকর্মী খুশি হলেন, এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আপনার সাম্প্রতিক পদোন্নতি নিয়ে কথা বললেন—সম্ভবত তার নিজের এআই–এর পরামর্শেই। তখন কি আপনি প্রকৃত মানুষটির সঙ্গে কথা বলছেন, নাকি তার কানে ফিসফিস করা এআই এজেন্টের সঙ্গে?
একদিকে মনে হবে যেন এক অদৃশ্য সুপারপাওয়ার আমাদের পকেটে আছে—যা আমাদের স্মৃতিকে অটুট রাখছে, কথোপকথনকে প্রাঞ্জল করছে, মিথ্যা শনাক্ত করছে। অন্যদিকে, হয়তো একসময় আমরা বুঝব—মানবিক মিথস্ক্রিয়ার স্বাভাবিকতা কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষে মানুষে সম্পর্কের মাঝখানে অদৃশ্য এক বুদ্ধিমান মধ্যস্থতাকারী ঢুকে পড়ছে, যা আমাদের সিদ্ধান্ত, প্রতিক্রিয়া, এমনকি আবেগকেও গড়ে দিচ্ছে।
অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, দেহে ধারণযোগ্য এআই সহকারী আমাদের ক্ষমতাবান করবে। কিন্তু সমানভাবে সম্ভব, এগুলো আমাদের আত্মবিশ্বাস কেড়ে নিতে পারে। মানুষের পরিচয়ের মূল গর্ব হলো আমাদের চিন্তাশক্তি—যেটি নিয়ে আমরা হাজার বছরের সভ্যতা গড়েছি। অথচ খুব দ্রুতই আমরা হয়তো নিজের চিন্তাশক্তির ওপর ভরসা না করে এমন এক এআই–এর কাছে মাথা নত করব, যা সবক্ষেত্রেই আমাদের চেয়ে এগিয়ে। তখন প্রশ্ন উঠবে—এটি কি সত্যিই ক্ষমতায়ন, নাকি এমন এক ‘বট–বর্ণনা’ বাস্তবতা, যেখানে আমরা কেবল দর্শক?
আমি এ উদ্বেগ তুলছি একজন প্রযুক্তি উদ্ভাবক হিসেবে—যিনি সারাজীবন মানুষের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রযুক্তি তৈরি করেছেন। অগমেন্টেড রিয়েলিটি থেকে শুরু করে কথোপকথন–ভিত্তিক এজেন্ট, সব ক্ষেত্রেই আমার বিশ্বাস ছিল—প্রযুক্তি মানুষকে আরও দক্ষ করে তুলতে পারে। কিন্তু সুপারইন্টেলিজেন্সের ক্ষেত্রে এক সূক্ষ্ম সীমারেখা রয়েছে—মানবিক ক্ষমতা বাড়ানো আর তা পুরোপুরি প্রতিস্থাপন করার মধ্যে। সেই সীমারেখা আমরা অতিক্রম করব কি না, তা নির্ভর করবে আমরা কতটা সতর্কতার সঙ্গে এই প্রযুক্তিকে সমাজে প্রয়োগ করতে পারি তার ওপর। নইলে আশঙ্কা থেকেই যাবে—একদিন হয়তো আমরা আর নিজের জন্য চিন্তা করব না, বরং চিন্তাগুলো আমাদের হয়ে কেউ আরেকজন, বা বরং ‘কিছু’ করে দেবে।







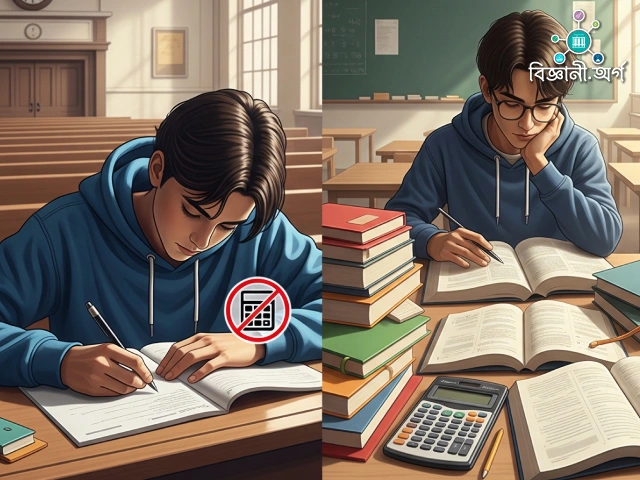

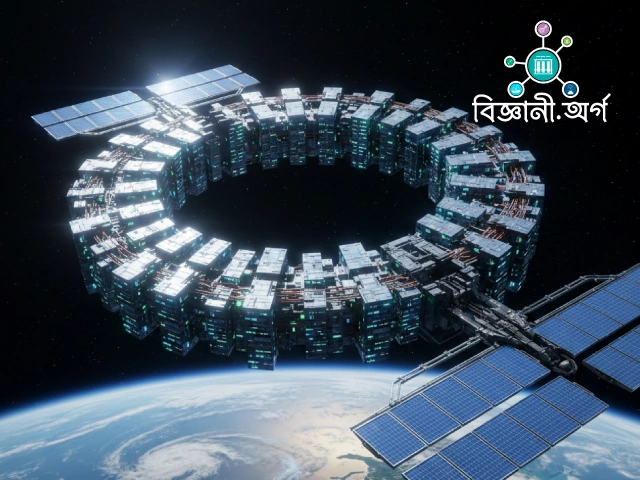
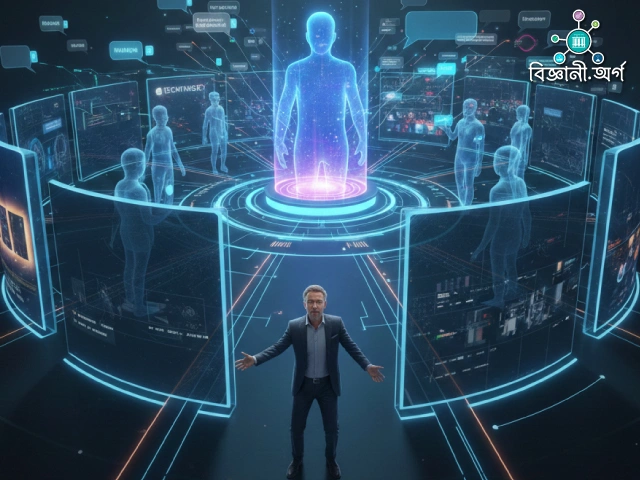
Leave a comment