বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্রজোয়ার-বলয় ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন প্রায় ১০,০০০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের, যার অন্তত ৬০১৭ বর্গকিলোমিটার বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা) জেলায় অবস্থিত। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মুন্সিগঞ্জের সমাহারে গড়ে ওঠা এ বনভূমি জোয়ার-ভাটার সঙ্গে নোনা পানির প্লাবিত, মাটিতে প্রচুর গাদা কাদা বালু আছে এবং বনভূমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৩১.১%) নদী-খাল-বিল নয়নাভিরূপ জলাভূমিতে পরিণত। এছাড়াও এ বনজুড়ে সাদা গেওয়া ও বড় সুন্দরীসহ ৮০০-এরও বেশি প্রজাতির উদ্ভিদ, মাছ, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণী বাস করে। সুন্দরবনের পরিবেশ ও বৈচিত্র্য প্রাকৃতিকভাবে অদ্ভুত: প্রবল জোয়ার-ভাটার ফলে বনভূমির জমি-আকৃতি বছর ঘুরে পরিবর্তিত হয়, বিভিন্ন দ্বীপ-চার ভেসে আসে বা বিলীন হয়। এর আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বিবেচনায় সুন্দরবন ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সুন্দরবনের পরিবেশঃ
ক্লাইমেট চেঞ্জ সুন্দরবনের পরিবেশকে মুঠো আকারে সংকুচিত করছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়লে সুন্দরবনের প্রান্তবর্তী ভূমি ক্রমশ বিলীন হচ্ছে; ১৯৬৪ সাল থেকে এ বনাঞ্চলের প্রায় ২১০ বর্গকিলোমিটার নতুন ভূমি সমুদ্র জলে বিলীনে গেছে। পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা ও ঘনত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে – ২০০৭ সালের সিডরের ধ্বংসে সুন্দরবনের প্রায় ৪০% বনজলাভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, আর ২০০৯ সালের আয়লা জলোচ্ছ্বাসে শত শত হাজার মানুষ প্রভাবিত হয়েছিল। ঝড়ের তীব্রতা ও ঘনতা বাড়ায় মাটি ও গাছপালির ক্ষয়ও বেড়ে যাচ্ছে। এসবের সঙ্গে বিদ্যমান সমুদ্রজল বৃদ্ধি ও মিঠাপানির সরবরাহ কমার প্রভাবে সুন্দরবনে ক্রমশ লবণাক্ততা ছড়িয়ে পড়ছে। নোনাজলের চাপে সুনামি-ছড়া জোয়ারবিলের মিঠা পানির অভাব দেখা দিলে সুন্দরবনের কিছু অংশের বনে গাছপালা ছেঁটে পড়ে। এমন পরিবর্তন বনজগতের জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যকে হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে। যেমন এক সমীক্ষা অবহিত করে যে “সমুদ্রপৃষ্ঠের ক্রমবর্ধমান উচ্চতা, প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও মৃত্তিকা ক্ষয় সুন্দরবনের ভূ–আকৃতি পরিবর্তন করে দিচ্ছে”। এই পরিবর্তনগুলো বনাঞ্চলের জলবায়ু ও আবহাওয়াকেও অস্থিতিশীল করছে – বিলুপ্ত দ্বীপ আর বর্ধিত লবণাক্ততার প্রতিক্রিয়ায় বনের আবহাওয়া ও মাটি ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে।
বাঘের বাসস্থান ও খাদ্য সংকটঃ
এই বদলে যাওয়া প্রকৃতিক প্রেক্ষাপটে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বাসস্থান সংকীর্ণ হচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অগ্রণী বনভূমি হলেও সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের টিকে থাকা একটি বড় অংশ এখন জলাবদ্ধ। গবেষণায় দেখা গেছে, “২০৭০ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সম্মিলিত প্রভাবে সুন্দরবনের বাঘের আর কোনো উপযুক্ত আবাসস্থল থাকবে না”। মানে মাত্র ৫০ বছরের মধ্যে সুন্দরবনের বাংলাদেশের অংশের সব বাঘ বাস্তুতন্ত্র বিলুপ্তির পথে চলে যাবে। একই গবেষণা সতর্ক করে দেয়, এখনও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া না হলে ২০৫০ সালের মধ্যেই বাঘ আর শুধুমাত্র ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কম লবণাক্ত বনাঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা মাত্র ৮৩–১৩০ এর মধ্যে (ভারতের অংশে প্রায় ৮৬টি), যা বনভূমি সংকোচনের হার আর উদ্বেগজনক করে তোলে।
খাদ্যের দিক থেকেও বিপুল চাপ পড়ছে। বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞদের মতে, সুন্দরবনের বাঘের খাদ্যের প্রায় ৭৮% হরিণ শিকার করেই পূরণ হয়। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে লবণাক্ততার মাত্রা বাড়ায় বনভূমির পুকুর-জলাশয়ে মিঠাপানির অভাব দেখা দিয়েছে। এতে শিকারি প্রাণীদের – চিত্রা হরিণ, বন্য শূকর, বানরসহ বনভূমির অন্যান্য উপদ্রুত প্রাণী – সংকটে পড়েছে। বনভূমিতে পানির ঘাটতি ও লবণাক্ততার প্রকোপে হরিণ এবং বন্য শূকরের সংখ্যা কমছে। ফলে বাঘ খাদ্যভিক্ষার পথে, শিকারসংকটে পড়ছে।
বাঘের জনসংখ্যা ও নিরাপত্তাঃ
পরিবেশগত পরিবর্তনের পাশাপাশি বাঘের নিরাপত্তাও জাঁকিয়ে ঘিরে ফেলা রয়েছে। আশার কথা, সরকারের সংরক্ষণ প্রচেষ্টায় সম্প্রতি সুন্দরবনের বাঘ সংখ্যা কিছুটা বাড়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে; ২০১৫ ও ২০১৮ সালের জরিপে যথাক্রমে ১০৬ টি ও ১১৪ টি বাঘ শনাক্ত করা হয়েছিল, আর সর্বশেষ ক্যামেরা-ট্র্যাপ জরিপে এই সংখ্যা ১২৫ ছাড়িয়েছে। তবে দাবিদাওয়া কমার প্রথম শর্ত হচ্ছে প্রাণনাশ না হওয়া – সুন্দরবনের বাঘদের ভর্ৎসনার প্রধান শত্রু এখনো অবৈধ শিকারি ও পরিবেশ ভাঙচুর।
সংকট প্রতিরোধে বন বিভাগ ইতিমধ্যে ‘টাইগার রেসপন্স টিম’ নামে ৪৯টি গ্রামে মোট ৩৪০ জন বনবাসী মসজিদের তত্ত্বাবধানে গঠন করেছে। এই উদ্যোগে গত পাঁচ বছরে সুন্দরবনে কোনো মানুষ-বাঘ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে নাই। তাছাড়া সরকারের উদ্যোগে সুন্দরবনের মোট আবাসাঞ্চলের ৫২% অংশ (প্রায় ৩০০০ বর্গকিমি) সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, যা আগের ২৩%-এর তুলনায় ব্যাপক বৃদ্ধি। এই রক্ষিত এলাকায় বাঘ অধিকারহীন থেকে মুক্ত আর প্রতি বিচরণ নিরাপদ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।
বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলছেন, বাঘের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শুধু রাজনৈতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ যথেষ্ট নয় – বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় সচেতনতা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশীদারীত্ব জরুরি। বন্যপ্রাণী গবেষক পাভেল পার্থ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, “বাস্তুসংস্থান রক্ষা করা ছাড়া বাঘ সংরক্ষণ সম্ভব নয়; বাঘ, হরিণ, বানরসহ বিভিন্ন প্রাণীর অস্তিত্ব একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত”। অর্থাৎ বনভূমির প্রতিটি স্তর রক্ষা করা হলে বাঘের জন্য খাবার ও আশ্রয় দুটোই নিশ্চিত থাকবে।
সাম্প্রতিক গবেষণা ও পরিসংখ্যানঃ
সুন্দরবনের বাঘ নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণা ও জরিপগুলোতে আশাব্যঞ্জক ও দুস্প্রাপ্য উভয় চিত্র ফুটে উঠেছে। ২০২৩-২৪ সালে করা সর্বশেষ সমীক্ষায় (ক্যামেরা-ট্র্যাপ পদ্ধতিতে) বাংলাদেশের সুন্দরবনে প্রাপ্তবয়স্ক বাঘের সংখ্যা কমপক্ষে ১২৫ হিসেবে ধরা হয়েছে, যা ২০১৮ সালের তুলনায় প্রায় ১০% বেশি। (আগের দুই জরিপে যথাক্রমে ২০১৫ ও ২০১৮ সালে শনাক্ত করা হয়েছিল ১০৬ ও ১১৪ বাঘ) ।এতে দেখা গেছে সুন্দরবনে বাঘ জনসংখ্যা ধীরে হলেও বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে যে, ব্যাঙাল টাইগার গ্লোবালি এখনও বিপন্ন প্রজাতি; এশিয়ার ১৩টি দেশ মিলিয়ে এখন বন্য বাঘের সংখ্যা প্রায় ৫,৫৭৪টি।
উপমহাদেশে গবেষকেরা আশা করছেন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নেওয়া পদক্ষেপ ও বাড়তি নজরদারির মাধ্যমে সুন্দরবনের বাঘদের টিকে থাকার সুযোগ বাড়ছে। যেমন অন্য এক সমীক্ষা দেখিয়েছে সুন্দরবনের হরিণ-শূকর-বানর প্রভৃতি মুখ্য খাদ্যপ্রাণীর সংখ্যা সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। স্পটেড চিত্রা হরিণের সংখ্যা ৮০-৮৫ হাজার থেকে প্রায় ১,৪১,৩৫৭-এ উন্নীত, বন্য শূকের সংখ্যাও প্রায় ২৮০০০ থেকে ৪৫,১১০-এ পৌঁছেছে। এই prey-population বৃদ্ধিই পরোক্ষে বাঘের পুণর্জীবনে সহায়ক বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।
উদ্যোগ ও সুপারিশঃ
পরিবেশবিদ ও সংরক্ষণবাদীরা জোর দিয়ে বলছেন, সুন্দরবনের বাঘ বেঁচে থাকার লড়াইয়ে শুধু বন সংরক্ষণই নয়; ব্যাপক নীতিগত উদ্যোগ প্রয়োজন। বাংলাদেশের সরকার ইতিমধ্যে অগ্রণী পদক্ষেপ নিয়েছে: গত জুলাইয় বিএশবলে ঘোষণা করা হয়েছে আগামী পাঁচ বছরে সুন্দরবনে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা ২০% বাড়িয়ে ১৪৫টি করার লক্ষ্য। এর অংশ হিসেবে ৫০ শতাংশেরও বেশি বনাঞ্চল (৫১%) সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বাঘের প্রজননকালে (তিন মাস) বনভূমিতে মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধের নিয়ম চালু রাখা হয়েছে। বনরক্ষা অভিযান ও টহলদারি তৎপরতা যেমন বাড়ানো হয়েছে, তেমনি জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণমূলক উদ্যোগও জোরদার হচ্ছে।
সংরক্ষণী সংস্থাগুলোও বিভিন্ন সুপারিশ করছে। উদাহরণস্বরূপ, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশবিদরা বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের ম্যানগ্রোভ জোনটিকে একটি অবিচ্ছিন্ন করিডর হিসেবে বিবেচনা করে এর পারস্পরিক সংরক্ষণের পরামর্শ দিচ্ছেন। জলবায়ু ঝুঁকি কমাতে বনাঞ্চল পুনঃবৃদ্ধি ও নিষিদ্ধ চাষাবাদ প্রতিরোধে নাগরিক অংশগ্রহণ বাড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বাঘের জন্য খাদ্যাধার বাড়ানোর জন্য বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি বন বিভাগের গবেষকরা এবং পরিবেশকর্মীরা জনসচেতনতা ও আইন প্রয়োগকে ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানাচ্ছেন; যেমন অধ্যাপক আব্দুল্লাহ হারুন চৌধুরী বলেছেন, বাঘের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাচার প্রতিরোধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আরো কঠোর হতে হবে।
সর্বোপরি বাঘ রক্ষায় পরিবেশবিদরা ঐক্যবদ্ধভাবে বলছেন, সুন্দরবনের বিস্ময়কর বাস্তুতন্ত্র বাঁচলে বাঘও বাঁচবে। তারা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, সুন্দরবনের বাঘ শুধু বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক নয়, এটি বিশ্ববাসীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ; তাই এর রক্ষায় গবেষণাভিত্তিক নির্ভরযোগ্য উদ্যোগ এবং আন্তঃবর্ণালী সহযোগিতা অত্যাবশ্যক।
সূত্রঃ উপরোক্ত তথ্য বিভিন্ন গবেষণা ও প্রতিবেদন থেকে সংগৃহীত। উৎসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: সুন্দরবনের পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য ও পরিসংখ্যান, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে আন্তর্জাতিক গবেষণা, সাম্প্রতিক বাঘ-জনগণনা ও খাদ্যজীবন সংক্রান্ত জরিপ এবং পরিবেশসংরক্ষণী লেখনী ও খবরে প্রকাশিত উদ্যোগ ও সুপারিশ।
মোঃ ফাহাদ হুসাইন
শিক্ষার্থী, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
শহীদ বুলবুল সরকারি কলেজ, পাবনা।
(অধিভুক্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ)










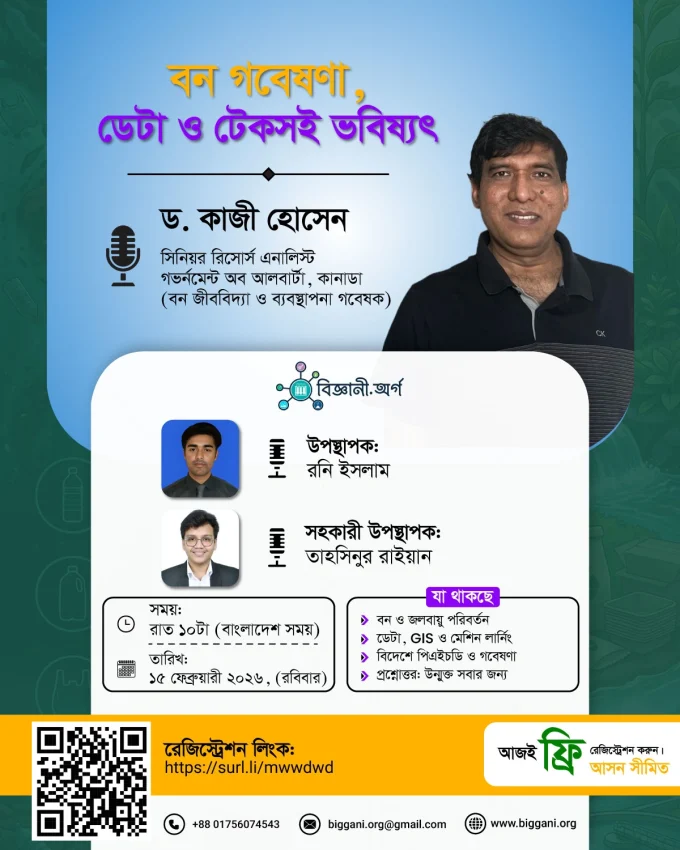
Leave a comment