ড. মশিউর রহমান
গবেষণা মানেই ল্যাবরেটরির টেস্ট টিউব কিংবা কম্পিউটার স্ক্রিনে কোডের লাইন নয়; গবেষণা মানেই সমাজ, দেশ ও বিশ্বকে একটি নতুন আলোয় দেখা। সম্প্রতি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং জাপানের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উপদেষ্টা ড. মিচিনোরি কান্নো এক আলোচনায় বললেন, গবেষককে শুধু বিজ্ঞানী হিসেবে নয়, বরং কূটনীতিক হিসেবেও ভাবা দরকার। কেননা, বিজ্ঞানের ভাষাই হতে পারে দেশ ও সংস্কৃতির ভেতরকার সেতুবন্ধন।
গবেষণার জগতে কূটনীতি বলতে আমরা কী বুঝি? সাধারণত কূটনীতি মানে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য, নিরাপত্তা বা বাণিজ্যচুক্তি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কূটনীতির বিষয়টি ভিন্নতর। এখানে লক্ষ্য থাকে গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞান ভাগাভাগি করা, নতুন সুযোগ তৈরি করা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে তোলা। গবেষকরা যখন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নেন, নতুন সহযোগিতার খোঁজ করেন বা যৌথ গবেষণা প্রকল্পে যুক্ত হন, তখন তারা কেবল জ্ঞানের অন্বেষণ করছেন না; একই সঙ্গে একটি কূটনৈতিক ভূমিকা পালন করছেন।
ড. কান্নোর মতে, গবেষণায় কূটনৈতিক দক্ষতা শুরু হয় শোনার মাধ্যমে। আমরা প্রায়ই ভাবি যোগাযোগ মানেই কথা বলা, কিন্তু বৈজ্ঞানিক কূটনীতির মূল হলো মনোযোগ দিয়ে শোনা। একজন ক্লিনিক্যাল চিকিৎসক যেমন রোগীর অভিযোগ না শুনে ওষুধ লিখে দিলে সেটা অবিশ্বাস সৃষ্টি করে, গবেষণার ক্ষেত্রেও তাই। আন্তর্জাতিক অংশীদারদের কথায় কান দেওয়া, তাদের প্রয়োজন বোঝা এবং সেখান থেকে নতুন ধারণা সৃষ্টি করা—এটাই সঠিক সূচনা।
তবে কেবল শোনা নয়, যুক্তি দিয়ে বোঝানোর ক্ষমতাও জরুরি। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতিতে আলোচনার ধারা এমন যে, সেখানে বিতর্ক বা ভিন্নমত প্রকাশ স্বাভাবিক বিষয়। আর আমাদের প্রাচ্য সংস্কৃতিতে প্রায়ই “শান্তি” বা “সমঝোতা”কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এই দুই ভুবনের ভিন্নতা গবেষণার যৌথ প্রকল্পে দ্বিধা তৈরি করতে পারে। তাই গবেষকদের শেখা দরকার—কখন যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে হবে, আর কখন সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে কূটনৈতিক ধৈর্য ধরতে হবে।
এই জায়গায় আসে আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন। পাশ্চাত্যে একজন গবেষককে বারবার জিজ্ঞেস করা হয়—“তোমার নতুনত্ব কোথায়?” এই প্রশ্ন ক্লান্তিকর হলেও গবেষককে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। বিপরীতে, এশিয়ার অনেক সমাজে গবেষণার ধারা প্রায়ই প্রবাহিত হয় প্রধান ধারা বা কর্তৃত্বের ছায়ায়, যেখানে ভিন্নমত বা নতুন দৃষ্টিকোণকে জায়গা দেওয়া হয় কম। অথচ প্রকৃত বিজ্ঞানের জন্ম হয় প্রশ্ন করার মধ্য দিয়েই। তাই আত্মপরিচয় ও নতুনত্বের চর্চা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গবেষকের জন্য অত্যন্ত জরুরি।
গবেষণার কূটনীতি মানে কেবল সহযোগিতা নয়, নতুন উদ্ভাবনের জন্মও। একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণায় দেখা গেছে, সর্বাধিক উদ্ধৃত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলোর বড় অংশই এসেছে বিভিন্ন শাখার সমন্বয় থেকে। একক ধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ গবেষণা খুব কম ক্ষেত্রেই বড় প্রভাব ফেলতে পারে। তাই গবেষকদের উচিত ঝুঁকি নিতে শেখা, নতুন জুটির সন্ধান করা, এমনকি ব্যর্থতাকে ভয় না পাওয়া। বৈজ্ঞানিক কূটনীতি গবেষকদের এই সাহস জোগায়—ভিন্ন সংস্কৃতির গবেষককে পাশে বসিয়ে নতুন প্রশ্ন করতে শেখায়।
বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের তরুণ গবেষকদের জন্য এই শিক্ষা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশে পড়াশোনা বা গবেষণা করতে গেলে কেবল ভাষাজ্ঞান নয়, বরং নিজের ভাবনা স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করার ক্ষমতা অপরিহার্য। শুধু ইংরেজিতে সাবলীল হওয়া যথেষ্ট নয়; মাতৃভাষাতেও যদি নিজের অবস্থান, গবেষণার গুরুত্ব বা সমাজের প্রতি দায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে না পারেন, তবে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে নিজেকে তুলে ধরা কঠিন হয়ে যায়।
এখানে কূটনীতির সঙ্গে ব্যক্তিগত উন্নতির যোগও আছে। মাসলোর চাহিদা তত্ত্বের কথা টেনে ড. কান্নো বোঝালেন, মানুষ যখন মৌলিক নিরাপত্তা ও সম্পদে নিশ্চিন্ত হয়, তখনই সে সৃজনশীলতা ও আত্ম-উপলব্ধির দিকে এগোয়। গবেষণাও সেই ধাপেরই অংশ—যেখানে কেবল বেঁচে থাকার জন্য নয়, বরং নতুন কিছু আবিষ্কারের আনন্দে কাজ করা হয়। বৈজ্ঞানিক কূটনীতি গবেষকদের এই আনন্দকে বৈশ্বিক মাত্রায় ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।
সবশেষে একটি প্রশ্ন থেকে যায়—আমাদের গবেষকরা কি প্রস্তুত এই কূটনৈতিক দায়িত্ব নিতে? বাংলাদেশি তরুণরা যখন বিদেশি সম্মেলনে অংশ নেবেন, আন্তর্জাতিক ল্যাবে কাজ করবেন বা যৌথ গবেষণায় যুক্ত হবেন, তখন শুধু তথ্য বিশ্লেষণ নয়, সম্পর্ক তৈরি করাও হবে তাদের দায়িত্ব। কূটনীতিকের মতোই গবেষককে শিখতে হবে কখন প্রশ্ন করতে হবে, কখন উত্তর দিতে হবে, আর কখন চুপ থেকে অন্যের ভাবনাকে জায়গা দিতে হবে।
বিজ্ঞান আজ কেবল জ্ঞানের অন্বেষণ নয়, এটি বিশ্বকে একত্রিত করার ভাষা। গবেষক যদি কূটনীতিকের ভূমিকা নিতে পারেন, তবে তিনি শুধু নিজের গবেষণায় অবদান রাখবেন না, বরং মানবতার অগ্রযাত্রার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠবেন। বিজ্ঞানের কূটনীতি আমাদের শেখায়—অন্যকে জানো, নিজেকে চিনো, আর একসঙ্গে মিলে নতুন ভবিষ্যৎ নির্মাণ করো।
সূত্র: Japan Science and Technology Agency এর একটি অনুষ্ঠানের বক্তব্য থেকে লেখাটি লিখিত


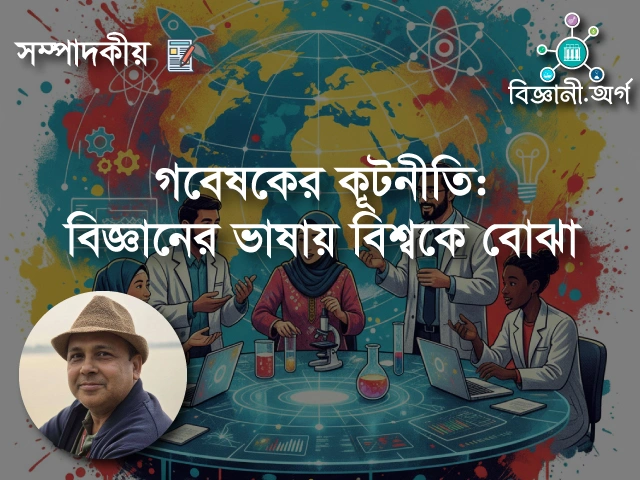



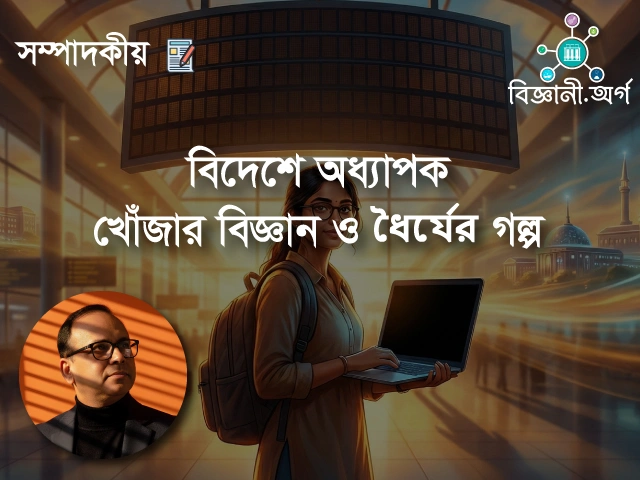
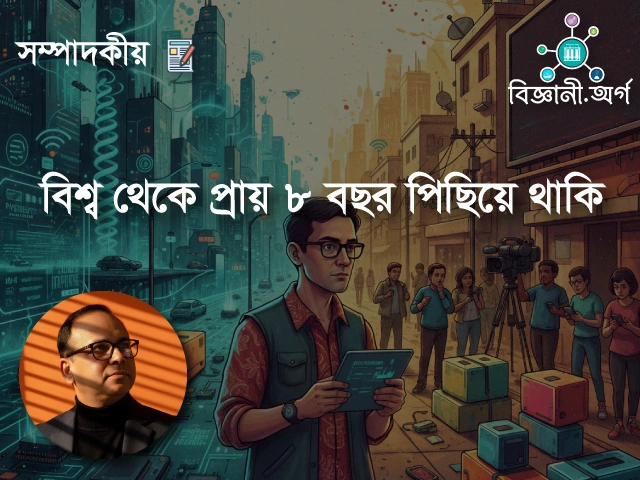
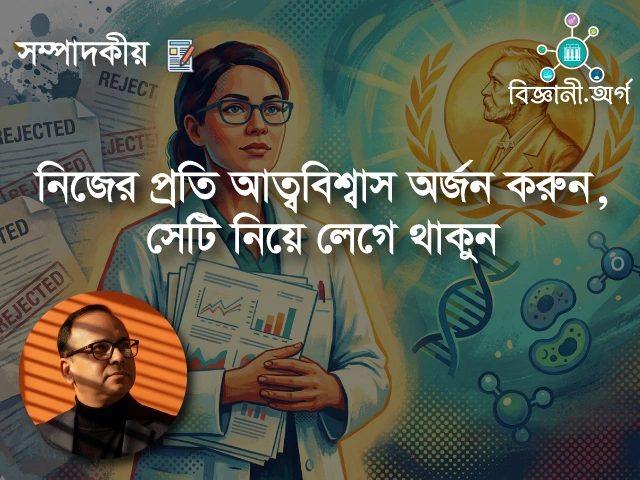

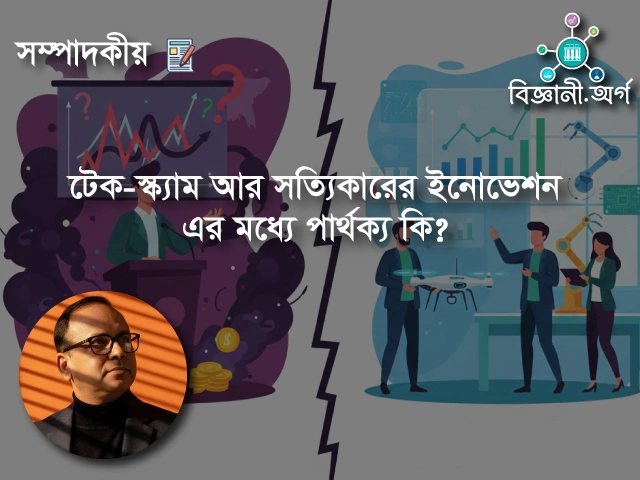
Leave a comment