ড. মশিউর রহমান
গবেষণাগারে দিন-রাত কাটানো একজন তরুণ গবেষক হয়তো ভেবেই দেখেন না, তার কাজ কেবল একাডেমিক জগতে নয়, সমাজেও একদিন গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। আমাদের দেশে যেমন, বিশ্বের অন্যত্রও বিজ্ঞান দীর্ঘদিন ধরে কেবল গবেষণা প্রবন্ধ বা একাডেমিক সাফল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু একবিংশ শতকে এসে এই সীমারেখা ভেঙে গেছে। গবেষকের দায়িত্ব এখন শুধু জ্ঞান তৈরি নয়, সেই জ্ঞানকে সমাজের উপকারে রূপান্তর করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই রূপান্তরের নাম—উদ্যোক্তা বিজ্ঞান বা রিসার্চার-লেড ভেঞ্চার।
জাপানে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক আলোচনায় বিষয়টি বিশেষভাবে উঠে এসেছে। সেখানে বলা হয়, একজন গবেষক যদি সমাজে প্রভাব রাখতে চান, তবে তাকে শুধু ‘সময়-স্রোতে ভাসা’ নয়, বরং নিজের হাতে নতুন স্রোত তৈরি করতে হবে। এর মানে হলো, গবেষণাকে এমনভাবে কাজে লাগানো, যাতে তা সমাজের সমস্যার সমাধান দিতে পারে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নেও অবদান রাখে।
ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা থেকেই অনেক বড় কোম্পানির জন্ম। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭০-এর দশকে স্ট্যানফোর্ডের গবেষণা থেকে জন্ম নিয়েছিল জেনেনটেক, যা আধুনিক বায়োটেকনোলজি শিল্পের পথিকৃৎ। জাপানেও একই ধরনের উদাহরণ আছে—টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি থেকে গড়ে উঠেছিল পেপটিড্রিম, যা আজ বহুজাতিক পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার করছে। এসব উদাহরণ প্রমাণ করে, গবেষক যদি সাহস করেন এবং সঠিক সহযোগিতা পান, তবে তার ল্যাবের আবিষ্কার সীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারে।
তবে এখানে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। বিজ্ঞান জগৎ সত্যের অনুসন্ধানকে উন্মুক্ত রাখে, আর ব্যবসার জগৎ কাজ করে কৌশল, প্রতিযোগিতা এবং মুনাফার হিসাব-নিকাশে। গবেষককে তাই শিখতে হয় কিভাবে তার জ্ঞানকে বাণিজ্যিকীকরণের পথে নিয়ে যাওয়া যায়। এজন্য দরকার হয় মেধাস্বত্ব সুরক্ষা, বিনিয়োগ সংগ্রহ এবং শিল্পখাতের সঙ্গে অংশীদারিত্ব। এটি কেবল একটি ব্যক্তিগত উদ্যোগ নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ সেতুবন্ধন—যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্পখাত ও ভেঞ্চার ক্যাপিটাল একসঙ্গে কাজ করে।
কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন একজন গবেষক উদ্যোক্তা হওয়ার কথা ভাববেন? কারণ উত্তর লুকিয়ে আছে সমাজের অমীমাংসিত সমস্যাগুলিতে। জাপানি এক তরুণ উদ্যোক্তা ইজুমো মিতসুরু একবার বাংলাদেশ সফরে এসে দেখেছিলেন অপুষ্ট শিশুদের অবস্থা। সেখান থেকেই তিনি ভাবেন, কীভাবে ক্ষুদ্র প্রাণী মাইক্রো-অ্যালগি (মিডোরিমুশি বা ইউগ্লিনা) খাদ্য সংকট সমাধানে কাজে লাগানো যায়। পরে তিনি এই ধারণা থেকেই কোম্পানি গড়ে তোলেন এবং আজ সেটি বৈশ্বিক পর্যায়ে খাদ্য প্রযুক্তির সমাধান দিচ্ছে। মূল কথা হলো—একজন গবেষকের আবিষ্কার তখনই অর্থবহ হয়, যখন তা বাস্তব সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করে।
বাংলাদেশের প্রসঙ্গে ভাবা যাক। আমরা একদিকে জলবায়ু পরিবর্তন, অন্যদিকে জনস্বাস্থ্য সংকট কিংবা খাদ্য নিরাপত্তার মতো সমস্যায় জর্জরিত। এগুলো কেবল রাজনৈতিক নীতি বা অর্থনৈতিক কর্মসূচি দিয়ে সমাধান সম্ভব নয়। এখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং তার প্রয়োগ অপরিহার্য। ধরা যাক, কারও ল্যাবে নতুন বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার হলো। এটি যদি শুধু গবেষণাপত্রে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে সমাজের কোনো উপকার হবে না। কিন্তু উদ্যোক্তা হয়ে সেটিকে বাজারে পৌঁছে দিলে, পরিবেশদূষণ কমাতে সরাসরি অবদান রাখা সম্ভব।
গবেষণা থেকে ব্যবসায় যাত্রা সহজ নয়। অর্থের যোগান, সঠিক সহকর্মী খুঁজে পাওয়া, এবং সামাজিক সন্দেহ কাটিয়ে ওঠা—এসব বড় বাধা। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও যখন প্রথম জেনেনটেক গড়ে উঠেছিল, তখন অনেকে সন্দেহ করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা থেকে ব্যবসা টেকসই হতে পারে কি না। কিন্তু সময় প্রমাণ করেছে, সেই সংশয় অমূলক ছিল। আজ জেনেনটেক কোটি মানুষের জীবন বাঁচানো ওষুধ তৈরি করছে।
এই বাস্তবতা আমাদের গবেষকদের জন্যও শিক্ষা। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিদিন নানা আবিষ্কার হচ্ছে, কিন্তু সেগুলো খুব কমই সমাজে পৌঁছায়। কারণ আমরা গবেষণাকে পেশাগত দায়িত্ব মনে করি, সামাজিক দায়িত্ব নয়। অথচ সত্যিকার পরিবর্তন তখনই আসে, যখন গবেষক নিজেকে সমাজের সমস্যার অংশগ্রহণকারী হিসেবে ভাবতে শুরু করেন।
আজ বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহী। তাদের সামনে চ্যালেঞ্জ যেমন আছে, সুযোগও তেমনি বিশাল। যদি আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে উদ্ভাবনী কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারি, গবেষকদের উদ্যোক্তা হওয়ার প্রশিক্ষণ দিতে পারি, তবে হয়তো একদিন আমাদের দেশ থেকেও জন্ম নেবে নতুন ‘বায়োটেক জেনেনটেক’ বা ‘স্পেস এক্সেলস্পেস’। আমাদের সামাজিক সমস্যাই হবে তাদের গবেষণা ও ব্যবসার প্রেরণা।
শেষ পর্যন্ত, গবেষকের কাছে প্রশ্ন একটাই—আপনি কি কেবল সত্য অনুসন্ধানী থাকতে চান, নাকি সেই সত্যকে মানুষের জীবনে কাজে লাগাতে চান? আজকের বিশ্ব সেই গবেষককেই খুঁজছে, যিনি ল্যাবের সীমা ছাড়িয়ে সমাজের সমস্যায় হাত লাগাতে প্রস্তুত। বাংলাদেশে এমন সাহসী গবেষক ও উদ্যোক্তারাই আগামী দিনের অগ্রগতির পথ তৈরি করবেন।


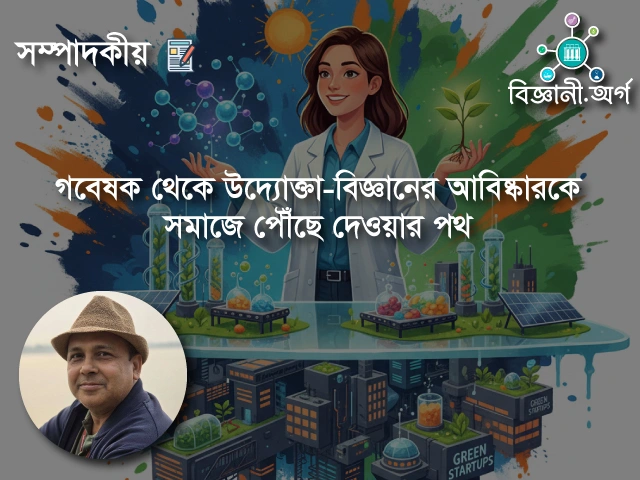

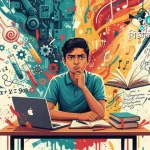

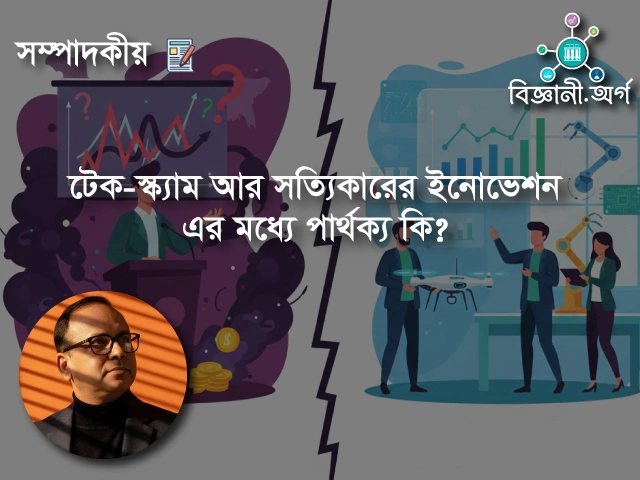

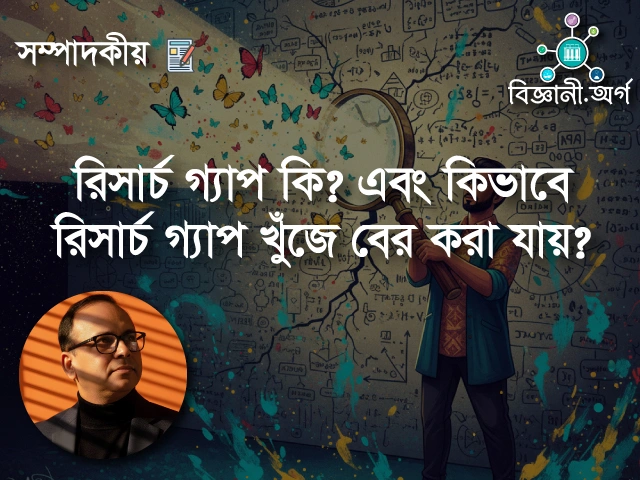
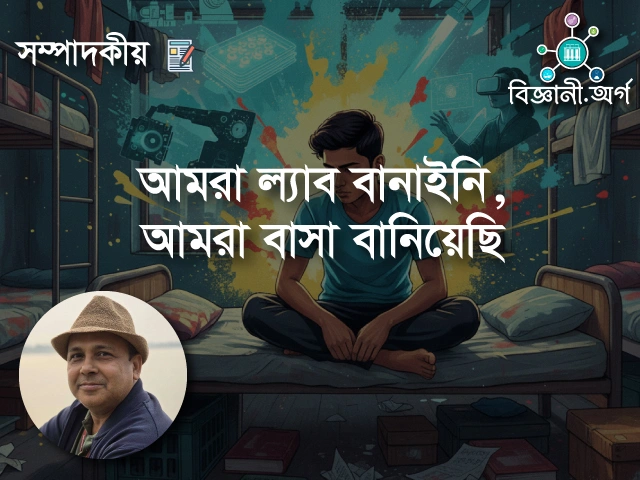
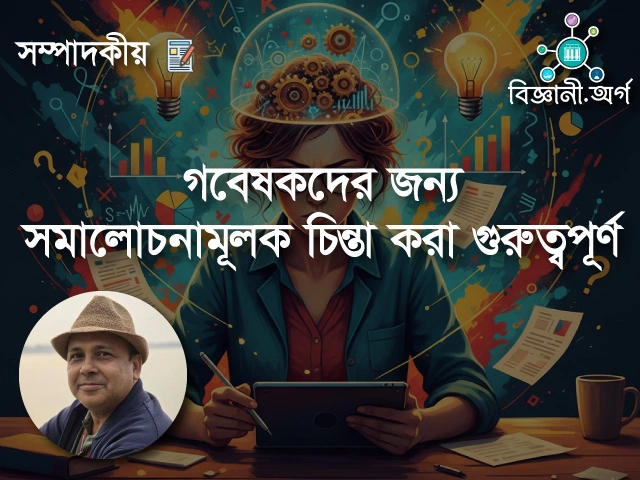
Leave a comment