শুরুতেই গল্পের আসর
একঝাঁক পাখি যেন ঘিরে রেখেছে ছোট্ট রিনির মন। স্কুলের মাঠে দৌড়ে বেড়ানোর বদলে আজ তার সারা বিকেল কেটে যাচ্ছে ডাক্তারের চেম্বারে। স্নায়ুবিক সমস্যা ধরা পড়েছে বলে তার বাবা-মা উদ্বিগ্ন। এক বিশেষজ্ঞের মতে—রিনি নাকি “হালকা মাত্রার অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার”-এ ভুগছে। অথচ তার লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ার বড় কোনো সমস্যা চোখে পড়েনি আগে। এদিকে রিনির মা-বাবা কিছুতেই শান্তি পাচ্ছেন না; তাঁরা ভাবছেন, একবার যদি নির্ভুলভাবে রিনির সমস্যাটির নামকরণ করা যায়—পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সেটি নিশ্চিত করা যায়—তাহলেই বুঝি মেয়ের ভবিষ্যৎ রক্ষা পাবে। কিন্তু ডাক্তারি লেবেল বসানোর পর রিনির নিজের মানসিক চাপ কী পরিমাণ বাড়তে পারে, সেই প্রশ্ন এখনো উন্মুক্ত।
ঠিক এমনই বহু রিনি আমাদের আশেপাশে আছে, যাদের “ডায়াগনোসিস”-এর সঠিকতা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন উঠছে। এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি বিশেষজ্ঞরা দিচ্ছেন একটি গুরুতর হুঁশিয়ারি—ওভারডায়াগনোসিস (অতিরিক্ত রোগনির্ণয়) আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।
একটি ক্রমবর্ধমান সংকট
নিউরোলজিস্ট সুজান ও’সালিভান তাঁর নতুন গ্রন্থ দ্য এজ অব ডায়াগনোসিস-এ চমকে দেওয়া কিছু তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলছেন, আধুনিক স্বাস্থ্যব্যবস্থায় রোগনির্ণয়ের হার বাড়লেও রোগীরা প্রকৃতপক্ষে সুস্থ হচ্ছেন না, বরং তাঁদের মানসিক অস্বস্তি আরও জটিল হয়ে উঠছে। তিনি উল্লেখ করেন, গত দুই দশকে autism (অটিজম) নির্ণয়ের হার যুক্তরাজ্যে ৭৮৭ শতাংশ বেড়েছে। আবার ADHD বা অন্যান্য স্নায়ুবিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার ক্ষেত্রেও একই ধরনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই রোগনির্ণয়ের পরে নির্দিষ্ট কোনো কার্যকর চিকিৎসাপদ্ধতি থাকে না, বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা তাঁর পরিবার অপ্রয়োজনীয় মানসিক চাপে ভোগেন।
সুজান ও’সালিভান WIRED Health-এ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, “ওভারডায়াগনোসিস এমন একটি সমস্যার জন্ম দিচ্ছে, যেখানে মানুষ একের পর এক ‘ডায়াগনোসিস’-এর ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, অথচ সঠিক চিকিৎসা হয়তো এখনো অনুপস্থিত। ফলস্বরূপ রোগের উপসর্গ আরও প্রকট হয়ে উঠতে পারে—এটাই হলো নোসিবো এফেক্ট।”
পাঠকের উদ্বেগ ও অভিজ্ঞতা
মোহাম্মদপুরের বাসিন্দা সুমন আহমেদ (৩৫) জানালেন, “আমার ছোটভাইকে তিন বছর আগে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ADHD বলে ডাক্তাররা সন্দেহ করেন। এরপর একের পর এক টেস্ট, ডাক্তারি লেবেল—কিন্তু বাচ্চাটি যে আসলেই বড় কোনো স্নায়ুবিক সমস্যায় ভুগছে, এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ মিললো না। তবু ADHD-র ‘ট্যাগ’ মাথায় নিয়ে সে আজও স্কুলে সহপাঠীদের হাসির পাত্র হয়।”
আরেকজন অভিভাবক রোকসানা হক বলেন, “শুরুতে এক বিশেষজ্ঞ বললেন, আমার মেয়ের খুব হালকা মাত্রায় অটিজম আছে। পরবর্তী পাঁচজন ডাক্তার একই পরীক্ষা করে বললেন উল্টোটা—জটিল কোনো সমস্যা নেই। এভাবে তথ্যের অসংগতি নিয়ে আমরা বেশ দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম।”
কেন ঘটছে এই ওভারডায়াগনোসিস?
গবেষকদের মতে, দু-তিন দশক আগেও অনেক রোগ ও অবস্থাকে গুরুত্বসহকারে ধরা হতো না, যা অবশ্যই একটি সমস্যার জন্ম দিয়েছিল—অনেক রোগী সঠিক সময়ে সেবা পেতেন না। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেই সমস্যার “সচেতনতা” বাড়াতে গিয়ে এখন উল্টো চিত্র দেখা যাচ্ছে। রোগের সংজ্ঞা ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে, মৃদু উপসর্গ থাকলেই ডাক্তাররা দ্রুত একটি লেবেল বসিয়ে দিচ্ছেন বা রোগীরা নিজেই ‘সাধারণ উপসর্গ’ খুঁজে পেয়ে অনলাইনে নিজেদের রোগ নির্ণয় করে ফেলছেন।
সুজান ও’সালিভান এই প্রবণতাকে “সঠিক সাহায্যের অভাব পূরণে তড়িঘড়ি করা মানসিক নিশ্চয়তা খোঁজা” বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, “রোগীরাও প্রায়ই দ্রুত কোনো ‘নামকরণ’ বা ডায়াগনোসিস শুনে আশ্বস্ত হতে চান, আবার ডাক্তারেরাও অনেক সময় সেই চাহিদা পূরণে তাড়াতাড়ি একটি লেবেল দিয়ে দেন। কিন্তু যখন এর কার্যকর কোনো চিকিৎসা পাওয়া যায় না, তখন সেটিই রোগীর মনে বাড়তি শঙ্কার জন্ম দেয়।”
আতঙ্ক বনাম বাস্তবতা
ওভারডায়াগনোসিসের ক্ষতিকর প্রভাব শুধু স্নায়ুবিক বা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় নয়, ক্যানসার স্ক্রিনিং Program বা অন্যান্য চিকিৎসা পরীক্ষাগারে সবখানেই দেখা যায়। ধরুন, প্রস্টেট ক্যানসার বা স্তন ক্যানসার নির্ণয়ে অতিসংবেদনশীল টেস্টের কারণে অনেকের অপ্রয়োজনীয়ভাবে “ক্যানসার” লেবেল বসে যায়। কিন্তু এগুলোর অনেকটাই হয়তো কখনোই প্রাণঘাতী পর্যায়ে যেত না। তবু রোগী আগে থেকেই অত্যধিক মানসিক চাপ ও চিকিৎসার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় ভোগেন।
একটি কোচরেইন রিভিউর তথ্যের বরাতে ডা. ও’সালিভান বলেন, “ডায়াগনস্টিক স্ক্রিনিং কখনোই শূন্য-ঝুঁকি নয়। সুস্থ মানুষের শরীরে রোগ খুঁজতে গেলে কেউ কেউ অনিবার্যভাবেই ‘অতিরিক্ত চিকিৎসা’ পেয়ে যাবেন। একদিকে যেমন কিছু জীবন বাঁচতে পারে, অন্যদিকে আবার অনেকেই অকারণে ওষুধ সেবন বা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে আরও বিপদ ডেকে আনবেন।”
সমাধানের পথ ও পরামর্শ
প্রথমত, ডাক্তারদের উচিত রোগনির্ণয়ের আগে-Patient Counseling-এর মাধ্যমে রোগীকে আশ্বস্ত করা যে সব উপসর্গের জন্য লেবেল প্রয়োজন পড়ে না। অনেকে স্রেফ জীবনযাত্রার পরিবর্তন, মানসিক সমর্থন বা সময় মতো পরামর্শের মাধ্যমে সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন।
দ্বিতীয়ত, ডাক্তারি পরীক্ষায় কোনো “সন্দেহজনক” ফলাফল পেলে রোগীকে সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কিত না করে পর্যাপ্ত তথ্য ও সময় দেওয়া জরুরি। “ওয়াচফুল ওয়েটিং” বা পর্যবেক্ষণে রাখার ব্যবস্থা অনেক ক্যানসার স্ক্রিনিং-এ উপকারী হতে পারে।
তৃতীয়ত, অভিভাবক কিংবা রোগীর নিজের উচিত, সম্ভাব্য ‘সোজা উপসর্গ’ খুঁজে পেয়ে চিকিৎসকের কাছে দৌড়ানোর আগে তথ্য ও পরামর্শ যাচাই করে নেওয়া। ব্লগ, ইউটিউব বা সামাজিক মাধ্যমে দেখা-বলা সবকিছু নিজের ওপর প্রয়োগ না করে চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের মতামত নিতে হবে।
চতুর্থত, স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি দরকার তেমন সঠিক পরিকাঠামো—যাতে রোগীদের প্রয়োজন মতো মানসিক সেবা, কাউন্সেলিং সাপোর্ট এবং বিশেষজ্ঞদের টিম ওয়ার্ক নিশ্চিত হয়।
বিশেষজ্ঞের চূড়ান্ত অভিমত
সুজান ও’সালিভানের মতে, আজকের দিনে ওভারডায়াগনোসিস একটি নীরব “মহামারি” হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, “আমরা সবাই ভালো চাই—প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ ধরে দ্রুত চিকিৎসার আওতায় আনতে চাই। কিন্তু বাড়তি তাড়াহুড়ো করে, সামান্য উপসর্গেও বড় রোগের লেবেল বসিয়ে দিলে রোগী মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এতে আসল রোগীরাও সঠিক চিকিৎসা পাওয়ার আগেই একধরনের আতঙ্কে ভোগেন এবং সমাজে চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর অনাস্থা তৈরি হয়।”
অনেক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও মনোবিদ এখন বলছেন, আমাদের উচিত স্বাস্থ্যব্যবস্থায় আরও সংযমী হওয়া—শুধু রোগনির্ণয়ের সংখ্যাকে বাড়ানোর চেয়ে রোগীর সামগ্রিক মঙ্গল ও মানসিক স্বস্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া। কারণ, দিনশেষে রোগচিহ্নিতকরণ না, রোগমুক্তিই আসল লক্ষ্য।
শেষকথা
রিনির গল্প যে খুব ব্যতিক্রমী, তা কিন্তু নয়। শহরের ব্যস্ত চিকিৎসাকেন্দ্রগুলোতে প্রতিদিনই দেখা যায় এমন শত শত কাহিনি। পরিণামে, স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সচেতনতার নামে অনেকে পান অপ্রয়োজনীয় ‘রোগীর তকমা’, যা তাদের মানসিক শান্তি কেড়ে নেয়। “শরীর-মন দুটোকেই সুস্থ রাখা জরুরি, তাই রোগনির্ণয়ের পাশাপাশি রোগমুক্তির উপায় ও রোগ-সচেতনতার গুণগত মান বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া দরকার”—এমনটাই মনে করেন মনোবিদ সৈয়দা অনুজা রহমান।
এখন সময়, আমরা একটু থামি। বোঝার চেষ্টা করি—সব উপসর্গ রোগ নয়, সব সময় একটা ডায়াগনোসিস দিলেই কোনো ম্যাজিকাল সমাধান চলে আসে না। বরং কখনও কখনও অপেক্ষা, পর্যবেক্ষণ, আর মৌলিক জীবনের প্রতি আস্থা রাখাই হতে পারে সুস্থ থাকার আসল চাবিকাঠি। দায়িত্বশীল সংবাদমাধ্যম হিসেবে আমরা আশা করব, চিকিৎসাজগৎ ও সমাজ একযোগে কাজ করে এই ওভারডায়াগনোসিসের সংকটকে মোকাবিলা করবে, যাতে আরও একটিও ‘রিনি’ অকারণে নিজের শৈশব আর মনোবল হারিয়ে না ফেলে।




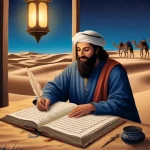



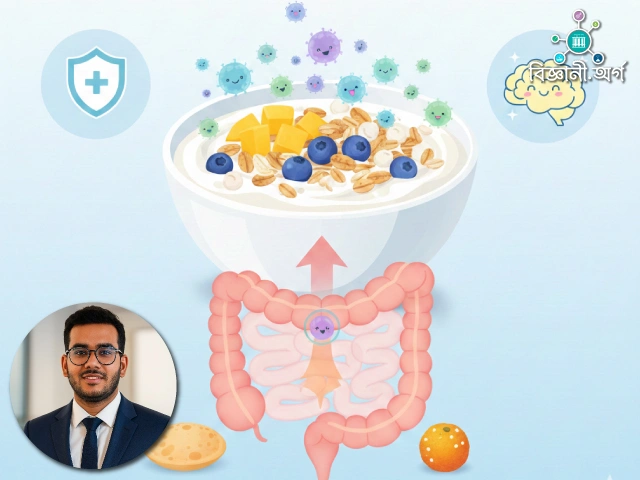


Leave a comment