ড. মশিউর রহমান
মানবসভ্যতার ইতিহাসে কিছু প্রতিষ্ঠান কেবল অর্থনৈতিক শক্তির প্রতীক হয়ে ওঠেনি, বরং প্রযুক্তিগত সক্ষমতার মাপকাঠি হিসেবেও দাঁড়িয়েছে। ১৯৮০ ও ৯০-এর দশকে ‘ইন্টেল’ ছিল তেমনই এক নাম। তাদের প্রসেসর ছাড়া ব্যক্তিগত কম্পিউটার ভাবাই যেত না, আর প্রযুক্তি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় উদ্ভাবনের পেছনে ছিল এই কোম্পানির নীরব কিন্তু নিরলস কাজ। কিন্তু আজ, মাত্র দুই দশকের মধ্যে, সেই একসময়ের শীর্ষস্থানীয় চিপ নির্মাতা বিশ্বের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়েছে, এমনকি রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে চলে এসেছে।
এই পতনের গল্প শুরু হয় ২০০০-এর দশকের গোড়ায়। তখন ইন্টেল ভাবছিল, পিসি বাজারের বাইরে আরও নতুন খাত জয় করতে হবে। তাই তারা টেলিকম ও ওয়্যারলেস প্রযুক্তি খাতে একের পর এক কোম্পানি কিনতে শুরু করে। ধারণা ছিল, ইন্টারনেটের বিস্তার এবং মোবাইল বিপ্লবের যুগে এসব খাতই হবে ভবিষ্যতের সোনার খনি। কিন্তু অধিগ্রহণও এক ধরনের শিল্প, যেখানে সঠিক লক্ষ্য নির্বাচন, সংহতকরণ, এবং নতুন প্রযুক্তি কাজে লাগানোর কৌশল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইন্টেলের এই ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলাফল—১২ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ শূন্য বা ঋণাত্মক রিটার্নে শেষ হয়। হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের অধ্যাপক ডেভিড ইয়ফি পরে বলেন, “১০০% সেই অধিগ্রহণ ব্যর্থ হয়েছিল।”
এরপর আসে এক ঐতিহাসিক ভুল—মোবাইল প্রসেসরের বাজারে সঠিক সময় ও সঠিক কৌশল নিতে ব্যর্থতা। ইন্টেল জনপ্রিয় ব্ল্যাকবেরি ফোনের জন্য ব্রিটিশ কোম্পানি Arm-এর নকশাকৃত চিপ সরবরাহ করত। কিন্তু তারা সিদ্ধান্ত নেয়, নিজস্ব x86 আর্কিটেকচারের চিপ বানাবে, যাতে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে থাকে। পরিকল্পনা ছিল এক বছরের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পণ্য আনার, কিন্তু বাস্তবে তা দশ বছরেও হয়নি। এর মধ্যে অ্যাপল, কোয়ালকম, স্যামসাং বাজার দখল করে নেয়, আর ইন্টেলকে স্মার্টফোন প্রসেসরের বাজার থেকে সরে দাঁড়াতে হয়।
বছরের পর বছর ব্যবস্থাপনার সমস্যাও বাড়তে থাকে। নতুন চিপ লঞ্চে দেরি, উৎপাদন প্রযুক্তিতে ব্যর্থতা, বাজারে প্রতিযোগিতামূলক পণ্য না আনা—সব মিলিয়ে ইন্টেলের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে। ২০২১ সালের মধ্যে তারা প্রতিযোগীদের তুলনায় দুই প্রজন্ম পিছিয়ে পড়ে। প্রতিদ্বন্দ্বীরা তখন তাইওয়ানের TSMC ও দক্ষিণ কোরিয়ার স্যামসাং—যারা শুধু প্রযুক্তিগতভাবে এগিয়েই ছিল না, বরং ‘ফাউন্ড্রি মডেল’-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়ে উঠেছিল।
এমন এক সময়ে ইন্টেল তাদের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার প্যাট গেলসিঞ্জারকে সিইও হিসেবে ফিরিয়ে আনে। গেলসিঞ্জার যুক্তরাষ্ট্রে আবার উন্নতমানের চিপ উৎপাদনের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা নেন। কিন্তু উৎপাদন সমস্যার সমাধান না হওয়া, বাজারের আস্থা ফেরাতে ব্যর্থতা এবং শেয়ারমূল্যের পতনে বোর্ড ২০২৫ সালের শুরুতে তাঁকে সরিয়ে লিপ-বু ট্যানকে নিয়োগ দেয়।
ট্যানের নিয়োগের কয়েক মাসের মধ্যেই নতুন বিতর্ক। ২০২৫ সালের ৭ আগস্ট সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প Truth Social-এ দাবি করেন, ট্যান “অত্যন্ত স্বার্থের দ্বন্দ্বে জড়িত” এবং তাঁকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। এর পেছনে ছিল সিনেটর টম কটনের অভিযোগ, ট্যান বহু চীনা কোম্পানির সাথে যুক্ত এবং তাঁর সময়ে একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান মার্কিন রপ্তানি আইন ভঙ্গ করেছে। ট্যান অভিযোগ অস্বীকার করলেও বাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে—শেয়ারমূল্য পড়ে যায় ৫%।
ইন্টেলের উত্থান ও বৈশ্বিক সেমিকন্ডাক্টর প্রেক্ষাপট
১৯৬৮ সালে সিলিকন ভ্যালিতে রবার্ট নয়েস ও গর্ডন মুর ইন্টেলের প্রতিষ্ঠা করেন। মুরের ‘মুর’স ল’—যা বলেছিল, প্রতি দুই বছরে চিপের ক্ষমতা দ্বিগুণ হবে—দশকের পর দশক প্রযুক্তি শিল্পের গতিপথ নির্ধারণ করেছে। ১৯৭১ সালে ইন্টেল চালু করে বিশ্বের প্রথম বাণিজ্যিক মাইক্রোপ্রসেসর Intel 4004।
১৯৮০–৯০-এর দশকে ইন্টেল ও মাইক্রোসফটের যুগলবন্দি “Wintel” আধিপত্য বিস্তার করে। ডেল, এইচপি, কমপ্যাক—সব বড় পিসি নির্মাতা ইন্টেলের চিপ ব্যবহার করত। বিশ্ব সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে তখন জাপান বড় প্রতিযোগী হলেও ইন্টেলের প্রযুক্তি ও কৌশল তাদের শীর্ষে রাখে।
কিন্তু ২০০০-এর দশকে বাজারের চেহারা বদলায়। ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, স্মার্টফোন—সব মিলিয়ে চিপ শিল্পে চাহিদার ধরণ পরিবর্তিত হয়। এখানে TSMC ও স্যামসাং ‘ফাউন্ড্রি মডেল’ নিয়ে এগিয়ে যায়—নিজেদের ডিজাইন না করে, অন্যের ডিজাইন নিয়ে অত্যাধুনিক কারখানায় চিপ তৈরি করে। অ্যাপল, এনভিডিয়া, কোয়ালকম—এসব কোম্পানি দ্রুত এই মডেল বেছে নেয়। ইন্টেল এই পরিবর্তনকে গুরুত্ব দেয়নি, যা তাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি বিপর্যয় ডেকে আনে।
জাতীয় নিরাপত্তা ও চিপ শিল্প
আজ উন্নতমানের চিপ কেবল বাণিজ্যিক নয়, জাতীয় নিরাপত্তার অংশ। আধুনিক সামরিক প্রযুক্তি, সাইবার নিরাপত্তা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা—সবকিছুই নির্ভর করে সেমিকন্ডাক্টরের ওপর। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত চিপ উৎপাদন হয় কেবল তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়ায়। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এটি ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়লে এই সরবরাহ চেইন ভেঙে পড়তে পারে।
এই প্রেক্ষাপটে ২০২২ সালে মার্কিন কংগ্রেস CHIPS and Science Act পাস করে, যাতে দেশীয় চিপ উৎপাদন বাড়াতে বিলিয়ন ডলার ভর্তুকি দেওয়া হয়। ইন্টেল পায় সবচেয়ে বেশি প্রতিশ্রুতি—৮ বিলিয়ন ডলার অনুদান ও ঋণ। তবুও উৎপাদন সমস্যার সমাধান না হওয়ায় তারা এই সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হচ্ছে।
বাংলাদেশের জন্য শিক্ষা
ইন্টেলের পতনের গল্প থেকে বাংলাদেশের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়।
প্রথমত, প্রযুক্তি নেতৃত্ব ধরে রাখা ক্রমাগত উদ্ভাবন ও দ্রুত সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। আজ যারা এগিয়ে, কাল তারা পিছিয়ে পড়তে পারে যদি প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে না পারে।
দ্বিতীয়ত, সরকারি ভর্তুকি সফলতার নিশ্চয়তা নয়। শুধু অর্থ নয়, কার্যকর ব্যবস্থাপনা, দক্ষ জনবল, ও সময়মতো ডেলিভারি সমান গুরুত্বপূর্ণ।
তৃতীয়ত, প্রযুক্তি শিল্প এখন জাতীয় নিরাপত্তার অংশ। স্যাটেলাইট প্রযুক্তি, সাইবার প্রতিরক্ষা, উন্নত চিপ—এসব কৌশলগত সম্পদ। বাংলাদেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রযুক্তি নীতি জরুরি।
চতুর্থত, মানবসম্পদ উন্নয়নই সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ। উন্নত প্রযুক্তি শিল্পে দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার, গবেষক, ও ম্যানেজারের অভাব থাকলে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যায় না।
পঞ্চমত, গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনে কৌশলগত অবস্থান নিতে হবে। সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনে না পারলেও সফটওয়্যার, ডিজাইন সাপোর্ট, আইটি সার্ভিস, ও হার্ডওয়্যার অ্যাসেম্বলিতে বড় ভূমিকা রাখা সম্ভব।
ইন্টেলের এই কাহিনি আসলে এক সতর্কবার্তা—প্রযুক্তি শিল্পে শীর্ষে ওঠা কঠিন, কিন্তু সেখানে টিকে থাকা আরও কঠিন। বাংলাদেশের জন্য এখনই সময় নীতি, বিনিয়োগ, শিক্ষা, এবং উদ্ভাবনকে একই স্রোতে বেঁধে দেওয়া, যেন আমরা শুধু বাজারের অংশীদার নই, বরং প্রযুক্তির দিকনির্দেশক হতে পারি।


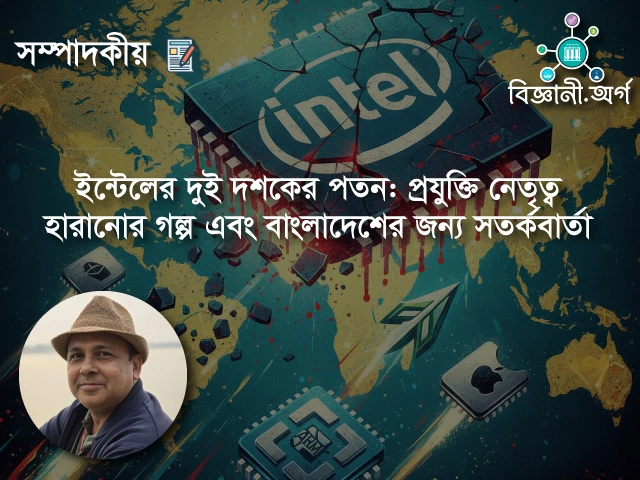

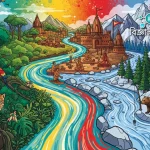
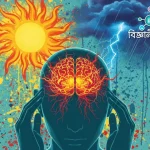
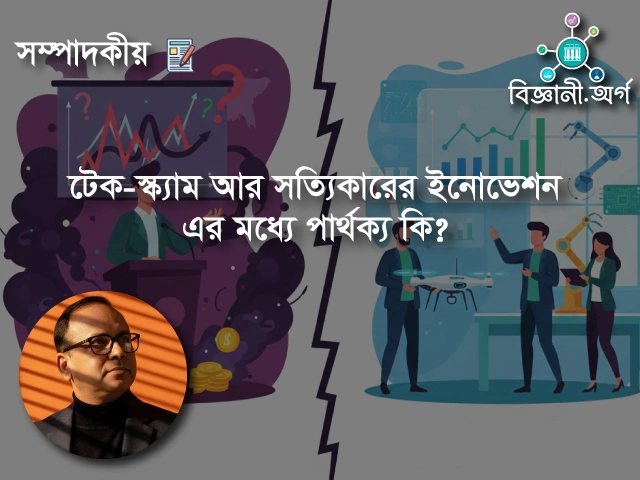

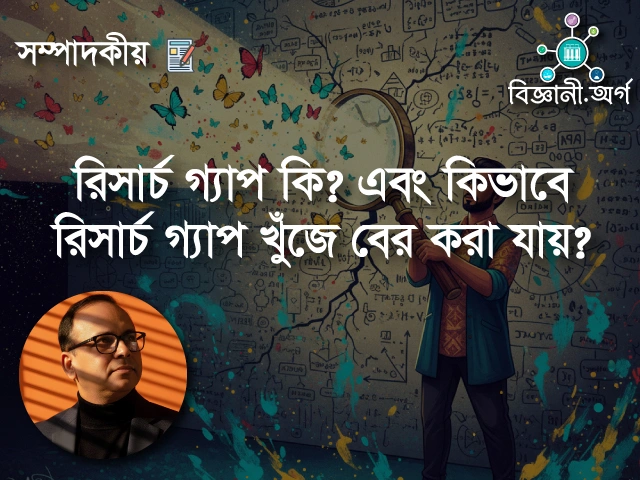
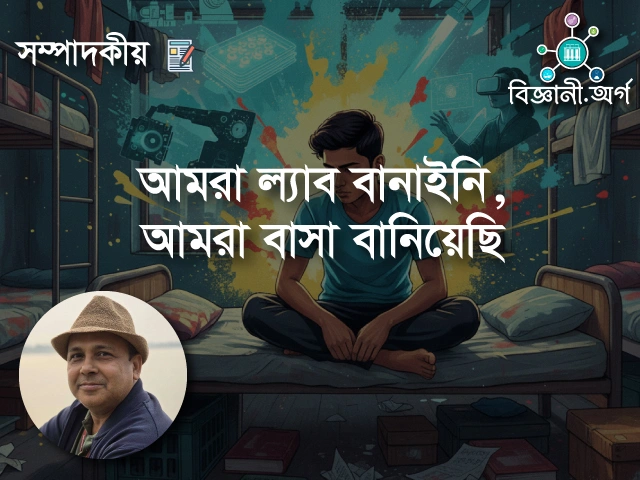
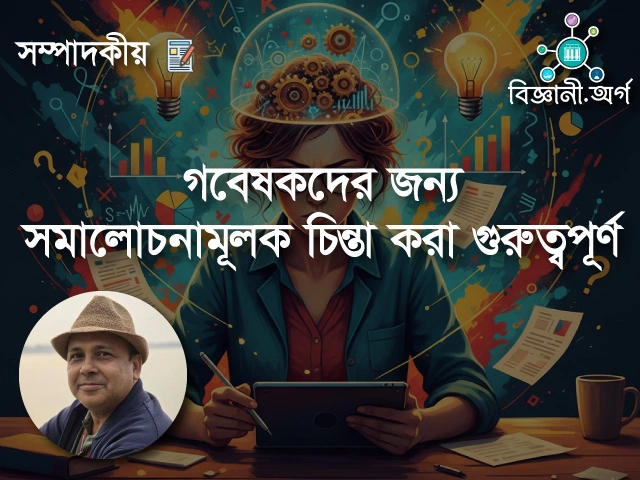
Leave a comment