কোনো দেশের ভবিষ্যৎ কীভাবে গড়ে ওঠে—প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে, নাকি সঠিক কৌশল ও প্রযুক্তি দিয়ে? ইন্দোনেশিয়া মনে করছে উত্তরটি প্রযুক্তির দিকেই বেশি ঝুঁকে আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই বৃহৎ রাষ্ট্র সম্প্রতি উন্মোচন করেছে তাদের জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) রোডম্যাপ, যার লক্ষ্য ২০৪৫ সালের মধ্যে দেশকে নিয়ে যাওয়া তথাকথিত “গোল্ডেন ইন্দোনেশিয়া”–র পথে। সরকারের যোগাযোগ ও ডিজিটাল বিষয়ক মন্ত্রী মেউতিয়া হাফিদ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, এআই শুধু প্রযুক্তি নয়, বরং একটি কৌশলগত হাতিয়ার, যা দেশের উন্নয়নের ধারা বদলে দিতে পারে যদি সঠিক শাসন কাঠামো এবং কার্যকর পরিকল্পনা থাকে।
এই রোডম্যাপ আসলে একটি শ্বেতপত্র—যেখানে নীতিগত দিকনির্দেশনা, উন্নয়ন অগ্রাধিকার এবং অর্থায়নের কাঠামো তুলে ধরা হয়েছে। সরকার একে বলছে “অন্তর্ভুক্তিমূলক ও নৈতিক এআই নীতি”–র ভিত্তি। প্রস্তুত করেছে ৪৪৩ সদস্যের এক টাস্কফোর্স, যেখানে সরকারি কর্মকর্তা, গবেষক, শিল্পখাতের প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজ এমনকি গণমাধ্যমও যুক্ত ছিল। এর ফলে নথিটি শুধু প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমাজের নানা স্তরের দৃষ্টিভঙ্গি এতে প্রতিফলিত হয়েছে। শ্বেতপত্রটি এখন খোলা পরামর্শের জন্য জনগণের হাতে দেওয়া হয়েছে, যাতে আরও মতামত যোগ হয় এবং নীতি হয়ে ওঠে বাস্তবতার কাছাকাছি।
ইন্দোনেশিয়ার এআই যাত্রার শুরু অবশ্য আজকের নয়। ২০২০ সালেই দেশটি প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কৌশল প্রণয়ন করেছিল। কিন্তু ২০২২ সালের শেষ থেকে জেনারেটিভ এআই–এর উত্থান এত দ্রুত হয়েছে যে পুরোনো পরিকল্পনা অনেকাংশেই পিছিয়ে পড়েছে। তাই নতুন রোডম্যাপকে বলা হচ্ছে আপডেটেড কৌশল, যা বিশ্ব প্রযুক্তির গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশকে এগিয়ে নেবে। আর এই রোডম্যাপের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছে তিনটি বড় স্তম্ভ: দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, গবেষণা ও শিল্প উদ্ভাবন, এবং অবকাঠামো ও ডেটা শক্তিশালীকরণ।
মানবসম্পদের দিকে নজর দিলে দেখা যায়, ইন্দোনেশিয়া প্রতি বছর এক লাখ এআই-প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির লক্ষ্য নিয়েছে। তাদের মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশ হবে ডেভেলপার, আবার তার মধ্যে ৩০ শতাংশ বিশেষজ্ঞ আর ৭০ শতাংশ ব্যবহারিক প্রয়োগকারী। বাকি ৭০ শতাংশ হবে সাধারণ ব্যবহারকারী যারা নিজেদের কাজের ক্ষেত্রে এআইকে কাজে লাগাতে পারবে। একই সঙ্গে, সরকার চায় ২০২৯ সালের মধ্যে অন্তত ২ কোটি মানুষ যেন এআই–এর প্রাথমিক জ্ঞান রাখে। এমন উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা হয়তো কারও কাছে অবাস্তব শোনাতে পারে, কিন্তু বৃহৎ জনসংখ্যার দেশ হিসেবে ইন্দোনেশিয়ার হাতে যদি সঠিক শিক্ষানীতি থাকে তবে এটি অসম্ভব নয়।
শুধু দক্ষতা নয়, গবেষণা ও শিল্পখাতেও রয়েছে বড় চিন্তা। সরকার বলছে, গবেষণাকে হতে হবে অগ্রসর, প্রাসঙ্গিক এবং সমাজের কাজে লাগার মতো। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প খাতকে একসঙ্গে কাজ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হবে। থাকবে “ওপেন স্যান্ডবক্স” প্ল্যাটফর্ম, যেখানে নতুন উদ্ভাবন পরীক্ষা করা যাবে মুক্ত পরিবেশে। এর ফলে শুধু কাগজে-কলমে নয়, বাস্তব জীবনেও এআই সমাধান দেখা যাবে কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা কিংবা পরিবহন খাতে।
অবকাঠামো হলো রোডম্যাপের তৃতীয় স্তম্ভ। এআইকে কাজে লাগাতে দরকার উচ্চক্ষমতার কম্পিউটিং, জিপিইউ/টিপিইউ এবং নির্ভরযোগ্য ডেটা সেন্টার। ইন্দোনেশিয়া এজন্য জাতীয় পর্যায়ের ক্লাউড অবকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে, যেখানে থাকবে সার্বভৌম ডেটা সেন্টার—যা দেশের ভেতরেই ডেটা সংরক্ষণ করবে নিরাপদভাবে। পাশাপাশি রয়েছে সবুজ ডেটা সেন্টারের পরিকল্পনা, যেখানে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জ্বালানি দক্ষ ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। প্রযুক্তির উন্নয়ন যদি পরিবেশের ক্ষতি করে, তবে তা টেকসই নয়—এই উপলব্ধিও নথিতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে।
কৌশলগত অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রেও রোডম্যাপটি উল্লেখযোগ্য। কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনীতি, প্রশাসন সংস্কার, জ্বালানি ও পরিবেশ—সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আগামী তিন বছরে, ২০২৫ থেকে ২০২৭–এর মধ্যে, বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে জনসেবা খাতে। স্বাস্থ্য খাতে এআই ব্যবহার হবে রোগ নির্ণয়ে, দূরবর্তী রোগী পর্যবেক্ষণে, ওষুধ ও টিকার সঠিক বণ্টনে। শিক্ষায় থাকবে অভিযোজিত শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম, যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য থাকবে আলাদা কনটেন্ট। এমনকি পরীক্ষার খাতাও স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। গণপরিষেবায় থাকবে চ্যাটবট ও ডেটা বিশ্লেষণভিত্তিক নীতি সহায়তা। পরিবহন খাতে তৈরি হবে স্মার্ট ট্রাফিক সিস্টেম ও উন্নত গণপরিবহন ব্যবস্থাপনা।
অবশ্য এতসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন অর্থায়ন। ইন্দোনেশিয়ার সরকার তাই ধাপে ধাপে অর্থায়নের কাঠামো সাজিয়েছে। এতে থাকবে সরকারি বাজেট, বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ, এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব। নতুন প্রতিষ্ঠিত সার্বভৌম সম্পদ তহবিল “দানান্তারা” বিশেষ ভূমিকা নেবে এই প্রক্রিয়ায়। তারা গড়ে তুলবে “সোভরেইন এআই ফান্ড” এবং তৈরি করবে উদ্ভাবনী অর্থনৈতিক উপকরণ। প্রথম পর্যায়ে অর্থ যাবে গবেষণা, পরীক্ষামূলক প্রকল্প এবং অবকাঠামো তৈরিতে। পরে তা বিস্তৃত হবে শিল্পখাত, বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্টার্টআপ পর্যন্ত।
ইন্দোনেশিয়ার এই এআই রোডম্যাপ শুধু প্রযুক্তির নথি নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক ধরনের দিকনির্দেশনা। যে দেশটি একসময় উপনিবেশের শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতা পেয়েছিল, এখন সেই দেশই ডিজিটাল বিশ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে নেতৃত্বের জায়গায়। তবে প্রশ্ন থেকে যায়—এমন পরিকল্পনা বাস্তবে কতটা কার্যকর হবে? লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কি পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, দক্ষতা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা বজায় রাখা সম্ভব হবে? সময়ই হয়তো এর উত্তর দেবে।
কিন্তু একটি জিনিস স্পষ্ট—ইন্দোনেশিয়া বুঝে গেছে, ২১ শতকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শুধু প্রযুক্তি নয়, বরং অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। যদি তারা এই রোডম্যাপ সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে, তবে শুধু “গোল্ডেন ইন্দোনেশিয়া ২০৪৫”–এর স্বপ্নই পূরণ হবে না, বরং বিশ্বমঞ্চে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক নতুন প্রযুক্তিশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে ইন্দোনেশিয়া। আর এ অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশসহ অন্য উন্নয়নশীল দেশগুলিও নিতে পারবে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা—কীভাবে পরিকল্পনা, নীতি আর প্রযুক্তিকে একত্র করে তৈরি করা যায় ভবিষ্যতের পথ।





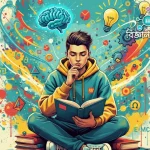
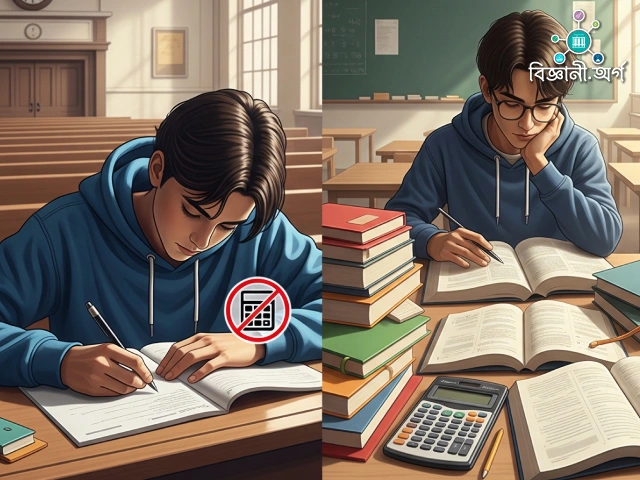

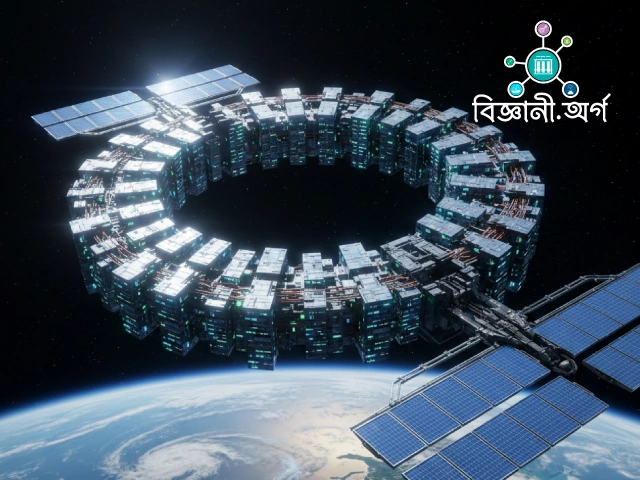
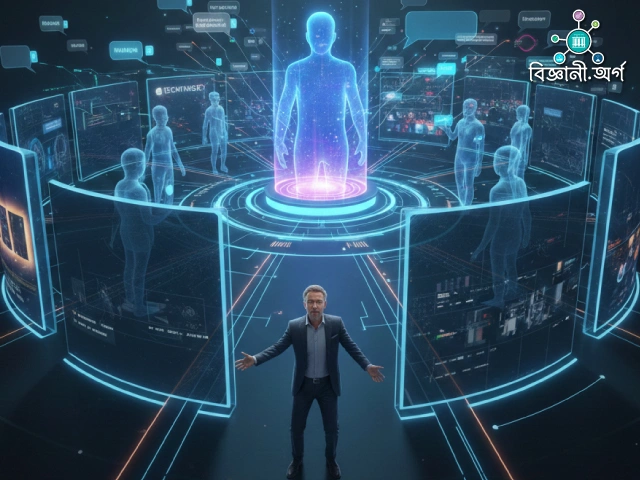
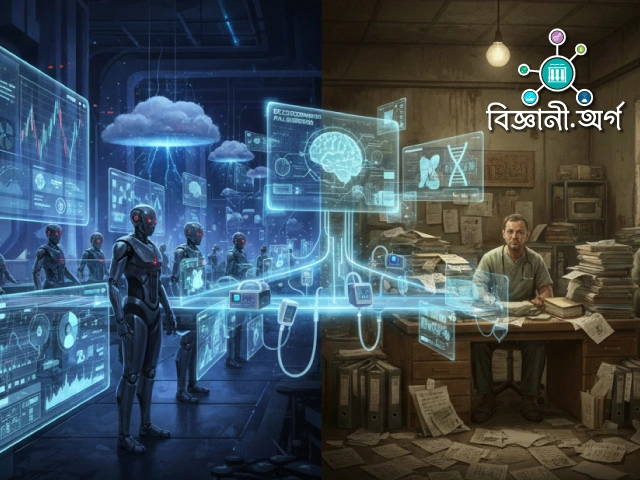
Leave a comment