ছবি: সিঙ্গাপুরের চাইনিজ গার্ডেন স্টেশনের পাশের দৃশ্য।
==== ড. মশিউর রহমান ===
একটা সময় ছিল যখন মানুষের জীবনের কেন্দ্র ছিল পরিবার, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, এবং একসাথে বাঁচার চেষ্টা। আমাদের চিন্তা-ভাবনার ভেতরে ‘আমরা’ শব্দটির প্রাধান্য ছিল। পরিবারের ছোট-বড় সিদ্ধান্ত হোক বা পাড়ার কোনো উৎসব—সবকিছুতেই ছিল সম্মিলিত অংশগ্রহণ, পারস্পরিক সহযোগিতা। কিন্তু সময় বদলেছে। আর সেই বদলের কেন্দ্রে এসেছে এক নতুন ধারণা—ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা। ইংরেজিতে যাকে বলে personalization।
ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার এই আগ্রাসী প্রবণতা প্রযুক্তির হাত ধরেই আমাদের জীবনে ঢুকেছে। আগে সামাজিক যোগাযোগের কেন্দ্রে থাকত সমাজ, এখন সেখানে স্থান পেয়েছে ‘আমি’। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক—সব জায়গাতেই আমরা দেখছি, কেবল ‘আমার’ ছবি, ‘আমার’ অনুভূতি, ‘আমার’ পছন্দ, ‘আমার’ মতামত। এমনকি আজকাল ই-কমার্স সাইট, ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম কিংবা গুগল সার্চ—সবকিছুই আমাকে চিনে নিচ্ছে, আমাকে জানছে, আমাকে সাজিয়ে দিচ্ছে এক কাল্পনিক আয়নায় যেখানে আমি সবকিছুর কেন্দ্র।
এই পরিবর্তনের সামাজিক প্রভাব গভীর এবং বহুমাত্রিক। পরিবার ছোট হয়ে এসেছে, যৌথ পরিবারের ধারণা প্রায় বিলুপ্তির পথে। আজকাল মানুষ একা থাকতে চায়, একলা সময় কাটাতে পছন্দ করে। বন্ধুত্ব, বিবাহ, এমনকি সহকর্মীদের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক—সবকিছুতেই যেন এক ধরণের ক্লান্তি। কারণ, অন্যের সঙ্গে মেলামেশা মানেই নিজেকে সামান্য হলেও বদলাতে হতে পারে, মানিয়ে নিতে হতে পারে। আর এই মানিয়ে নেওয়ার প্রবণতা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের ভেতর থেকে।
এর চেয়েও ভয়াবহ ব্যাপার হচ্ছে, এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতা আমাদের সহানুভূতির জায়গাটাকেও দুর্বল করে দিচ্ছে। যদি কেউ আমার মতো না হয়, আমার চিন্তা না করে, আমার মতো কথা না বলে, তবে তাকে আমি সহ্য করতে পারি না। যে কারণে সমাজে বাড়ছে মেরুকরণ, বাড়ছে সহিষ্ণুতার অভাব। ব্যক্তিত্বের ভিন্নতা এখন আমাদের জন্য বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, একে বৈচিত্র্য হিসেবে আর কেউ দেখছে না।
এই সমস্যার শিকড় আরও গভীরে ছড়িয়ে পড়ছে যখন আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) যুগে প্রবেশ করছি। চ্যাটবট, ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট, প্রেডিক্টিভ অ্যালগরিদম—সবকিছুই যেন তৈরি হচ্ছে আমার পছন্দ অনুযায়ী সেবা দেওয়ার জন্য। আমি যা শুনতে চাই, তা-ই শুনিয়ে দিচ্ছে স্পটিফাই; আমি যে খবর পড়তে চাই, সেটাই দেখাচ্ছে গুগল নিউজ। আর আমি যেমন ধরনের মানুষদের দেখতে চাই, তেমন মানুষের প্রোফাইলই দেখাচ্ছে ফেসবুক কিংবা লিংকডইন।
সম্প্রতি একটি গবেষণায় দেখা গেছে, তরুণ প্রজন্মের অনেকেই বাস্তব বন্ধুর চেয়ে ভার্চুয়াল চ্যাটবটের সঙ্গে কথা বলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে। কারণ, বাস্তব বন্ধু ‘না’ বলে, দ্বিমত করে, সমালোচনা করে। কিন্তু চ্যাটবট সবসময় ইতিবাচক কথা বলে, কখনো বিরুদ্ধমত দেয় না। এ এক ধরনের ভার্চুয়াল দুনিয়া যেখানে আমি শাসক, আমি শ্রোতা, আমি বিচারক—সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে আমি নিজেই।
এই নতুন সমাজব্যবস্থা আমাদের ভবিষ্যৎকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? যদি আগামী প্রজন্ম একে একে সবাই শুধু নিজের ভেতরে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, তাহলে কি একদিন এই পৃথিবী একটি একা একা বাঁচার অভ্যাসে পরিণত হবে না? যদি সবাই কেবল নিজেকে বোঝে, তবে অন্যকে বোঝার চেষ্টা কে করবে? যদি সবাই নিজেকে ভালোবাসে, তবে অন্যকে ভালোবাসার জায়গা কোথায় থাকবে?
বিবাহ কিংবা পরিবার গঠনের প্রতি অনীহা এখন আর কেবল ‘আধুনিকতা’র অংশ নয়, বরং এক জৈবিক পরিবর্তনের ফলও বটে। অনেকেই মনে করেন, নিজের জীবনকে অন্য কারও সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার মধ্যে আছে সীমাবদ্ধতা, জটিলতা, এমনকি আত্মত্যাগের ঝুঁকি। তাই নিজের মতো করে, নিজের ছন্দে, নিজের পছন্দের দুনিয়ায় থাকতে চায় মানুষ। কিন্তু একবার কি ভেবেছি, এই ‘নিজের দুনিয়া’টা আদৌ কি সত্যিকারের?
একটি সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন অন্যকে বোঝা, অন্যের মতামত শ্রবণ করা, ভিন্নমতকে শ্রদ্ধা করা। প্রযুক্তি আমাদের আরও ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে তুলতে পারে, কিন্তু সেই প্রযুক্তিকেই যদি আমরা মানবিকতার আলোয় পরিচালিত করতে পারি, তবে হয়তো এই সমস্যার কিছুটা হলেও সমাধান সম্ভব। আমাদের প্রয়োজন এমন শিক্ষা ও সচেতনতা, যা তরুণ প্রজন্মকে শেখাবে—সবকিছুর কেন্দ্র আমি নই, বরং আমি কেবল একটি বৃহত্তর সমাজের অংশ।
অতএব, ‘আমি’র এই একচ্ছত্র আধিপত্যের যুগে ফিরে দেখা জরুরি ‘আমরা’র দিকে। আমাদের প্রযুক্তি যদি আমাদের একাকী করে তোলে, তবে সেই প্রযুক্তিকে মানবিক করে তোলার দায়টাও আমাদেরই নিতে হবে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার এই ভয়াবহ ঢেউকে রুখে দিতে হলে আমাদের আবার শিখতে হবে একসঙ্গে বাঁচার শিল্প, একসঙ্গে ভাবার কৌশল। না হলে, হয়তো একদিন এই পৃথিবী হবে শুধুই অনেকগুলো ‘আমি’র গুঁটিয়ে রাখা এক একটি নিঃসঙ্গ দ্বীপ। আর তাতে আমাদের মনুষ্যত্বই হারিয়ে যেতে পারে চিরতরে।






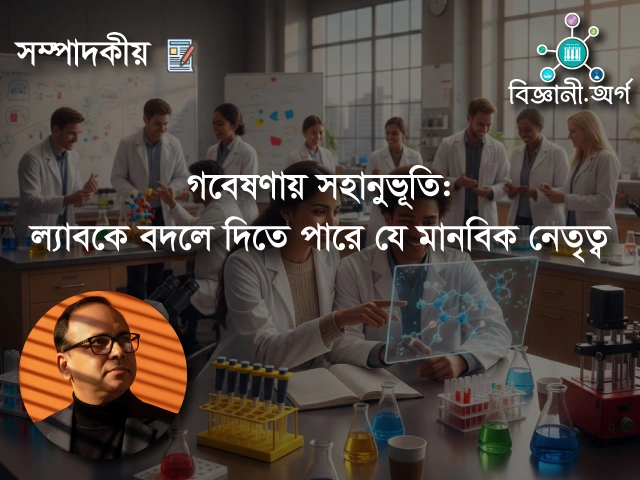
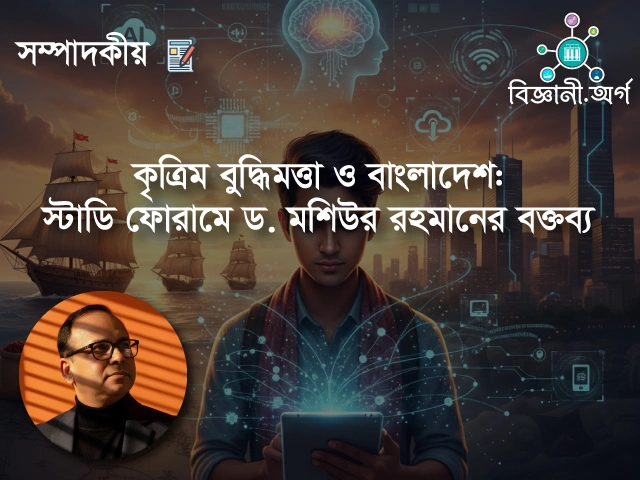
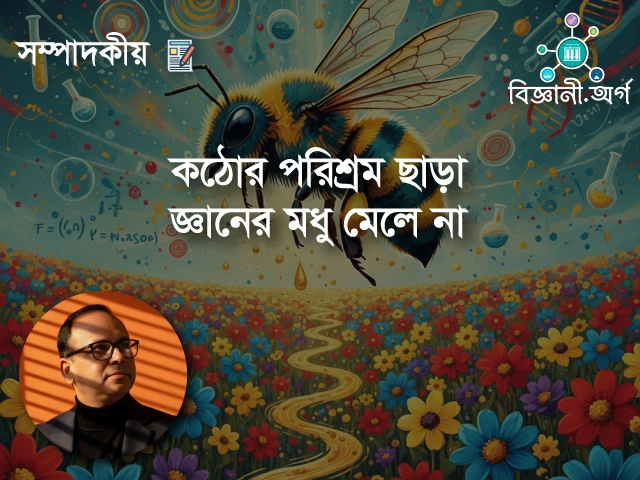
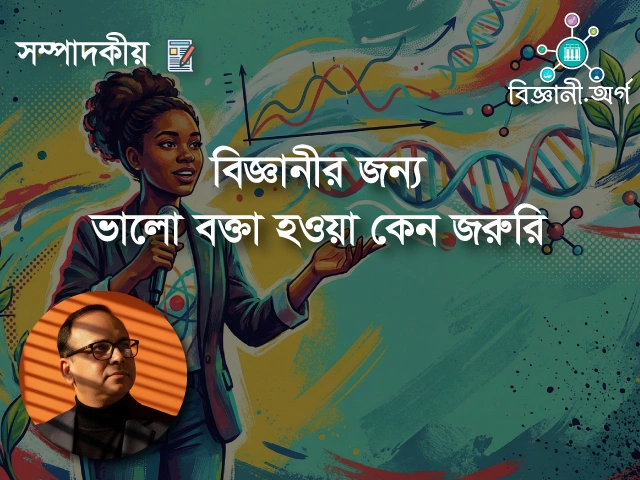
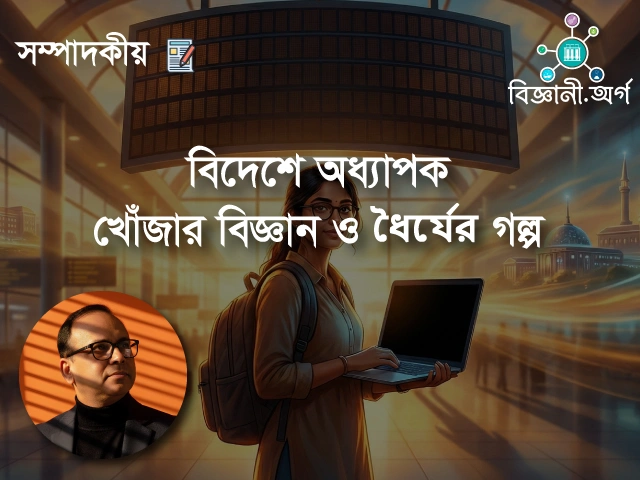
Leave a comment