বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবার আলোচনায় আমরা প্রায়শই ঢাকা ও বড় শহরগুলোকেই কেন্দ্র করে চিন্তা করি। অথচ দেশের প্রায় ৬৮ শতাংশ মানুষ বাস করেন গ্রামে, যেখানে আধুনিক চিকিৎসার আলো এখনো পুরোপুরি পৌঁছায়নি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারীর হার মাত্র ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ। অর্থাৎ, দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ এখনো চিকিৎসা ব্যবস্থার বাইরে বা প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে আছেন।
এই বৈষম্যের মূল কারণ হলো স্বাস্থ্যসেবার অবকাঠামো এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের বণ্টনে ভয়াবহ বৈসাদৃশ্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, দেশের প্রায় ৭০–৮০ শতাংশ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও মানসম্মত হাসপাতাল ঢাকা এবং অন্যান্য নগরকেন্দ্রিক এলাকায় কেন্দ্রীভূত। ফলে হৃদরোগ, ক্যান্সার, কিডনি বা নিউরোলজিক্যাল রোগের মতো জটিল চিকিৎসা সেবা গ্রামে কার্যত অনুপস্থিত। একজন গ্রামীণ রোগীর জন্য রাজধানীতে পৌঁছানো মানেই সময়, অর্থ এবং মানসিক কষ্টের এক দীর্ঘ লড়াই।
এই বাস্তবতার আরও এক করুণ প্রতিফলন দেখা যায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বা ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। পর্যাপ্ত ডাক্তার, নার্স, ল্যাব টেকনিশিয়ান কিংবা ওষুধের ঘাটতি সেখানে নিয়মিত চিত্র। আধুনিক ডায়াগনস্টিক সুবিধা বা উন্নত ল্যাব সেবা না থাকায় রোগ প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়ে না, যার ফল—জটিলতা, চিকিৎসার উচ্চ খরচ এবং অকালমৃত্যু। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ডের অনুপস্থিতি। ফলে একজন রোগীর চিকিৎসা ইতিহাস এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে সহজে পৌঁছায় না, ডাক্তারদের জন্য রোগীর অবস্থা বোঝা হয়ে ওঠে কঠিন।
শুধু অবকাঠামোগত দুর্বলতা নয়, গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে দারিদ্র্য ও শিক্ষার সীমাবদ্ধতার এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, দেশে দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশ এবং অতিদারিদ্র্য ১০.৫ শতাংশ। গ্রামে সাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশের নিচে, আর প্রাথমিক স্বাস্থ্য-সচেতনতা প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে ডায়রিয়া, পানিবাহিত রোগ, অপুষ্টি বা ত্বকের রোগের মতো প্রতিরোধযোগ্য সমস্যাগুলোও গ্রামীণ মানুষকে পঙ্গু করে দেয়, অনেক ক্ষেত্রেই জীবন কেড়ে নেয়।
ঢাকার হাসপাতালে প্রতিদিন প্রায় ৫০ থেকে ৭০ হাজার রোগীর ভিড় হয়, যার ৬০ শতাংশই গ্রাম থেকে আসা। এই রোগীরা দীর্ঘ যাত্রা, থাকার সমস্যা, দীর্ঘ লাইন এবং উচ্চ চিকিৎসা ব্যয়ের চাপে প্রায়শই অসহায় হয়ে পড়েন। অথচ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রতি ১০,০০০ জনে ৪.৫ জন চিকিৎসক থাকার কথা, সেখানে বাংলাদেশে রয়েছে মাত্র ৫ জন। আরও বড় অসামঞ্জস্য দেখা যায় জাতীয় বাজেটে—স্বাস্থ্যখাতে জিডিপির অন্তত ৫ শতাংশ ব্যয় করা উচিত হলেও বাংলাদেশে তা মাত্র ২.৩ শতাংশ।
এই ঘাটতি ও আস্থার সংকটই কোটি কোটি মানুষকে বিদেশমুখী করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০১৮–১৯ অর্থবছরে যেখানে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছিল বিদেশে চিকিৎসায়, সেখানে ২০২৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫–৭ বিলিয়ন ডলার। প্রতিবছর ১০ থেকে ১২ লাখ মানুষ চিকিৎসার জন্য ভারত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া বা থাইল্যান্ডের মতো দেশে যান। মূল কারণগুলো পরিষ্কার—ভুল ডায়াগনোসিস, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ঘাটতি, প্রমাণভিত্তিক দ্বিতীয় মতামতের অনুপস্থিতি এবং চিকিৎসকদের ওপর আস্থার সংকট।
ফলাফল শুধু অর্থের অপচয় নয়, বরং স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রতি এক গভীর আস্থাহীনতা। একদিকে দেশীয় স্বাস্থ্যখাত বিদেশমুখী রোগীর চাপ হারাচ্ছে, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতির ওপর চাপ বাড়ছে। স্বাস্থ্যব্যয়ে বাংলাদেশের মাত্র ১৬.৯ শতাংশ সরকারি বাজেট থেকে আসে, বাকি ৭৩ থেকে ৯৬ শতাংশ গুনতে হয় রোগীদের নিজেদের পকেট থেকে। ফলে গ্রামীণ কিংবা মধ্যবিত্ত মানুষদের জন্য উন্নত চিকিৎসা এক অপ্রাপ্য স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায়।
এখানেই প্রযুক্তির ভূমিকা সামনে আসে। বিশ্বের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বারবার বলছেন—কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), বিগ ডেটা এবং মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে যদি টেলিমেডিসিন ও প্রেডিকটিভ ডায়াগনস্টিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, তবে বৈষম্যের এই দেয়াল ভাঙা সম্ভব। রোগীর ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ড তৈরি হলে ৯৭ শতাংশ সেবা কাভার করা সম্ভব বলে ধারণা দিচ্ছে সাম্প্রতিক গবেষণা। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে টেলিমেডিসিন, অনলাইন রিপোর্ট বিশ্লেষণ, এআই-চালিত ডায়াগনোসিস অ্যাপ এবং স্বাস্থ্যবিমা—সব একত্রে একটি সমন্বিত স্বাস্থ্য ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে পারে।
এমন বাস্তবতায় একটি নতুন সম্ভাবনার নাম—Wikimedix। এই এআই-চালিত অ্যাপটি গ্রামীণ ও নগর উভয় জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার এক সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য সমাধান হতে পারে। মোবাইলভিত্তিক এই প্ল্যাটফর্মে থাকছে স্কিন ডিজঅর্ডার বিশ্লেষণ, ল্যাব রিপোর্ট ও রেডিওলজি ব্যাখ্যা, এআই-চালিত “Ask Your Doctor” ফিচার, রোগীর ডিজিটাল স্বাস্থ্য ইতিহাস সংরক্ষণ, দ্বিতীয় মতামত গ্রহণের সুযোগ এবং এমনকি স্বাস্থ্য বিমার সঙ্গেও যুক্ত থাকার ব্যবস্থা। সবচেয়ে বড় সুবিধা—এটি সীমিত ইন্টারনেট সংযোগেও কার্যকর।
এই প্রযুক্তি যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়, তবে এর বহুমাত্রিক সুফল পাওয়া সম্ভব। প্রথমত, রোগীরা সময় ও অর্থ সাশ্রয় করবেন, কারণ অনেক সাধারণ সমস্যা গ্রামেই সমাধান হবে। দ্বিতীয়ত, ঢাকার হাসপাতালে রোগীর অতিরিক্ত চাপ কমবে, ফলে চিকিৎসকরা জটিল কেসে বেশি মনোযোগ দিতে পারবেন। তৃতীয়ত, জাতীয় পর্যায়ে একটি সমন্বিত স্বাস্থ্য ডেটাবেইস গড়ে উঠবে, যা ভবিষ্যতের জন্য অমূল্য সম্পদ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এ ধরনের প্ল্যাটফর্ম ধীরে ধীরে বিদেশমুখী চিকিৎসার প্রবণতা কমাতে সাহায্য করবে।
বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত এখন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। একদিকে রয়েছে অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, বাজেট ঘাটতি, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের স্বল্পতা; অন্যদিকে রয়েছে এআই-চালিত প্রযুক্তি, টেলিমেডিসিন এবং ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবার সম্ভাবনা। Wikimedix-এর মতো উদ্যোগ হয়তো এখনই মহাকাশে পৌঁছায়নি, তবে এটি নিঃসন্দেহে একটি সাহসী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ।
স্বাস্থ্যসেবার ভবিষ্যৎ আর কেবল ঢাকার জন্য নয়। একজন কৃষক, শ্রমিক বা শিক্ষার্থী নিজের মোবাইলেই যদি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও সঠিক ডায়াগনোসিস পেতে পারেন, তবে সেটিই হবে প্রকৃত অর্থে স্বাস্থ্যসেবার গণতন্ত্রীকরণ। ডিজিটাল সমতার এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিলে বাংলাদেশ কেবল বিদেশমুখী ব্যয় কমাতে পারবে না, বরং একটি আস্থাশীল, আধুনিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্যখাত গড়ে তুলবে।
স্বাস্থ্যসেবা হবে সবার জন্য, শহর নয়—দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য।
✍️ নিউজ ডেস্ক, বিজ্ঞানী অর্গ
📧 [email protected]






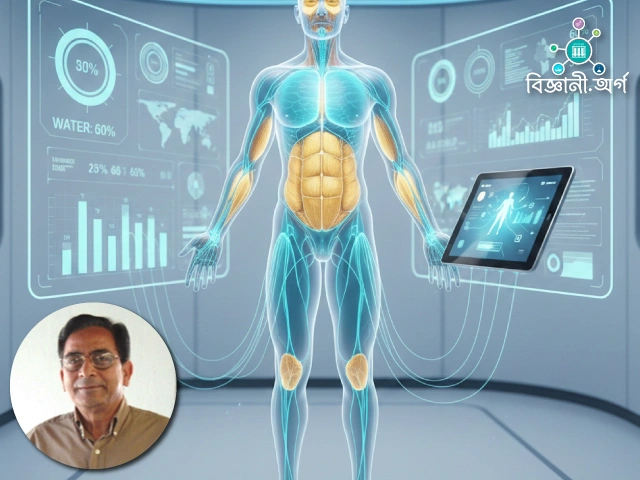
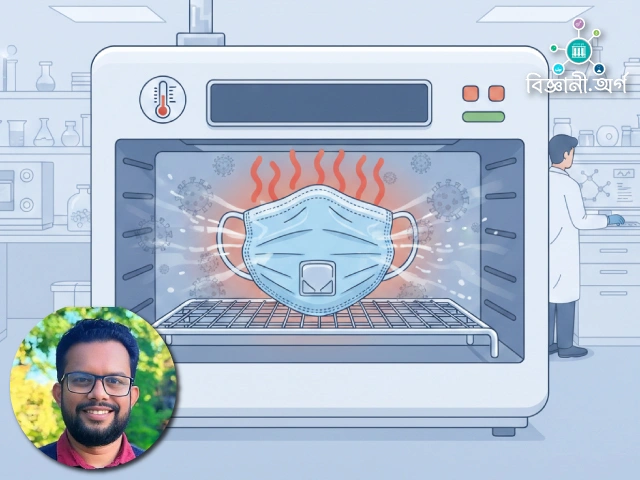



Leave a comment