ভূমিকাঃ
আমরা প্রায়ই শুনি—“মেয়ে সন্তান হওয়ার জন্য মা দায়ী।” অথচ বিজ্ঞানের চোখে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আসলে ছেলে না মেয়ে সন্তান হবে তা নির্ধারণ করে বাবার জেনেটিক উপাদান। তবুও সমাজে অনেক সময় মেয়েশিশু জন্ম নিলে মায়ের ওপর দোষ চাপানো হয়, যা কেবল কুসংস্কার নয়, কখনও কখনও তা পরিবার ভাঙনের কারণও হয়ে ওঠে।
বিজ্ঞান কী বলে: ছেলে না মেয়ে হবে কে নির্ধারণ করে?
প্রতিটি মানুষের শরীরে বিশেষ কিছু “ক্রোমোজোম” থাকে যা আমাদের দেহের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। এর মধ্যে একটি জোড়া হলো লিঙ্গ নির্ধারণকারী ক্রোমোজোম।
- মায়ের ডিম্বাণু সবসময় X ক্রোমোজোম বহন করে।
- বাবার শুক্রাণু হয় X অথবা Y বহন করে।
বাবার শুক্রাণু যদি X নিয়ে ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় → শিশুটি হবে মেয়ে (XX)।
বাবার শুক্রাণু যদি Y নিয়ে মিলিত হয় → শিশুটি হবে ছেলে (XY)।
অর্থাৎ, ছেলে না মেয়ে হবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে বাবার শুক্রাণুর ওপর, মায়ের ওপর নয়।
সমাজের ভুল ধারণা
যদিও বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা একেবারে পরিষ্কার, তবুও আমাদের সমাজে ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। অনেক সময় মেয়েশিশু জন্ম নিলে মায়ের ওপর দোষ চাপানো হয়।
- কন্যাশিশুকে বোঝা মনে করা হয়, কারণ বিয়েতে খরচ, যৌতুক বা পরিবারের বাইরে চলে যাওয়ার সামাজিক রীতি।
- পুত্রসন্তানকে পরিবারের উত্তরাধিকারী ধরা হয়, যে নাকি বংশ চালাবে এবং বৃদ্ধ বয়সে বাবা-মাকে দেখাশোনা করবে।
ফলে সমাজে এখনো ছেলে সন্তানের প্রতি পক্ষপাত দেখা যায়।
পারিবারিক টানাপোড়েন ও ডিভোর্স
দক্ষিণ এশিয়ার অনেক পরিবারে দেখা যায়—
- একের পর এক মেয়ে সন্তান জন্মালে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হয়।
- মায়ের ওপর দোষ চাপানো হয়, যদিও তার কোনো ভূমিকা নেই।
- অনেক ক্ষেত্রে মেয়ে সন্তান জন্মের কারণে নির্যাতন, দ্বিতীয় বিয়ে বা ডিভোর্স পর্যন্ত হয়।
এটি একদিকে নারীর প্রতি অন্যায়, অন্যদিকে বিজ্ঞানের সত্যকে অস্বীকার করার উদাহরণ।
বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপট
- অতীতে বাংলাদেশে পুত্রসন্তানকে “অবশ্যক” মনে করা হতো।
- গবেষণায় দেখা গেছে, অনেক পরিবার শুধু ছেলের আশায় বেশি সন্তান নিতে চাইতো।
- তবে সাম্প্রতিক সময়ে শহরাঞ্চলে দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে—অনেক বাবা-মা এখন ছেলে-মেয়েকে সমানভাবে চান।
- বাংলাদেশ হাইকোর্ট সম্প্রতি প্রশ্ন তুলেছে, গর্ভে থাকা শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণের পরীক্ষা অবাধে চলতে দেওয়া কেন ঠিক হবে না, কারণ এতে লিঙ্গভিত্তিক গর্ভপাতের ঝুঁকি বাড়ে।
উপসংহারঃ
বিজ্ঞানের সত্য হলো—সন্তানের ছেলে না মেয়ে হবে তা বাবার শুক্রাণুই নির্ধারণ করে, মায়ের কোনো ভূমিকা নেই।
কিন্তু সমাজে এই সত্য অস্বীকার করে মেয়েশিশুর জন্য মাকে দায়ী করা হয়। এর ফলে অনেক নারীকে অন্যায়ভাবে নির্যাতন, অবহেলা এমনকি ডিভোর্স পর্যন্ত সহ্য করতে হয়।
আমাদের করণীয় হলো—
- এই বৈজ্ঞানিক তথ্য মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।
- ছেলে-মেয়ে উভয়কে সমান মর্যাদা দেওয়া।
- কন্যাশিশুকে বোঝা নয়, বরং পরিবারের সমান আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করা।
রেফারেন্সঃ
- Jobling, M.A., & Tyler-Smith, C. (2003). The human Y chromosome: An evolutionary marker comes of age. Nature Reviews Genetics.
- UNICEF (2019). Gender equality and children in South Asia.
- NIPORT & ICDDR,B (2021). Bangladesh Demographic and Health Survey.
- Pande, R. & Malhotra, A. (2006). Son Preference and Daughter Neglect in India. World Bank.
- The Daily Star (2024). “High Court questions govt over sex determination tests in pregnancy.”
Written by,
Md. Fahad Hossain
Student, Department of Zoology.
Shahid Bulbul Govt. College, Pabna.
(Affiliated with National University of Bangladesh.)




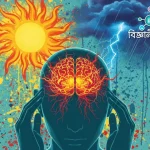
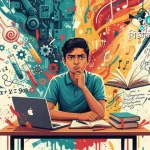


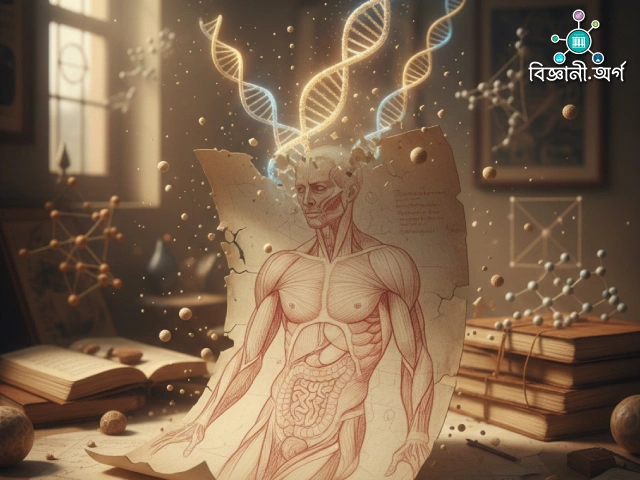


Leave a comment