ড. মশিউর রহমান
বাংলাদেশের তরুণ গবেষকরা যখন উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যান, তখন তাদের অধিকাংশই ভেবে নেন যে একমাত্র মর্যাদাপূর্ণ ক্যারিয়ারের পথ হলো বিশ্ববিদ্যালয় বা একাডেমিয়ার ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকা। গবেষণা করা, প্রবন্ধ প্রকাশ করা এবং অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পাওয়াই যেন সফলতার একমাত্র সংজ্ঞা। কিন্তু বাস্তবতা এর চেয়ে অনেক বেশি জটিল এবং বিস্তৃত। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক জরিপগুলো আমাদের জানাচ্ছে, বিশ্বের মাত্র ১০ থেকে ১৫ শতাংশ পিএইচডি ধারী শেষ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে একাডেমিয়ার ভেতরে থাকতে পারেন। বাকিরা, অর্থাৎ প্রায় ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ, শেষ পর্যন্ত চলে যান অন্য খাতে—সরকারি সংস্থা, শিল্প গবেষণা, বিজ্ঞান সাংবাদিকতা, এমনকি স্বাস্থ্যসেবা কিংবা নীতিনির্ধারণেও।
তাহলে প্রশ্ন জাগে—এতজন কেন একাডেমিয়ার বাইরে চলে যান? গবেষণায় দেখা গেছে, প্রধান কারণ হলো অনিশ্চয়তা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চাকরির সুযোগ সীমিত, দীর্ঘদিন অস্থায়ী চুক্তিতে কাজ করার পরও স্থায়ী পদ পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া গবেষণা অনুদান জোগাড়ের চাপ, প্রকাশনা নিয়ে প্রতিযোগিতা, এবং ক্রমাগত মানসিক চাপে অনেকেই বিকল্প পথ খুঁজতে বাধ্য হন। অনেকের জন্য ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করাও বড় চ্যালেঞ্জ—দীর্ঘ সময় ল্যাবে কাটানো এবং সীমিত বেতনে পরিবার চালানো সবসময় সম্ভব হয় না।
কিন্তু একাডেমিয়ার বাইরের জগৎ শুধু ‘বিকল্প’ নয়, বরং সমান মর্যাদাপূর্ণ এবং সম্ভাবনাময় এক কর্মক্ষেত্র। ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, প্রযুক্তি শিল্প, সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বা নীতি-প্রণয়নকারী সংস্থা—সবখানেই প্রয়োজন হয় গবেষণার দক্ষতা ও সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তির। এক জরিপে দেখা গেছে, একাডেমিয়া ছেড়ে যাওয়া গবেষকদের ৮৪ শতাংশই বলেছেন তারা তাদের নতুন পেশায় সন্তুষ্ট। আরও চমকপ্রদ তথ্য হলো, মাত্র ৬ শতাংশ বলেছেন সুযোগ পেলে তাঁরা আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যেতে চান। অর্থাৎ, একবার অন্য খাতে ঢুকে পড়লে গবেষকরা সেখানে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে নতুনভাবে কাজে লাগাতে পারেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই সফলতা অর্জন করেন।
একাডেমিয়ায় অর্জিত অভিজ্ঞতা আসলে কতটা কার্যকর? সংখ্যাগুলো বেশ স্পষ্ট। প্রায় ৭৫ শতাংশ গবেষক জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখা দক্ষতাগুলো তাঁরা এখনও ব্যবহার করছেন। এমনকি যারা সরাসরি গবেষণার বাইরে গিয়েছেন—যেমন সাংবাদিকতা, ব্যবস্থাপনা বা পরামর্শকতায়—তাঁরাও তাঁদের সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি, ডেটা বিশ্লেষণ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কিংবা দলগত কাজের দক্ষতা প্রতিদিন কাজে লাগাচ্ছেন। অর্থাৎ, গবেষণার সময় অর্জিত অভিজ্ঞতা কোনো সংকীর্ণ খাঁচায় আবদ্ধ নয়; বরং এটি বহুমাত্রিক ও আন্তঃবিভাগীয় কর্মক্ষেত্রে সমান কার্যকর।
কিন্তু সমস্যা হলো এই দক্ষতাগুলোকে প্রমাণ করতে না পারা। গবেষকরা প্রায়ই নিজেদের যোগ্যতা একাডেমিক প্রকাশনার ভাষায় সীমাবদ্ধ রাখেন। ফলে শিল্প খাত বা সরকারি সংস্থার কাছে নিজেদের বাজারযোগ্যতা বোঝাতে ব্যর্থ হন। এই সীমাবদ্ধতাই ভাঙতে তৈরি হয়েছে Researcher Development Framework (RDF)—একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কাঠামো, যা গবেষকদের শেখায় কিভাবে নিজেদের দক্ষতাকে দৃশ্যমান করতে হয়, কীভাবে বৈজ্ঞানিক যোগ্যতাকে পেশাগত ভাষায় রূপান্তর করতে হয়। RDF এর মূল উদ্দেশ্য হলো গবেষককে শুধু বিজ্ঞানচর্চায় সীমাবদ্ধ না রেখে, বরং তাকে এমন এক পেশাজীবী হিসেবে তৈরি করা, যে যেকোনো খাতে নিজের জায়গা তৈরি করতে পারে।
তাহলে আমাদের তরুণ গবেষকদের জন্য বার্তাটি কী? প্রথমত, একাডেমিয়ার ভেতরে ক্যারিয়ারের সুযোগ যেমন সীমিত, তেমনি প্রতিযোগিতামূলক। কিন্তু এর বাইরেও সমান মর্যাদাপূর্ণ ও প্রভাবশালী ক্যারিয়ারের সুযোগ রয়েছে। দ্বিতীয়ত, গবেষক হিসেবে আপনার আসল শক্তি শুধু প্রবন্ধ বা ল্যাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, সমস্যা সমাধান, দলগত কাজ এবং যোগাযোগ দক্ষতায়ও নিহিত। তৃতীয়ত, এই দক্ষতাগুলোকে প্রকাশ করার কৌশল রপ্ত করাই আপনার ভবিষ্যতের সাফল্যের চাবিকাঠি।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ আলোচনা আরও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি করে বের হচ্ছেন। কিন্তু গবেষণাগার বা একাডেমিক পদের সংখ্যা সীমিত। এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়কে একমাত্র লক্ষ্য বানালে হতাশা তৈরি হবে। বরং প্রয়োজন সচেতনতা বাড়ানো—যাতে তরুণ গবেষকরা জানতে পারেন, তাঁদের দক্ষতার মূল্য শিল্প, প্রযুক্তি, নীতি কিংবা আন্তর্জাতিক সংস্থায়ও সমানভাবে রয়েছে।
আজকের বিশ্বে গবেষণা কেবল একাডেমির সীমানায় আবদ্ধ নয়। জলবায়ু পরিবর্তন, জনস্বাস্থ্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কিংবা অর্থনৈতিক উন্নয়ন—সব ক্ষেত্রেই গবেষণা ও প্রমাণভিত্তিক জ্ঞান অপরিহার্য। তাই একজন গবেষকের প্রকৃত পরিচয় হওয়া উচিত জ্ঞানস্রষ্টা এবং সমস্যা সমাধানকারী, যিনি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নয়, পুরো সমাজের জন্য অপরিহার্য।
বাংলাদেশের তরুণ গবেষকদের সামনে তাই বড় প্রশ্ন হলো—আপনার পরিচয় কি শুধু একাডেমিক ‘প্রবন্ধ প্রকাশক’, নাকি আপনি এক বহুমাত্রিক পেশাজীবী, যিনি জ্ঞানের শক্তিকে সমাজের নানা স্তরে কাজে লাগাতে সক্ষম? উত্তর খুঁজে পাওয়া জরুরি এখনই। কারণ একাডেমিয়ার বাইরের বিশ্বও আপনার জন্য অপেক্ষা করছে—সম্ভাবনায় ভরা, চ্যালেঞ্জে পূর্ণ এবং সমান মর্যাদাপূর্ণ এক কর্মক্ষেত্র।






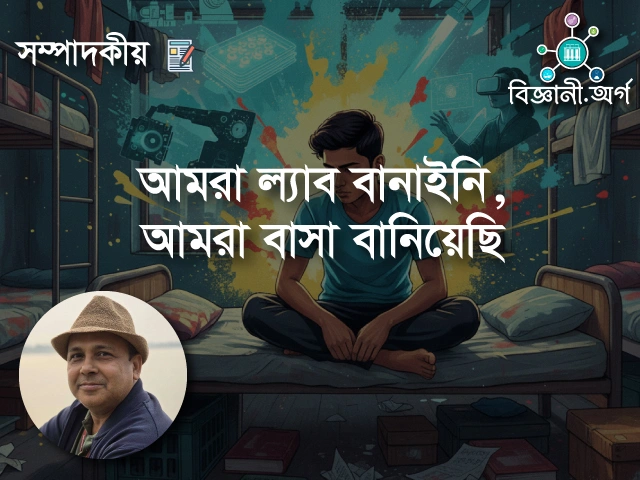
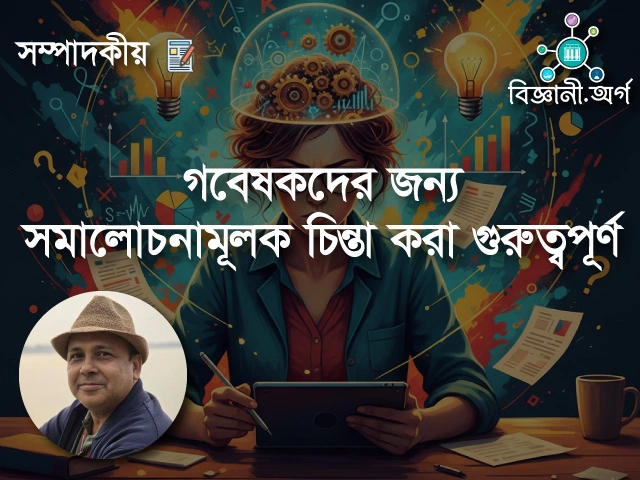
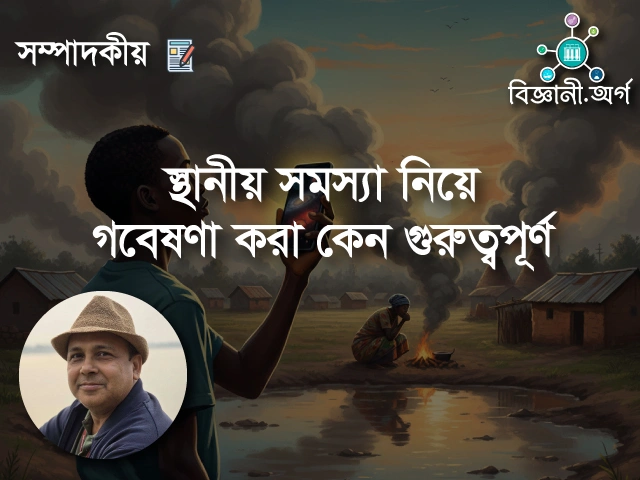
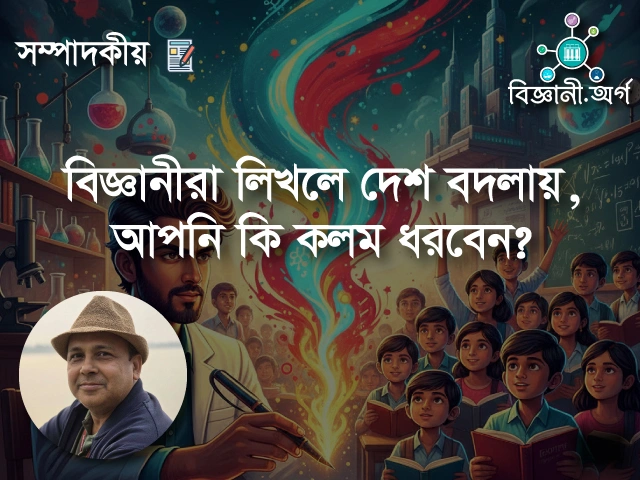
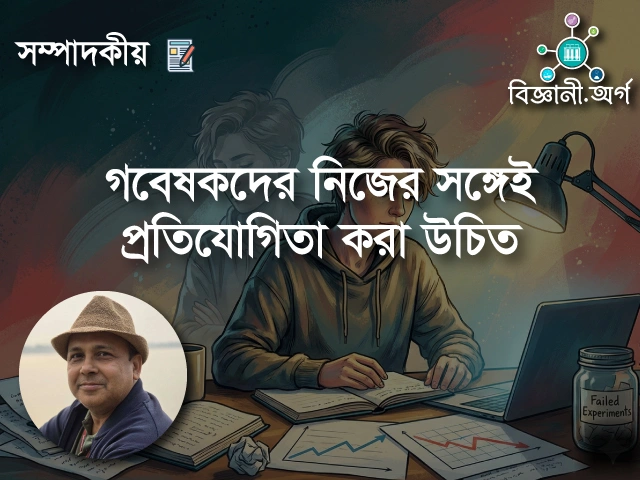
Leave a comment