ড. মশিউর রহমান
বাংলাদেশের তরুণ গবেষকদের সামনে আজ যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা হলো—গবেষণার পরবর্তী ধাপ কোথায় শুরু হবে? দেশে থেকে ক্যারিয়ার গড়া, নাকি বিদেশে গিয়ে নতুন পরিবেশে, নতুন বিষয়ের সঙ্গে লড়াই করা? সাম্প্রতিক এক সেমিনারে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুতোমাত্সু ও কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক সাকাই তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করেছেন। আলোচনার কেন্দ্রে ছিল হিউম্যান ফ্রন্টিয়ার সায়েন্স প্রোগ্রাম (HFSP) ফেলোশিপ, যা গবেষকদের একেবারে নতুন, আন্তঃবিষয়ক (interdisciplinary) গবেষণায় ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে।
গবেষণা জীবন সাধারণত একটানা একটি শৃঙ্খলার ভেতর দিয়ে এগোয়। কেউ হয়তো উদ্ভিদবিজ্ঞান নিয়ে শুরু করেন, কেউ জেনেটিক্স বা বায়োকেমিস্ট্রি। কিন্তু পোস্টডক পর্যায়ে এসে হঠাৎ করে নিজের ক্ষেত্র বদলে ফেলা, একেবারে নতুন হাতিয়ার বা নতুন জীববৈজ্ঞানিক প্রশ্নের দিকে ঝুঁকে পড়া—এটি যেমন ভয়ানক ঝুঁকির, তেমনি অসাধারণ সম্ভাবনারও। HFSP ঠিক এই ধরনের সাহসী উদ্যোগকে পুরস্কৃত করতে তৈরি। এটি এমন সব প্রস্তাব খুঁজে নেয়, যেগুলো হয়তো সফল হবে না, কিন্তু সফল হলে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বিজ্ঞানের জগতে।
অধ্যাপক সুতোমাত্সু নিজেই এরকম এক যাত্রার উদাহরণ। তিনি ডক্টরেট শেষ করার পর ইউরোপে ছয় বছরের বেশি সময় কাটিয়েছেন। প্রথমে ছোট একটি ল্যাবে, যেখানে প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গভীরভাবে শেখার সুযোগ ছিল। পরে গেছেন বড় গবেষণা দলে, যেখানে নানা দেশের, নানা প্রেক্ষাপটের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কাজ করেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা বলছে—ছোট ল্যাব গবেষকের দক্ষতা গড়ে তোলে, আর বড় ল্যাব তাকে আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক ও দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তারের সুযোগ দেয়। উভয়ের সংমিশ্রণ গবেষককে পূর্ণতা দেয়।
কিন্তু এসব অভিজ্ঞতা একা যথেষ্ট নয়। HFSP-এর মতো আন্তর্জাতিক ফেলোশিপে আবেদন করতে হলে প্রমাণ করতে হয় তিনটি বিষয়। প্রথমত, গবেষণা প্রকল্পটি ডক্টরেট পর্যায়ের কাজের স্রেফ পুনরাবৃত্তি নয়, বরং স্পষ্ট নতুনত্ব রয়েছে। দ্বিতীয়ত, কাজটি সত্যিই বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিতে পারে, অর্থাৎ ‘হাই-রিস্ক, হাই-গেইন’। তৃতীয়ত, প্রস্তাবিত গবেষণা কেন নির্দিষ্ট হোস্ট ল্যাবরেটরিতেই সবচেয়ে ভালোভাবে সম্পন্ন হতে পারে, তা যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়। অন্যভাবে বললে, শুধু ভালো আইডিয়া থাকলেই চলবে না, সেটি কোথায়, কার সঙ্গে, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে তা দেখাতে হবে।
এমন প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিকভাবেই প্রতিযোগিতা প্রচণ্ড কঠিন। প্রথম ধাপের আবেদন (Letter of Intent) থেকেই ৮০ শতাংশ প্রস্তাব বাদ পড়ে যায়। যারা প্রথম ধাপ পার করতে পারে, তাদেরই কেবল পূর্ণ প্রস্তাব জমা দেওয়ার সুযোগ থাকে, এবং চূড়ান্ত নির্বাচিত হয় মাত্র ১০ শতাংশের মতো। এর মানে হলো, আবেদন করার সাহস দেখানোই এক বড় পদক্ষেপ। আর এ প্রক্রিয়ায় অনেক সময়ই গবেষককে নিজের পরিচিত ক্ষেত্র ছাড়তে হয়, এমন কিছুর দিকে পা বাড়াতে হয় যা আগে কখনও করেননি।
বাংলাদেশের তরুণদের জন্য এর মধ্যে বিশেষ বার্তা আছে। দেশে অনেক সময় আমরা গবেষণাকে সীমিত পরিসরে দেখি, কেবল নিরাপদ পথে চলতে চাই। অথচ বিজ্ঞানের আসল শক্তি নিহিত আছে ঝুঁকি নেওয়ার মধ্যেই। নতুন পরিবেশে গিয়ে, নতুন হাতিয়ার শিখে, নতুন প্রশ্নে হাত দেওয়া মানেই অজানার সঙ্গে এক ধরনের লড়াই। এই লড়াইয়েই তৈরি হয় বড় বিজ্ঞানী। বিদেশে পোস্টডক মানেই শুধু একাডেমিক সনদ নয়, বরং জীবন ও গবেষণার পরিসর প্রসারিত করা।
অধ্যাপক সুতোমাত্সুর ভাষায়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—গবেষক কি তাঁর প্রস্তাব দিয়ে রিভিউয়ারকে উত্তেজিত করতে পারছেন? বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব কেবল তথ্যের সমষ্টি নয়; এটি এক ধরনের গল্পও, যেখানে পাঠক হঠাৎ থেমে বলেন, “আহা, যদি এটা সত্যিই সম্ভব হয়, তবে অসাধারণ কিছু ঘটবে।” এই ‘উত্তেজনা সৃষ্টির ক্ষমতা’ই ভালো প্রস্তাবকে সাধারণ প্রস্তাব থেকে আলাদা করে দেয়।
শেষ পর্যন্ত বিদেশে পোস্টডক করা হোক বা না হোক, তরুণ গবেষকের কাছে আসল প্রশ্নটি একটাই—সে কি নিজের সীমা ভাঙার সাহস রাখে? HFSP-এর মতো সুযোগগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয়, বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ কেবল নিশ্চিত পথেই নয়, বরং অনিশ্চিত, অচেনা পথে হাঁটার মধ্যেই লুকিয়ে আছে। বাংলাদেশের তরুণ গবেষকদের তাই শুধু নিরাপদ গণ্ডি নয়, বরং চ্যালেঞ্জিং নতুন দিগন্তকেও আলিঙ্গন করতে হবে।
সূত্র:
Japan Science and Technology Agency এর একটি অনুষ্ঠানের বক্তব্য থেকে লেখাটি লিখিত


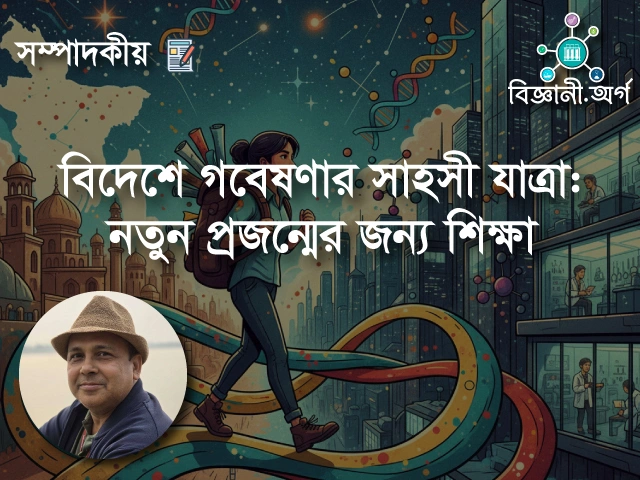



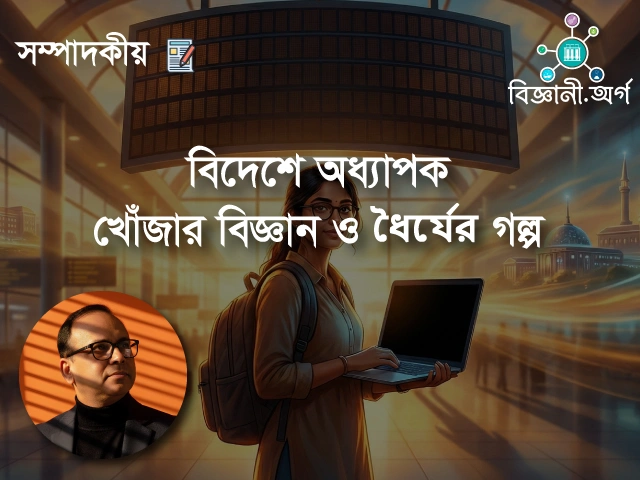
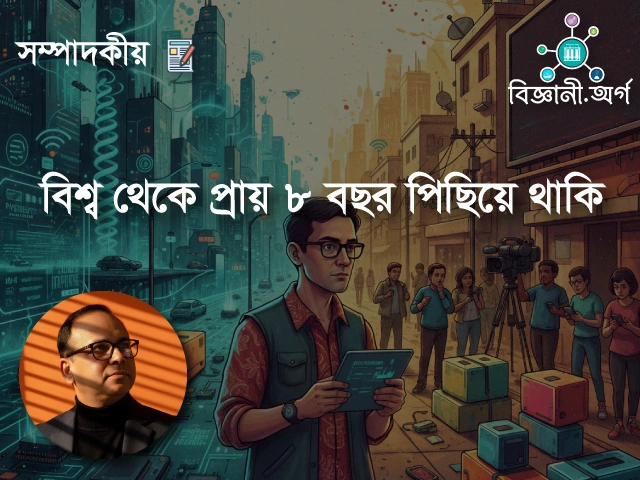
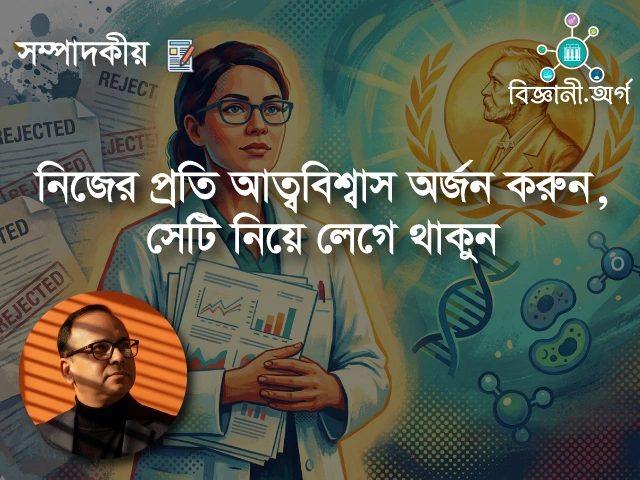

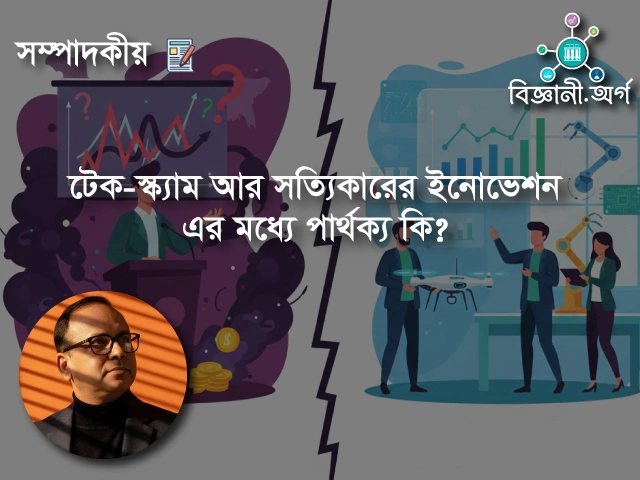
Leave a comment