নিউজ ডেস্ক, বিজ্ঞানী অর্গ |
যোগাযোগ: [email protected]
বিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের একটি সাধারণ ধারণা হলো এটি একগুচ্ছ নিশ্চিত জ্ঞানের ভাণ্ডার, যেখানে পরীক্ষার পর প্রমাণিত সত্যগুলো সযত্নে সঞ্চিত থাকে। কিন্তু অস্ট্রিয়ান-ইংরেজ দার্শনিক কার্ল পপার এই ধারণার গোড়া ধরে নাড়িয়ে দেন। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত তাঁর বই The Logic of Scientific Discovery বিজ্ঞানের একটি বিপ্লবী ব্যাখ্যা হাজির করে, যেখানে বিজ্ঞান শুধুমাত্র সত্যের অনুসন্ধান নয়, বরং মিথ্যা প্রমাণের সক্ষমতা বা “ফলসিফায়েবিলিটি”-র ওপর ভিত্তি করে এগিয়ে চলে। এই চিন্তাধারাই আধুনিক বিজ্ঞানের দর্শনের কেন্দ্রে জায়গা করে নেয়।
পপারের মূল যুক্তিটি ছিল একেবারেই সোজা কিন্তু গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তখনই অর্থপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য, যখন সেটি এমনভাবে গঠিত যে তা ভুল প্রমাণ করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ যদি কোনো তত্ত্ব এমন হয় যে তা সব পরিস্থিতিতে সত্য বলেই দাবি করে, এবং তাকে কোনোভাবেই ভুল প্রমাণ করা যায় না, তবে সেটি বিজ্ঞানের নয়, বরং মতবাদ বা বিশ্বাসের পর্যায়ে পড়ে। এই দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে বড় উদাহরণ তিনি দেন জ্যোতির্বিজ্ঞান বনাম জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রসঙ্গে। জ্যোতির্বিজ্ঞান যেখানে সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করে যেগুলো পরীক্ষাযোগ্য, সেখানে জ্যোতিষশাস্ত্র এমন ভবিষ্যদ্বাণী করে যেগুলো এতটা অস্পষ্ট যে ভুল প্রমাণ করা অসম্ভব।
এই যুক্তি আমাদের চিন্তার পদ্ধতিকে গভীরভাবে নাড়িয়ে দেয়। আমরা অনেক সময়ই একটি তত্ত্বকে “সত্য” মনে করি কারণ তা আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যায় বা ইতিহাসে কখনো ভুল প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু পপারের মতে, একটি তত্ত্ব যত বেশি পরীক্ষার মুখে পড়ে এবং তাতে টিকে যায়, ততই তার বৈজ্ঞানিক শক্তি বাড়ে। এর মানে এই নয় যে তত্ত্বটি চূড়ান্ত সত্য, বরং এটিই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা—যেটিকে ভবিষ্যতে আরও উন্নত তত্ত্ব এসে ভুল প্রমাণ করতে পারে। এভাবেই বিজ্ঞান এগোয়, একের পর এক ভুলকে চিনে নিয়ে, নিজেকে সংশোধন করে।
পপারের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন আমরা বিভিন্ন ছদ্মবিজ্ঞান বা ‘পসুডোসায়েন্স’-এর মুখোমুখি হই। উদাহরণস্বরূপ, হোমিওপ্যাথি কিংবা অ্যাস্ট্রোলজির মতো অনেক বিষয়ই নিজেদের বৈজ্ঞানিক রূপে উপস্থাপন করে, কিন্তু এদের কোনো তত্ত্বকেই ফলসিফাই করা যায় না। কারণ তারা এমনভাবে গঠিত যে সবকিছুকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়—ফলাফল যাই হোক না কেন। এক্ষেত্রে পপারের মাপকাঠি আমাদের একটি দারুণ হাতিয়ার দেয়: যদি কোনো তত্ত্ব পরীক্ষা করে ভুল প্রমাণ করার সুযোগ না থাকে, তবে তা বিজ্ঞানের নয়।
এই ধারণার আরও গভীরে গেলে দেখা যায়, পপারের ‘ফলসিফায়েবিলিটি’ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একটি নৈতিক মাপকাঠিও দাঁড় করায়। একজন প্রকৃত বিজ্ঞানীর দায়িত্ব হলো নিজের তত্ত্বকে কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলানো এবং ভুল প্রমাণ করার সুযোগ রাখা। এটি আত্মবিশ্বাসের চেয়ে বেশি আত্মসমালোচনার সাহস, যা একজন গবেষকের নৈতিক উচ্চতাকে প্রকাশ করে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেখানে বিজ্ঞানচর্চা এখনও নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে, সেখানে এই দর্শন নতুন প্রজন্মের গবেষকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা হতে পারে।
পপারের তত্ত্ব আমাদের আরও একটি মৌলিক সত্য মনে করিয়ে দেয়—বিজ্ঞান কোনো চূড়ান্ত সত্যের জ্ঞান নয়, বরং একটি চলমান অনুসন্ধান। নিউটনের তত্ত্ব এক সময় আমাদের সৌরজগত ব্যাখ্যায় শ্রেষ্ঠ ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে আইনস্টাইন এসে সেই কাঠামোর সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে দিলেন। আজকে আমরা কোয়ান্টাম তত্ত্ব কিংবা স্ট্রিং থিওরির কথা বলছি, কিন্তু সেগুলোর প্রতিটিই পরীক্ষার মুখে দাঁড়িয়ে। প্রতিটি ধাপে পপারের বক্তব্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়—একটি তত্ত্ব যতক্ষণ না ভুল প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণই তা টিকে থাকে, চূড়ান্ত নয়।
এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটটিও ভাবতে হয়। আমাদের দেশে গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক সময় একটি তত্ত্ব বা গবেষণালব্ধ ফলাফলকে প্রশ্নাতীত বলে ধরে নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। পপারের দর্শন আমাদের শেখায়—প্রশ্ন করাই হল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল চালিকাশক্তি। শুধু পরীক্ষাগারে নয়, পাঠ্যবইয়েও যদি আমরা এই আত্মসমালোচনার জায়গাটি তৈরি করতে পারি, তবে ভবিষ্যতের গবেষকরা আর অনুকরণে নয়, অনুসন্ধানে উৎসাহী হবেন।
পপারের চিন্তাভাবনা শুধুমাত্র গবেষণার জন্যই নয়, গণতান্ত্রিক চর্চার সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি সমাজ কতটা বিজ্ঞানমনস্ক, তা বোঝা যায় সেটি কতটা প্রশ্ন করতে শেখে। যুক্তিনির্ভর সমাজ গড়ে ওঠে তখনই, যখন মানুষ বিশ্বাস নয়, প্রমাণ চায়; কর্তৃপক্ষের কথা নয়, ব্যাখ্যা চায়। এই বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরিতে ‘ফলসিফায়েবিলিটি’ ধারণা একটি মৌলিক কাঠামো প্রদান করে।
আজ যখন আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের মতো নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের মুখোমুখি হচ্ছি, তখন পপারের চিন্তা আমাদের মনে করিয়ে দেয়—এই প্রযুক্তিগুলোকেও প্রশ্ন করতে হবে, যাচাই করতে হবে, আর তারপরে গ্রহণ করতে হবে। কারণ বিজ্ঞান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, সেটি কোনো মতবাদ নয়; সেটি একটি পদ্ধতি—যেখানে প্রশ্ন করার স্বাধীনতাই সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক গুণ।
কার্ল পপারের The Logic of Scientific Discovery তাই শুধু দার্শনিকদের জন্য নয়, বরং প্রতিটি শিক্ষক, গবেষক, ছাত্র এবং বিজ্ঞানপ্রেমীর জন্য একটি জরুরি পাঠ। এটি আমাদের শেখায় যে বিজ্ঞান কোনো নিখুঁত গোষ্ঠীর কার্যকলাপ নয়; এটি মানুষদের এক বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রা—যেখানে ভুল করা মানেই পথ এগিয়ে যাওয়া। যে সমাজ এই ভুলকে গ্রহণ করতে পারে, এবং প্রতিটি সত্যকে প্রশ্ন করতে সাহস পায়, সেই সমাজই দীর্ঘমেয়াদে উন্নত ও মুক্ত চিন্তার একটি ভিত্তি গড়ে তোলে।
সর্বোপরি, বাংলাদেশের মতো একটি উদীয়মান দেশের জন্য এই বইটি একটি সময়োপযোগী পাঠ হতে পারে। আমরা যদি পপারের দৃষ্টিভঙ্গিকে তরুণ গবেষকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারি, তবে একদিন আমাদের দেশের গবেষণাগুলো শুধু তথ্যের পেছনে ছুটবে না, বরং সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের অবস্থান পর্যালোচনা করতে শিখবে। সেটিই হবে একটি জ্ঞানভিত্তিক জাতি গঠনের প্রকৃত সূচনা।






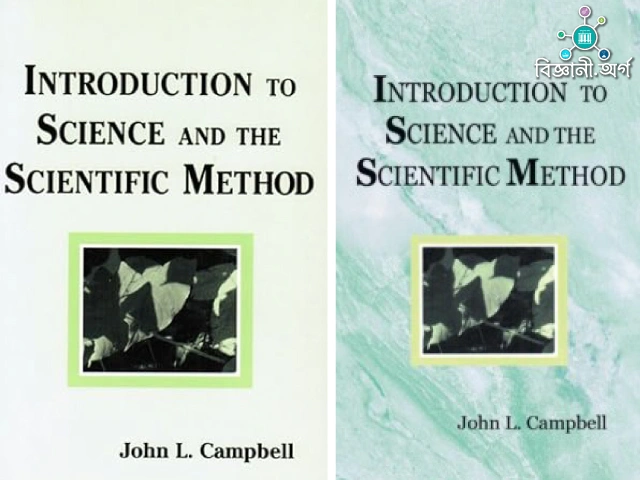

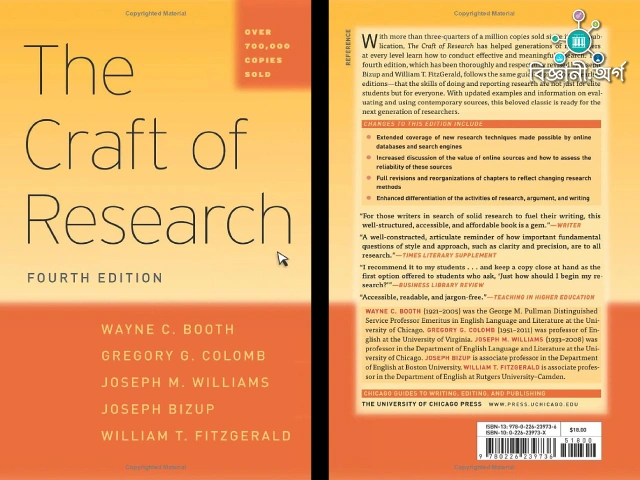
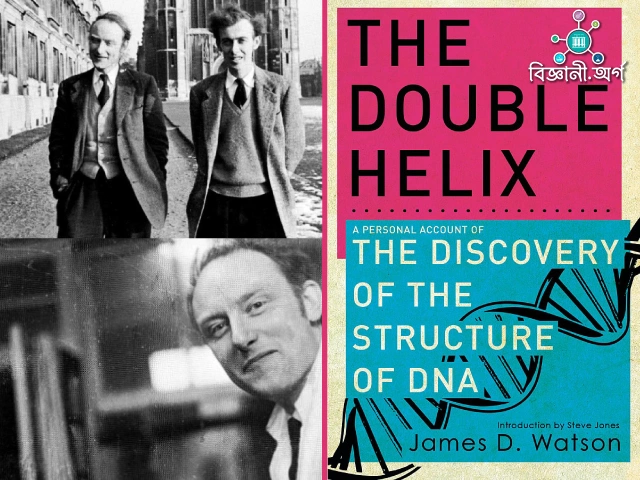
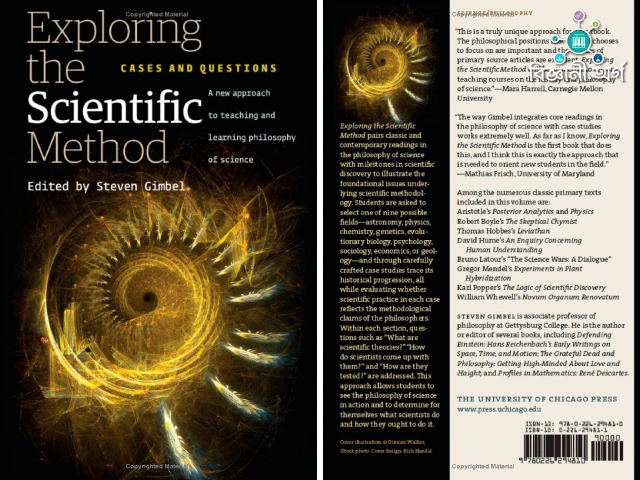
Leave a comment