নিউজ ডেস্ক, বিজ্ঞানী অর্গ
biggani.org
সিনেমায় অনেকবার দেখা যায়—আকাশযানটি জ্বালানিহীন, শত্রু আক্রমণ অথবা মহাজাগতিক কোনো বিপর্যয় থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইছে, তখন সামনে হঠাৎ একটি গ্রহকে দেখা যায়। তারা সেই গ্রহের মাধ্যাকর্ষণকে কাজে লাগিয়ে, এক ধরণের ‘স্লিংশট’ ব্যবহার করে দ্রুত পালিয়ে যায়। এই দৃশ্য বাস্তবে কি সম্ভব?
আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই প্রযুক্তি সত্যিই বাস্তবে ব্যবহৃত হয়! বিজ্ঞানীরা এই কৌশলকে ‘গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাসিস্ট’ বা গ্র্যাভিটেশনাল স্লিংশট বলেন, যা মহাকাশ ভ্রমণের জন্য অত্যন্ত জরুরি।
এই পদ্ধতিতে মূল ধারণাটি হলো: একটি মহাকাশযান কোনো গ্রহের কাছাকাছি আসার সময়, গ্রহটির মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে তার গতিপথ পরিবর্তন হয়। তবে শুধু গতিপথই নয়, গ্রহটির কক্ষপথের গতি ব্যবহার করে মহাকাশযান তার গতি বাড়াতেও পারে। এটি আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত মনে হলেও বাস্তবে সম্ভব। কিন্তু কীভাবে?
ধরা যাক, আপনি একটি বল মাটির কিছুটা ওপরে ধরে রেখে ছেড়ে দিলেন। বলটি নিচে পড়ার সময় দ্রুতগতিতে নিচের দিকে যাবে এবং মাটি ছুঁয়ে আবার উপরে উঠবে। কিন্তু কখনোই আপনি যেখান থেকে বলটি ছেড়েছেন, তার ওপরে উঠবে না। অর্থাৎ বলের গতিশক্তি (কাইনেটিক এনার্জি) নিয়ম অনুযায়ী একই থাকে, কখনো বাড়ে না।
একই ঘটনা মহাকাশযানের ক্ষেত্রেও ঘটে। গ্রহের দিকে এগিয়ে আসার সময় মহাকাশযানটি দ্রুতগতিতে এগোয়, কিন্তু যাওয়ার পথে একই পরিমাণ শক্তি হারায়। তাহলে মহাকাশযান কীভাবে গতি বৃদ্ধি পায়? এখানেই মূল রহস্য।
মূল ব্যাপারটি হলো “গ্রহের আপেক্ষিক গতি”। মহাকাশযান যখন একটি গ্রহের কাছ দিয়ে যায়, তখন এটি গ্রহের নিজের কক্ষপথের গতি থেকে সামান্য শক্তি চুরি করে নিতে পারে। অর্থাৎ, সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণায়মান গ্রহের গতি থেকে কিছুটা গতি মহাকাশযানটি নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারে। এতে গ্রহের গতি সামান্য কমলেও, গ্রহের বিশাল ভরের তুলনায় এই ক্ষয় অতি নগণ্য। একটি ছোট মহাকাশযান, যেমন মাত্র কয়েক টন ওজনের, এই বিশাল গ্রহের গতির ওপর কার্যত কোনো প্রভাব ফেলে না।
মহাকাশে দূরের গ্রহে পৌঁছাতে প্রচুর জ্বালানি প্রয়োজন। রকেট প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতার কারণে এটি অত্যন্ত কঠিন। একটি রকেটে যত বেশি জ্বালানি বহন করা হয়, রকেটের ওজন তত বাড়ে। আর বেশি ওজনের কারণে আরো বেশি জ্বালানি লাগে। এই চক্রটি একসময় অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, যা “রকেট সমীকরণ” দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়।
তাই, গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাসিস্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাধান। উদাহরণ হিসেবে ক্যাসিনি মহাকাশযানটির কথা বলা যায়, যেটি ১৯৯৭ সালে শনি গ্রহের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। এটি তার যাত্রায় বৃহস্পতি গ্রহের কাছাকাছি দিয়ে যায় এবং গ্রহের কক্ষপথের শক্তি ব্যবহার করে নিজের গতি বৃদ্ধি করে। এর ফলে ক্যাসিনি কম সময়ে শনিতে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। এমনকি ক্যাসিনি শুক্র ও পৃথিবীর কাছ দিয়েও একাধিকবার গিয়েছিল, যাতে সে আরো বেশি শক্তি সঞ্চয় করতে পারে।
এই কৌশলটি বিপরীত ভাবেও কাজ করে। পৃথিবী থেকে সূর্যের কাছের গ্রহ যেমন শুক্র বা বুধের দিকে যেতে হলে, পৃথিবীর ৩০ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডের বিপুল গতিকে অতিক্রম করা কঠিন। তাই বিজ্ঞানীরা গ্রহের বিপরীত দিকে প্রোবটি পাঠিয়ে শুক্রের কাছাকাছি নিয়ে এসে, গ্রহকে কিছু গতি দিয়ে মহাকাশযানের গতি ধীরে ধীরে কমিয়ে সূর্যের দিকে পাঠান। ইউরোপ ও জাপানের যৌথ প্রোজেক্ট বেপিকলম্বো এই পদ্ধতিতে বুধ গ্রহে পৌঁছাতে কাজ করছে।
২০২৫ সালের জানুয়ারিতে শেষবারের মতো বুধের কাছে পৌঁছে ২০২৬ সালের নভেম্বরে এটি বুধের কক্ষপথে প্রবেশ করবে। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা ইন্টারপ্ল্যানেটারি মিশনগুলোকে অত্যন্ত সাশ্রয়ী ও দ্রুত করেছেন।
গ্র্যাভিটেশনাল স্লিংশট আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় মহাকাশ ভ্রমণের জটিলতা কতখানি। মহাকাশ ভ্রমণ আসলেই ‘রকেট বিজ্ঞান’ এবং এটি অত্যন্ত জটিল। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি থেকে বের হওয়াই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তবে মজার বিষয়, যে মাধ্যাকর্ষণ থেকে মুক্তি পেতে এত সংগ্রাম করতে হয়, সেই মাধ্যাকর্ষণই আবার আমাদের দূর মহাকাশে সহজে পৌঁছানোর পথ তৈরি করে দিয়েছে।
গ্র্যাভিটেশনাল স্লিংশট প্রযুক্তি আমাদের মহাকাশ অভিযানকে শুধু সহজই করেনি, বরং আমাদের সামনে উন্মোচন করেছে মহাকাশ অভিযানের অসীম সম্ভাবনার নতুন দ্বার।










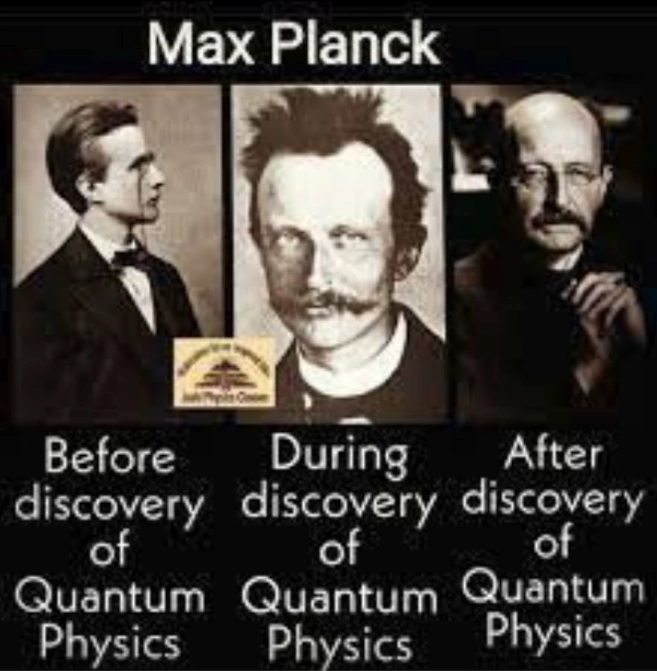
Leave a comment